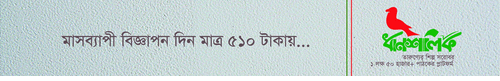গল্পটি
শুনতে চেয়ো না
সোহেল নওরোজ
১
একে একে তিন কাপ চা শেষ করলেন হাফিজুল হক। এই কাজটা তিনি রোজ
করেন। প্রথমে পান করেন চিনি ছাড়া আদা চা। এটা গিলতে তার বেশ কষ্ট হয়। মুখের ভেতর বিশ্রী
একটা অনুভূতি হয়। তবে গলা পরিষ্কারসহ পেটের উপকারের জন্য এই চায়ের নাকি বিকল্প নেই!
আপ্তবাক্য মেনে নিয়ে দ্বিতীয় কাপের জন্য অপেক্ষা করেন। কিছুক্ষণ পর আসে ঘন চিনি দেওয়া
লেয়ার চা। এই চা তৈরির ফর্মুলা আলাদা। পান করার চেয়ে চেয়ে দেখায় বেশি আনন্দ। লালচে
লিকারের নিচে ঘন সাদা চিনির স্তর। কেউ কারো সীমানা অতিক্রম করছে না। তিনি চিনির ওপরের
স্তরের লাল লেয়ারটুকুতে ধীরে ধীরে চুমুক দেন। চিনির অংশ ভুলেও মুখে দেন না। এত ঘন চিনি
তার স্বাস্থ্যের জন্য ভালো না। ডায়াবেটিস না থাকলেও তিনি বেশি মিষ্টি জাতীয় খাবার এড়িয়ে
চলেন। দ্বিতীয় কাপ চা খাওয়ার পরপরই তৃতীয় এবং শেষ কাপ চা মুখে দেন। এই চা খাঁটি দুধের
তৈরি। ওপরে হালকা সর ভাসে। চিনি হতে হয় পরিমান মতো। জহুরা লিকার আর রং চা ভালো বানালেও
দুধ চা বানাতে পারে না। দুধ-চিনির পরিমাণে গ-গোল পাকিয়ে ফেলে। লিকারের ব্যাপারটাও ঠিকমতো
ধরতে পারে না। তাই দুধ চা-টা বাইরে থেকে ফ্লাস্কে করে আনাতে হয়। তালাত মিয়া দুধ চা
ভালো বানায়। দোকানের তালা খুলে রোজ প্রথম যে কাজটা করে তা হলো মফিজুল সাহেবের জন্য
চা বানানো। যে-সে চা না, সর ভাসা স্পেশাল দুধ চা।
হাফিজুল হক মোটামুটি
কঠিন সময় পার করছেন। পদার্থের তিন অবস্থার মতো মানুষের জীবনেও তিনটা পর্যায় থাকে। কঠিন,
তরল ও বায়বীয়। তার জীবনে বায়বীয় সময় তেমন আসেনি বললেই চলে। এটা ভালো না মন্দ বোঝা মুশকিল।
কঠিন আর তরলের মধ্যেই জীবনের বেশিরভাগ সময় পেরিয়ে গেছে। এখন তিনি তরল সময়ের জন্য অপেক্ষা
করছেন। এই কঠিন সময় কেটে গেলেই তিনি তরলের মধ্যে ডুব দিবেন। দীর্ঘ একটা ডুব।
রুটিন মেনে কাজ করা মানুষের জীবন আর অনুভূতিশূন্য যন্ত্রের
মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই। রুটিন মানা মানুষ অনেকটা চিরতার পানির মতো। ফল ভালো হলেও
স্বাদ তিক্ত।
হাফিজুল হক রুটিনের বাইরের মানুষ। দুটি কাজ কখনো ঠিক মতো করতে
পারেন না কথা দিয়ে তা রক্ষা করা আর ঘড়ির সময় ধরে ওঠা-বসা করা।
কথা দিয়ে না রাখার ব্যাপারে তার নিজের ভূমিকা সামান্য। তিনি
সচেতনভাবে লক্ষ্য করেছেন, প্রকৃতিই সেটা চায় না কিংবা হতে দেয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই
তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি ভুলে যান। লোকে ভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে কাজটি করেন।
ব্যাপার তা না। মস্তিষ্কের কোষ অপ্রয়োজনীয় বিষয় মুছে ফেলে মেমোরি খালি করতে চায়। প্রতিশ্রুতি
হয়তো তার মস্তিষ্কের কাছে তেমন অপ্রয়োজনীয় একটা ব্যাপার!
সময় মেনে কাজ করতে পারেন না বলে কখনো হাতে ঘড়ি পরেন না। কাউকে
সময়ও জিজ্ঞেস করেন না। যে জিনিস নিজের কাছে নেই অন্যকে তার মুখাপেক্ষী হতে বাধ্য করবেন
কেন? তাছাড়া সময় জানতে চাওয়ার অর্থ তাকে বাস বা ট্রেন ধরার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে
হবে। দু-চার মিনিট এদিক-সেদিক হলেই গাড়ি মিস! তার যেহেতু গাড়ি ধরার চিন্ত নেই তাই সময়
নিয়েও তেমন ভাবনা নেই।
চা-পর্ব শেষ হলে তিনি গোসলখানায় ঢোকেন। তার ধারণা এ জায়গা থেকেই
বেশিরভাগ সৃজনশীল কাজের সূচনা হয়। শর্ত একটাই, নেতিবাচক চিন্তা মাথায় আনা যাবে না।
দুর্ভাবনামুক্ত থাকার যাবতীয় আয়োজন গোসলখানায় করা আছে। হালকা মিউজিকের ব্যবস্থা রেখেছেন।
ওয়েস্টার্ন ধাঁচের। কথা কম, বাদ্য বেশি। আরামদায়ক বাজনা। এটা মাথা ঠান্ডা রাখে। তিনি
কখনো স্নানঘরের দরজা বন্ধ করেন না। বন্ধ থাকে শোবার ঘরের দরজা। স্নানের সময় দরজা খুলে
রাখার বেশকিছু সুবিধা রয়েছে।
দরজা খুলে রাখার ফলে রুমের এসির বাতাস বাথরুমে ঢুকে আরামদায়ক
পরিবেশ সৃষ্টি করে। গুমোটভাব অনেকটাই কেটে যায়। তাছাড়া তিনি চার দেয়ালে বন্দী অবস্থায়
গোসল সারতে পারেন না। জানালাবিহীন চার দেয়াল মানেই এক প্রকার হাজতখানা। তিনি কোন দুঃখে
হাজতখানায় বসে গোসলের মতো জরুরত সারবেন!
গোসলের প্রথম পর্যায়ে শীতল পানিতে কিছুক্ষণ শরীর ডুবিয়ে রাখেন।
এ বয়সে মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখা খুব জরুরি। ঠাণ্ডা মেজাজের জন্য আরামদায়ক শীতল বাথের
বিকল্প নেই।
উদল গায়ে পানির মধ্যে শুয়ে আছেন হাফিজুল হক । তার কাক্সিক্ষত
চিন্তাগুলো একে একে এসে হাজির হচ্ছে। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারলে কঠিন ব্যাপারও
সহজে গলে যায়। তিনি তেমন একটা বিষয় গলানোর চেষ্টা করছেন।
এ কাজটা তাকে বেশ ভোগাচ্ছে। লেখালেখি তার কাছে চরম আনন্দদায়ক
ব্যাপার। জীবনের সিরিয়াস বিষয়গুলোর তালিকা করলে লেখালেখি থাকবে এক অথবা দুই নম্বরে।
শুনতে খারাপ লাগলেও তার অনেক লেখার থিম মাথায় এসেছে বাথরুম থেকে, গোসলের সময়। তা বলে
তাকে ‘বাথরুম রাইটার’ উপাধি দেওয়ার বোকামি করা যাবে না। লেখক হিসেবে জনপ্রিয়তার সঙ্গে
তার অর্জনের ঝুলিও কম সমৃদ্ধ নয়!
হাফিজুল হক আটকে আছেন উপন্যাসের শেষ অনুচ্ছেদে। পুরো উপন্যাস
নিয়ে তিনি নানা ধরনের খেলা খেলেছেন। শেষ ভাগে এসে মনে হচ্ছে পুরো খেলাই গোলশূন্য ড্র!
তবু তিনি নাছোড়। উপন্যাস শেষ করতে না পারার যন্ত্রণা বয়ে বেড়ানো যাবে না। যত দ্রুত
সম্ভব মাথা থেকে বোঝা নামাতে হবে। সমস্যা হলো, জগতের অনেক বিষয় মানুষের হাতে থাকে না।
অদৃশ্য কোনো হাত এসে সেটা আটকে দেয়। তিনিও একটা অদৃশ্য হাতের অস্তিত্ব অনুভব করছেন।
হাতটা মেয়েদের হাতের মতো মোলায়েম কিন্তু একরোখা, দৃঢ় ও কঠিন।
এটা নিজে থেকে সরবে নাকি জোরপূর্বক তাকেই তাড়াতে হবে ঠিক বুঝে
উঠতে পারছেন না। আচ্ছা, ওটা যদি কখনোই দূর না হয়! একটা উপন্যাস অসমাপ্ত রেখে যাওয়ার
অতৃপ্তি তাকে বাকি জীবন বয়ে বেড়াতে হবে। তিনিও এ ব্যাপারে যথেষ্ট কঠিন। এটা শেষ না
করে নতুন কোনো লেখায় হাত দিবেন না। হতে পারে এটাই তার শেষ লেখা! প্রকৃতির সঙ্গে তার
চলমান দ্বন্দ্ব মস্ত একটা খেলা, অপ্রত্যাশিত বাজি।
২
গোসলের পর শরীর একটা জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়। তরল থেকে
বায়বীয় অবস্থার মধ্যে শরীরকে ছেড়ে দেওয়ার এ সময়টাকে হাফিজুল হক বেশ উপভোগ করেন। এসির
তাপমাত্রা কমিয়ে দেন। সঙ্গে ফুল স্পিডে ফ্যান চলে। অন্য কেউ হলে এমন ঠান্ডা সহ্য করতে
পারত না। তিনি তোয়ালে পরে দিব্যি ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করেন। এটা তার গল্প সাজানোর
সময়। মাথার সঙ্গে শরীর শীতল রাখাও জরুরি।
একটা প্লটের ওপর তিনি চরিত্রগুলো ছেড়ে দেন। তারা ইচ্ছেমতো ঘোরাফেরা
করে। তিনি বাধা দেন না। গল্পের বাইরের মানুষের মতো গল্পের ভেতরের মানুষেরও স্বাধীনতা
থাকা উচিৎ। তিনি সে স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার ঘোর বিরোধী। চরিত্রগুলো ঘুরতে ঘুরতে
একটা বিন্দুতে গিয়ে স্থির হয়। তিনি সেই স্থিরবিন্দু থেকে শুরু করেন।
হাফিজুল হকের লেখার ধরনটা ভিন্ন। তিনি চরিত্র নিয়ে কাজ করেন।
একেকদিন মস্তিষ্কের কোষে একটা মুখের ছবি এঁকে নেন। সেই মুখোশের ভেতরের মানুষকে দিয়েই
গল্প সাজান। গল্প সাজানো শেষ হলে লিখতে বসেন। লেখার ফাঁকে সাদা আর্ট পেপারে পেন্সিলের
টানটোন চলতে থাকে। এক সঙ্গে দুই কাজ। এটা তার সহজাত ব্যাপার। তার ধারণা, মস্তিষ্ক যুগপৎ
এই ব্যাপারটা পছন্দ করে। তার নিজেরও বিশ্বাস, এর যে কোনো একটা ব্যতিরেকে অন্যটি চলতে
পারবে না। মানুষের চোখ বা কিডনির মতো এক জোড়া থেকে একটা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলে আরেকটা
দিয়ে কাজ সারা সম্ভব হবে না। গল্প শেষ হতে হতে চরিত্রটির একটা অবয়ব দাঁড়িয়ে যায়। তিনি
তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। তবে প্রায় সময়ই অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটে, তার আঁকা অবয়বের
মধ্যে জীবনের কোনো এক সময়ে তার নিজের বা অতি পরিচিত কারো মুখচ্ছবির মিল খুঁজে পান।
তিনি চমকে ওঠেন। এটা ইচ্ছাকৃত না হলেও দেখতে মন্দ লাগে না!
তরল ও বায়বীয় অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে একটা মানুষ কঠিন সময় পার
করছে প্রকৃতির খেয়াল বোঝা বড় দায়। হাফিজুল হক প্রকৃতির খেয়াল বোঝার বৃথা চেষ্টা করছেন
না। গল্প গোয়ালের গরু-ছাগল না যে তাকে টেনে-হিঁচড়ে বের করতে হবে। তিনি স্থিরাবস্থার
মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকে না। তারাও একসময় চলতে শুরু করে।
তার এই স্থিরাবস্থার মধ্যেও নিশ্চয় ভালো কিছু আছে। আরো দ্রুত গতিতে চলার জন্য একটা
বিরতির প্রয়োজন হয়। কাহিনিও হয়তো নীরব বিরতি পছন্দ করে! তিনি বিরতি শেষের সেই ভালোর
জন্য অপেক্ষা করছেন।
আপাতত হাফিজুল হকের মাথায় কোনো গল্প নেই, হাতে কিছু স্কেচ আছে।
তিনি স্কেচগুলো সিরিয়ালি সাজাতে থাকেন। এক, দুই করে উনিশটা
মুখের স্কেচ হয়ে গেছে!
কুড়িতে গিয়ে থামবেন তিনি। আগে গ্রামে-গঞ্জে কুড়িতে গিয়ে বুড়ি
হওয়ার একটা প্রবাদ ছিল। এখন সে দিন নেই। কুড়ি থেকেই যৌবনের গাড়ি চলতে আরম্ভ করে। তবে
তার গল্পের যৌবন মেষ হয়ে এসেছে। আর একটা মুখের জন্যই কেবল অপেক্ষা।
ক্রিকেট খেলায় ‘ব্যাডপ্যাঁচ’ বলে একটা শব্দ আছে। ব্যাটসম্যানরা
যখন খারাপ সময় পার করে, আগে যে বল শুয়ে-বসে চার মারত এখন তেমন বলে হরহামেশা আউট হচ্ছে
তখন তাদের ‘ব্যাডপ্যাঁচ’ চলে। এটা কাটিয়ে ওঠার সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি হলো, নিজের সুসময়ের
ভালো ইনিংসগুলোর ভিডিও দেখা। এতে আত্মবিশ্বাস বাড়ে। নতুন করে শুরু করা যায়। তার নিজের
লেখার ভিডিও না থাকলেও নিজ হাতে আঁকা স্কেচ আছে। আপাতত সেগুলোর দিকে তাকিয়ে চরিত্রগুলোতে
ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করা যায়। এটা কাজে দিতে পারে। প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করা হলেও পরীক্ষার
আগে রিভিশন দেওয়ার ব্যাপার থাকে। ভালো ছাত্ররা রিভিশন দিতে কখনো ভুল করে না। তিনি ভালো
লেখক কিনা জানেন না, তবে লেখার শেষ প্রান্তে এসে তেমনিভাবে একবার রিভিশন দেওয়া যেতেই
পারে।
৩
যখনই প্রথম স্কেচটি হাতে নেন, নিজের ভেতর একটা পবিত্র সত্তার
উপস্থিতি অনুভব করেন হাফিজুল হক। তিনি আঁকার সময় ভাবেননি এ মুখটাতে এত মায়া ভর করবে।
আঁকার পর বিষয়টি চোখে পড়ে। ছেলেটির ঠোঁটের কোণে নিষ্পাপ হাসি যেন তার আরোপিত নয়, এটা
নির্ধারিতই ছিল। তিনি যতবার তাকান, মুগ্ধতার ঘোর সহজে কাটতে চায় না। তার মেয়ে অর্পা
যেদিন ছবিটা প্রথম দেখে, প্রবল বিস্ময়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিল।
‘বাবা, ছবিটার
মধ্যে লাজুক একটা ভাব আছে, খেয়াল করেছ?’
‘না তো! ছবি এক
হলেও এর ভাষা ধ্রুব নয়, আপেক্ষিক। একেকজনের চোখে একেকভাবে ধরা দেয়।’
‘তোমার কথা ঠিক
আছে, তবে আমি কারণটা ব্যাখ্যা করি।’
অর্পার ভেতর শিক্ষক শিক্ষক একটা ভাব আছে। মেয়েটা কথা বলার সময়
নির্মোহ থাকে। আবেগের চেয়ে যুক্তিকে প্রাধান্য দেয়। যখন কথা বলা শুরু করে তখন রেল
লাইনের মতো সমান্তরালভাবে চলতেই থাকে। পরবর্তী গন্তব্যে না পৌঁছানো অবধি থামে না। একনাগাড়ে
অনেক কথা বললেও কোনো শব্দ শুনতে বা বুঝতে অসুবিধা হয় না। প্রতিটা কথা স্পষ্ট, তীব্র।
অপ্রয়োজনীয় কথা তেমন বলে না। ওর সঙ্গে কথা বলে তৃপ্তি পাওয়া যায়। মেয়েটাও তাকে যথেষ্ট
পছন্দ করে, সময় দেয়। তার একটা লেখা শেষ হলেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে। ভালো লাগা, মন্দ
লাগার ব্যাপারগুলো স্পষ্টভাবে জানায়। হাফিজুল হক তার মেয়ের প্রতিটি মতামত গুরুত্বের
সঙ্গে নেন। মেয়েটার জন্যই লেখার সময় তাকে সাবধানী হতে হয়। সস্তা বা স্থূল লেখা লিখে
বিপদে পড়ার চেয়ে আগে থেকে সতর্ক হওয়া ভালো।
অর্পা হাত নেড়ে নেড়ে বলে, ‘শিশুরা হাসলে সাধারণত তাদের দাঁত
বের হয়। অথচ এ ছবিতে ছেলেটার মুখে হাসি থাকলেও দাঁত দেখা যাচ্ছে না। আবার সে যে জোর
করে ঠোঁট চেপে আছে তেমনও নয়। আরেকটা বিষয় লক্ষ করো, তুমি যদি মুখের হাসিটা আরেকটু বিস্তৃত
করতে, বিষয়টা ছেলেমানুষির মতো হয়ে যেত। তুমি তা করোনি। আবার চোখ দুটোকেও কিঞ্চিৎ ছোট
করে এঁকেছ। তার মানে ছবিটা একই সঙ্গে লাজুক, বুদ্ধিদীপ্ত, নিষ্পাপ এবং সরল হয়ে উঠেছে।
হাফিজুল হক বরাবরের মতো মুগ্ধ হয়ে মেয়ের বিশ্লেষণ শুনছিলেন।
পরীক্ষার খাতায় যেমন প্রশ্নের ব্যাখ্যামূলক উত্তরের জন্য নম্বর দিতে হয়, তেমনিভাবে
মেয়ের বিশ্লেষণের জন্যও মনে মনে নম্বর দেওয়া যেতেই পারে। দশের ভেতর কত দেওয়া যায়? পুরো
দশ না দিলেও সাড়ে নয়ের কম দিলে মেয়েটার প্রতি অন্যায় করা হবে। তিনি শিক্ষক নন, তবু
এ ধরনের অন্যায় করতে পারেন না। তাই নয় দশমিক পাঁচ শূন্য দিলেন।
হাফিজুল হকের ছেলেবেলার কোনো ছবি নেই। তখন গ্রামের বাড়িতে থাকতেন।
একবার ঘরে আগুন লেগে ঘরের সবকিছু পুড়ে যায়। মায়ের মুখ থেকে শুনেছিলেন পুড়ে যাওয়া জিনিসের
মধ্যে তার দুই বছর বয়সের একটা সাদাকালো ছবি ছিল। তিনি যত্নে শাড়ির ভাঁজে রেখেছিলেন।
স্কুলের ফরম পূরণের আগে আর কোনো ছবি তোলা হয়নি। স্মৃতি ধরে রাখায় প্রয়োজনীয়তা তখন অনুভূত
হয়নি। অনেকেই ছেলে-মেয়েদের কাছে নিজের শৈশব-শৈশরের ছবি দেখিয়ে স্মৃতির ঝাপি খুলে দেয়।
ডিএসএলআরের যুগে সাদাকালো ছবির প্রতি অনাগ্রহ থাকলেও ছেলে-মেয়েদের বাধ্য হয়ে তা দেখতে
হয়। শুধু দেখলেই চলে না, আশ্চর্য হওয়ার ভান করতে হয়। তার কোনো ছবি না থাকায় ভিন্ন পথ
অবলম্বন করতে হয়। গল্প করার সময় কল্পনায় একটা ছবি এঁকে নিতে হয়। তার ছেলে-মেয়ের সৌভাগ্য,
সে ছবি দেখে বিস্মিত হওয়ার অভিনয় করতে হয় না।
তার বিশ্বাস, ছবি দেখলেও তারা বিস্মিত হতো না। হয়তো হাতে নিয়ে
‘ও, আচ্ছা’ বলে একনজর দেখে রেখে দিত।
অর্পা অবশ্য এ ছবিটা নিয়ে যথেষ্ট কৌতুহলী।
‘তুমি দেখতে কেমন ছিলে বাবা? কোনো ধারণা দিতে পারো? ধরো, দাদিজান
কি কখনো বলেছিল, ছোটবেলায় তুমি দেখতে আরও সুন্দর ছিলে, চোখ দুটো ছিল ভাসা ভাসা। গায়ের
রং ছিল দুধে-আলতা?’
‘আমি কখনোই মা-ঘেঁষা ছিলাম না। তাই এমন করে গল্প শোনাও হয়নি।
এখন তার অনুপস্থিতিতে এ জন্য বড় আফসোস হয় রে!’
‘তাহলে ছবির পুরোটাই তোমার কল্পনা থেকে এসেছে?’
‘তা বলতে পারিস।’
‘আচ্ছা, এমন কারো সঙ্গে ছেলেবেলায় তোমার বন্ধুত্ব ছিল বা পরিচিত
কারো চেহারা এমন ছিল?’
‘থাকতে পারে। মস্তিষ্ক
হুট করে কিছু তৈরি করে না। পুরনো কোনো বিষয়ের সঙ্গে সাযুজ্য খোঁজে। এক্ষেত্রেও তেমন
হতে পারে।’
‘তুমি গল্পে বলেছ
ছেলেটা এতিমখানায় বড় হয়েছে। এটাও কি কাল্পনিক?’
‘আমাদের বাড়ির
খুব কাছেই একটা এতিমখানা ছিল। সেখানে দল বেঁধে বাচ্চাদের আসা-যাওয়া দেখতাম। বাড়িতে
কোনো অনুষ্ঠান বা খানা-দানা হলে তাদের ডেকে আনা হতো। তারা কড়া নিয়মের মধ্যে বেড়ে উঠত।
ইচ্ছেমতো যখন-তখন বাইরে বের হতে পারত না। তবে কিছু ছেলে ব্যতিক্রম ছিল। তারা সুযোগের
অপেক্ষায় থাকত। সুযোগ পেলেই বাইরে চলে আসত। এমন দু-একজনের সঙ্গে আমার সখ্য হয়েছিল।
তবে তা খুব অল্প সময়ের জন্য।’
‘তেমন কাউকে কল্পনা
করেই কি স্কেচ শুরু করেছিলে?’
‘শুরুর সময় কী
ভেবেছিলাম এখন ঠিক মনে করতে পারছি না। তবে শেষমেশ যা দাঁড়িয়েছে তাতে আমি খুশি।’
স্কেচের ছেলেটির ব্যাপারে অর্পার কৌতুহল বাড়তে থাকে। সে তার
বাবার সঙ্গে ছেলেটির যোগসূত্র উদ্ধারে সচেষ্ট। তার বাবা মেয়ের এই কৌতুহলী চেহারা দেখে
তৃপ্তি পান। মেয়ের অতৃপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে চিকন একটা হাসি দেন। কিছু ঘটনা মেয়ের কাছে
বলা যায় না বলে ইচ্ছে করে আড়াল করেছেন। এতিমখানা থেকে লুকিয়ে-চুরিয়ে বেরিয়ে আসা ছেলেগুলো
ছিল বদে হাড্ডি। তার একটা হাফপ্যান্ট ছিল। প্যান্টের চেন ছিল না। হয়তো কেটে গিয়েছিল!
তাদের একজন ওদিক দিয়ে কবে নাকি গোপন জিনিস দেখেছিল! সেই কথা এতিমখানার সবাইকে জানিয়ে
দিয়েছিল। দেখা হলেই ছেলেগুলো তাকে ‘ন্যাংটাবাবা’ বলে ডাকত। সে লজ্জা আর ক্ষোভে ফেটে
পড়ত। কিছুই করার ছিল না বলে তাদের থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করত।
৪
প্রথম স্কেচের মায়াবী ছেলেটির নাম নাহিদ। এটা লেখকের আরোপিত
নাম। তিনি যে সময়ের গল্প বলছেন সে সময়ে মফস্বলের মোটামুটি আধুনিক নাম বলা যেতে পারে।
নাহিদের অবস্থান যদি গল্পের কেন্দ্রে হয় তবে অনিকেত তার চারপাশের একটা গুরুত্বপূর্ণ
বিন্দু। কেন্দ্রের ওপর যার প্রভাব আছে। হাফিজুল হকের হাতে ধরা দ্বিতীয় স্কেচটি অনিকেতের।
অনিকেত নামটার মধ্যেই রহস্যের গন্ধ আছে। হালকা গন্ধ না, গড়া
টাইপের গন্ধ। বিশেষ করে এতিমখানায় বেড়ে ওঠা কোনো বালকের নাম অনিকেত হওয়া অসম্ভবের পর্যায়ে
পড়ে। হয়তো ওটা তার প্রকৃত নাম ছিল না। তবে কাহিনির ভেতরে কিছু রহস্যজনক বিষয় সচেতনে
ঢুকিয়ে দিতে হয়। যেগুলোর যুতসই ব্যাখ্যা শুধুমাত্র লেখকের কাছে থাকে। পাঠক যে যার মতো
ভেবে নিতে পারে। অনিকেতের নামের ব্যাপারে তিনি সে পথেই হেঁটেছেন। তার কাছে এ চরিত্রটির
গুরুত্ব কম নয়। নাহিদকে আঁকতে গিয়ে অনিকেতকে অবহেলা করেছেন বলে মনে পড়ে না। গল্পের
পরবর্তী ধাপ নির্মাণের জন্য অনিকেতের জোর ভূমিকা রয়েছে।
.
অনিকেতে অর্পাও মুগ্ধ হয়েছে। যদিও তা অপ্রকাশ্য। কিন্তু তিনি
বেশ বুঝতে পারেন। হয়তো তার বাড়তি আকর্ষণের জন্য অর্পা বিষয়টি প্রকাশ করে না। অর্পার
মতো জেরা করে ঘটনার নেপথ্যের কথা বের করার ক্ষমতা তার নেই।
‘কী রে মা, অনিকেতকে
নিয়ে তোর পর্যবেক্ষণ কেমন শুনি।’
‘অনিকেত সিগারেটের
ধোঁয়ার মতো। একটা বলয় তৈরি করে। তার কাছে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক না, কিন্তু চাইলেই দূরে
সরা যায় না। নাহিদ যেমন পারেনি অনিকেতের বলয় অগ্রাহ্য করতে।’
হাফিজুল হক স্কেচ দুটি পাশাপাশি রাখেন। দুজনেই সমবয়সী বালক।
অথচ একজন দুর্বোধ্য, আরেকজনের স্কেচ দেখলেই গড়গড় করে মনের খবর বলে দেয়া যাচ্ছে! অনিকেতের
চেহারার মধ্যে সারল্যের চেয়ে প্রকাশ্য বিষয় বেশি। এটা তিনি ইচ্ছে করেই করেছেন। নাহিদের
জীবনের গতিপথ বদলে দিতে অনিকেতের ভূমিকা সমধিক।
.
সে বড় অবাধ্য সময়। মানুষ সময়কে অবাধ্য হতে বাধ্য করে নাকি সময়
মানুষকেÑ সেটি তর্ক সাপেক্ষ হলেও তারা দুজনেই স্বাভাবিক নিয়মের অবাধ্য হয়েছিল। নাহিদের
একার পক্ষে যা করা কল্পনাতীত ছিল, তা-ই সম্ভব হয়েছিল অনিকেতের সাহচর্যে। এতিমখানার
অচলায়তন ভেঙেছিল তারা। নাহিদের সংকোচ খুব দ্রুত কেটে যায়। অনিকেত তাকে চুম্বকের মতো
স্পর্শ করে। একটা ভিন্ন জগতের সন্ধান পেয়েছিল নাহিদ। যেখানে চাইলেই সবকিছু করা যায়।
নিয়মের বেড়াজাল নেই। শাসন নেই, বারণ নেই। রাত করে ঘরে ফিরলে চোখ রাঙানির ভয় নেই।
.
একদিনের ঘটনা। পড়া না পারায় স্যারের কাছে অপমানিত হয় নাহিদ।
আগে কখনো এমন হয়নি। যত যাই করুক পড়াশোনার জায়গাটা ঠিক রেখেছিল। আগের রাতে পালিয়ে অনিকেতের
সঙ্গে টেলিভিশন দেখতে গিয়েই ঝামেলা হয়েছিল। বেশ রাত হওয়ায় অনিকেতের কথা মতো তারা না
ফেরার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই প্রথম নাহিদ এভাবে বাইরে রাত কাটায়। এতিমখানার কেউ অনিকেতের
ভয়ে বিষয়টা ফাঁস করবে না জানত বলেই নাহিদ সাহস পেয়েছিল। তারপরও সে চিন্তামুক্ত হতে
পারছিল না। সবকিছুর সমাধান অনিকেতের কাছে আছে। চিন্তামুক্ত থাকার দাওয়াাই দিয়েছিল সে।
বিড়ির শলাকা সে রাতেই প্রথম হাতে নিয়েছিল নাহিদ। অনিকেত আগে থেকেই টানত। কিন্তু বস্তুটা
যে এত কাজের আগে বুঝতে পারেনি। ওই জিনিসটার
জন্য হলেও অনিকেতের প্রতি আসক্তি বেড়ে যায়।
ভোরে এতিমখানায় ফিরে পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারেনি। ঝিমুনি উপেক্ষা
করে বই নিয়ে বসে থাকাই সার। মাথায় কিছু ঢোকে না। ফল যা হওয়ার তাই! প্রথমবারের মতো পড়া
বলতে না পারার লজ্জা সঙ্গী হয়। লজ্জা কাটানোর উপায় নিয়ে বরাবরের মতোই এগিয়ে আসে অনিকেত।
এবার ডাবল ডোজ! একটার জায়গায় দুটো বিড়ি টানতে হবে! নাহিদ সবকিছু মানতে পারে অপমান ছাড়া।
দুটো বিড়ি টানার পরও অস্বস্তি দূর হয় না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে জীবনে আর কখনো পড়ালেখার
জন্য কথা শুনবে না। ওটাই মূল জায়গা। সেখান থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না। এটা নিজের মধ্যে
রেখেই অনিকেতের সঙ্গে মেশে। সুযোগ পেলেই পালিয়ে গিয়ে টেলিভিশন দেখে, তাস খেলে। ফিরে
এসে ঠিকই পড়া মুখস্ত করে।
.
এতিমখানা থেকে পালিয়ে বাইরে যাওয়া নেশার মতো হয়ে যায়। বাইরের
সময়টা অনিকেতের সৌজন্যে দারুণ কাটে। ভেতরের সময়টা ভালো কাটানোর ব্যবস্থা নাহিদকেই করতে
হয়। পড়াশোনা। সে তা পারে। শান্ত এবং উড়ন্ত দুই জীবনকে পাশাপাশি নিয়ে চলতে হয়। তাতে
একঘেয়েমি আসে না। শুধু সাদাকালো বা শুধু রঙিন ছবি দেখতে দেখতে য়েমন ক্লান্তি আসে, নাহিদ
তা থেকে মুক্ত। এমন একটা জীবনের জন্য আবারও সে অনিকেতের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়।
.
একটা দুর্ঘটনা নাহিদের জীবনকে ওলট-পালট করে দেয়। যদিও সে ঘটনার
সঙ্গে তার সংশ্লিষ্টতা ছিল না। ঘটনার সূত্রপাত বিড়ির প্যাকেট নিয়ে। অনিকেতের বালিশের
নিচে পেয়েছিল রিপন। অনেকদিন ধরেই রিপন আর অনিকেতের মধ্যে মনোমালিন্য চলছিল। অনিকেত
নানাভাবে তাকে অপমান-অপদস্থের মাধ্যমে কোণঠাসা করে রেখেছিল। রিপন শুধু সুযোগের অপেক্ষায়
ছিল। সুযোগ পেলেই দেখে নেবে এমন অবস্থা। বিড়ির প্যাকেটটা সে সুযোগ করে দেয়। সোজা গিয়ে
মন্টু স্যারের হাতে তুলে দেয় আলামত। মন্টু স্যার এমনিতেই রগচটা টাইপের। প্রচলিত ছিল,
তিনি নাকি সঙ্গে বাঘ নিয়ে ঘোরেন। তার চোখের দিকে তাকিয়ে কেউ কথা বলার সাহস পায় না।
সেখানে এত বড় অন্যায় বরদাস্ত করার প্রশ্নই ওঠে না। এতিমখানার শাস্তি ছিল ভয়ঙ্কর। উদাহরণ
দেওয়া যাক, শাস্তির বিবিন্ন ভাগ ছিল। অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি নির্ধারণ করা হতো।
গুরুতর শাস্তি, মধ্যম শাস্তি, লঘু শাস্তি এবং মৌখিক সতর্কতা।
অনিকেতের অপরাধ গুরুতর। কাজেই তাকে গুরুতর শাস্তি ভোগ করতে
হবে। তা হলো দুই হাতে ইট নিয়ে সূর্যের দিকে এক বেলা তাকিয়ে থাকা। এ পর্যন্ত হলে ঠিক
ছিল। অপরাধ অনিকেতের, তার শাস্তি পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ঝড় যখন একবার বইতে শুরু করে
তখন তার হাওয়া আশপাশের মানুষের গায়ে লাগে। এই হাওয়া যেমন নাহিদের গায়েও লাগল। অনিকেতের
বিড়ি খাওয়ার সঙ্গী হিসেবে নাহিদের নাম কেউ একজন ফাঁস করে দিয়েছিল। তাতেই তার জন্য লঘু
শাস্তির হুকুম হলো। এই শাস্তিতে শারীরিক কষ্টের চেয়ে মানসিক কষ্ট বেশি। সবার সামনে
এক হাজার বার কান ধরে ওঠা-বসা করা।
.
পরদিন সকালে শাস্তি শুরু হবে। অনিকেত নির্বিকার। সম্ভাব্য অপমানের
কথা চিন্তা করে নাহিদ ভেঙে পড়ে। তার শাস্তি পাওয়ার বিষয়টি কিছুতেই মেনে নিতে পারে না।
অনিকেতের সঙ্গে মেশাটাই কি তবে ভুল হয়েছে!
নাহিদের ঘুম আসে না। এই দিনটাকে যদি জীবনের খাতা থেকে মুছে
ফেলার মতো তার যদি একটা ইরেজার থাকত! শেষ রাতের দিকে অনিকেত চুপিচুপি তার কাছে হাজির
হয়। সে জানায়, এতিমখানা ছেড়ে একেবারে পালিয়ে যাবে। শাস্তি এড়ানোর এটাই একমাত্র পথ।
নাহিদ চাইলে তার সঙ্গে যেতে পারে। ক্লাসের পরীক্ষায় বরাবরই সাফল্যের সঙ্গে উতরে যাওয়া
নাহিদ যেন জীবনের কঠিনতম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়! সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বেশি সময় পায়
না। অপমান এড়াতে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ খোলা না থাকায় সেও অনিকেতের সঙ্গী হয়।
শঙ্কা আর অনিশ্চয়তা সঙ্গে করে তারা দুজনে এতিমখানা থেকে পালিয়ে
যায়। নিশুতি রাত দুজন বালকের অন্তর্গত হাহাকারের গল্প লিখে রাখে। যে গল্পের ভবিষ্যত
অনিকেত বা নাহিদ কেউ জানে না।
চলবে...