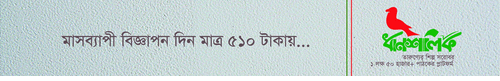রামবন্দনা
শাদমান শাহিদ
(গত সংখ্যার পর)
কদিন পরেই সব স্বাভাবিক। আকাশের তলায় সূর্যটা যথারীতি পুবদিক থেকেই ওঠে। মাটিও সবুজময়। কোনো গাছেই ফুল-ফল আটকে নেই। যাপিত জীবনও মন্দ চলছে বলে মনে হয় না। মুখে বিষাদ ছড়িয়ে রাখলেও, বাজারের কোনো পণ্য থেমে নেই। কলেজপাড়া, ব্যাংকপাড়া, মাগীপাড়া কোনো পাড়াতেই খরার চিহ্ন পর্যন্ত চোখে পড়ে না। পাবলিক পরীক্ষার রেজাল্টও চমকপ্রদ। পাশের হার সাতানব্বই-আটানব্বই। এসএসসি’তে প্রতিষ্ঠান মাত্রই ‘এ-প্লাস’-এর ছড়াছড়ি। প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলো টাকা দিয়ে কিনে নেয় পত্রিকার পাতা। ফোর কালারের ছবিতে ভেসে যায় পত্রিকার শরীর। আনন্দে ভেসে ওঠে সারাদেশ। আনন্দ নেই কেবল বুদ্ধিজীবীদের কণ্ঠে। তাঁরা বলে—‘হচ্ছে না, কিছুই হচ্ছে না। কোমলমতি শিশুদের মেধা নিয়ে এতোবড়ো জোচ্চোরি কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না।’ আমাদের সরস্বতী সেদিকে কান দেন না। তিনি তো খুশিতে বাকবাকুম। বলেন, জাতির মেধাকে আকাশে তোলার জন্যে স্বয়ং মহাদেব তাঁকে পাক-কাদার দেশে পাঠিয়েছেন। শুনে খুশি আমরাও। অভিভাবকরা দৌড়ে যায় ময়রার দোকানে। মিষ্টি খেতে খেতে মনে হয়, আমরা যেনো কোনো সিরামিক কারখানার মেশিন থেকে বেরিয়ে এসেছি। দেহ মনে নতুন নকশার ঝিলিক। পুরোনো স্মৃতি ভুলে গিয়ে মগজে তখন নতুন প্রত্যয়। নতুন প্রত্যয়ে বিভোর হয়ে অভিভাবক বাচ্চা নিয়ে পাড়ি জমায় কলেজের সবুজ ঘাসের আঙিনায়। কিন্তু তাদের ছেলে-মেয়েরা সরকারি কলেজে ভর্তি হতে পারে না। আইন-গাইন আর কোটার ভিড়েই সরকারি কলেজের শ্রেণিকক্ষগুলো ফেটে যায়। তখন জনসাধারণকে দৌড়াতে হয় প্রাইভেট পট্টিতে। এ-দেশে এটা একটা চমৎকার ব্যবসা। কোনো রিক্স নেই। প্রতিবছরই সরকার শতকরা হার বৃদ্ধির জন্যে পোনার ঝাঁকের মতো লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীকে এসএসসি পাশ করিয়ে স্কুল থেকে বের করে দেয়। যাদেরকে পরবর্তী শ্রেণিতে ভর্তি করানোর মতো পর্যাপ্ত প্রতিষ্ঠান সরকারের হাতে থাকে না। তখন বাধ্য হয়ে দিশেহারা শিক্ষার্থীরা ব্যাঙের ছাতার মতো যত্রতত্র গজিয়ে ওঠা প্রাইভেট কলেজ নামে বেড়জালে প্রবেশ করে। প্রবেশ করার পর বুঝতে পারে ভুল গলিতে ঢুকে পড়েছে তারা। তখন কিছুই করার থাকে না। দু’বছরের মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওখানেই থাকতে বাধ্য। ফলে এসব প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া যেমন-তেমন হিসাবের খাতা কড়া। এক টাকা বকেয়া রেখে একজন শিক্ষার্থীও এসব গরাদ থেকে বের হতে পারবে না।
এমন গলাকাটা ব্যবসার রহস্যটা আমাদের কাছে উন্মোচিত হওয়ার পরও আমাদের কিছু করার থাকে না। অভিভাবকগণ ছেলে-মেয়েকে প্রাইভেটে দিয়েই শুরু করে স্বপ্নের চাষাবাদ। আর গোপনে গোপনে জায়নামাজের দেনাও শোধ হতে থাকে। রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাও, ওয়াফিল আখেরাতে হাসানা, ওকিনা আজাবান্নার। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাতে কল্যাণ দান করো এবং জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করো। সে-সাথে চোখের পানি তো রয়েছেই। এভাবে দিন চলতে থাকে। এবং এক ধরনের আরামবোধও লাগে। যদ্দূর বুঝতে পারি, সবাইকেই একধরনের ভালোলাগা পেয়ে বসেছে। আরামের জাজিমে পিঠ লাগিয়ে অলস বসে থাকতে ভালো লাগে। সকালে পত্রিকা এলে সময় নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবর পড়তে ভালো লাগে। টিভি দেখতে ভালো লাগে। চ্যানেল থেকে চ্যানেলে দৌড়াতে ভালো লাগে। এমন ভালো আগে কখনো লেগেছে বলে মনে হয় না। যা দেখি, যা খাই সবই ভালো লাগে। কোথাও কোনো অভিযোগ নেই। ভারতীয় সিরিয়াল নিয়েও অভিযোগ নেই। দেশি-বিদেশি চ্যানেলের বিজ্ঞাপনে এমন সব দৃশ্য দেখায়, রীতিমতো পর্নোছবির মতো লাগে। সে-সাথে রয়েছে মর্দনা শক্তি বৃদ্ধির বিজ্ঞাপনও। বেশ সময় নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ দেখায়। এসব বিজ্ঞাপনে আমাদের কোমলমতি শিশু-কিশোর চোখ বড়ো করে চেয়ে থাকে। তাতেও আমাদের কোথাও কোনো মন্দ লাগে না। ধীরে ধীরে আমরা মুক্তমনা হতে থাকি। অসংখ্য যুক্তি এসে ভর করে মাথার মগজে। যুক্তি-তর্কে এক সময় রেজাল্ট বেরিয়ে আসে, জন্মনিয়ন্ত্রণে এ-চ্যানেলগুলো বেশ কার্যকর। শুরুতেই যদি শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণীদের যৌনগতভাবে বিকলাঙ্গ বা অক্ষম করে দেয়া যায়... ইত্যাদি ইত্যাদি। যুক্তিটা বেশ জুতসই লাগে। মনে মনে বলি, তাহলে তো এসব বিজ্ঞাপন নির্মাতাদেরকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেয়া উচিত। যেসব ব্যবসায়িক-শিল্পপতি এসব বিজ্ঞাপনে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করছেন, তাদেরকে স্বাধীনতা পুরস্কার দিয়ে সম্মানীত করা উচিত। আমরা বিজ্ঞাপনগুলো দেখি আর মগজের সুতায় একের পর এক যুক্তি গাঁথতে থাকি। বিজ্ঞাপনের ফাঁকে ফাঁকে সস্তা কৌতুক নির্ভর নাটক দেখি। ইতিহাস বিকৃত চলচ্চিত্র দেখি। এখানেও আমাদের চমৎকার যুক্তি আছে, সিনেম্যাটিক দেখাতে হলে একটু-আধটু ইতিহাস বিকৃত হবেই।
তখন আর মুখ ঠেলে বমি আসে না। টিভি দেখতে দেখতে বোরিং লাগলে বাইরে বেরিয়ে পড়ি। ক্লাবে যেয়ে আড্ডা মারি। আগেই বলেছি, আমাদের আড্ডায় সমকালীন প্রসঙ্গের অনেককিছুই উঠে আসে। আড্ডার সদস্যদের মধ্যে রাজনীতি সচেতন বেশ কয়েকজন বুদ্ধিজীবীও আছে। তাদের বিশ্লেষণও চমৎকার। এই তো সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক মাহমুদ রেজা কথা প্রসঙ্গে শোনালো, রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক প্রত্যেকটি ঘটনার পেছনে কেবল একটি লক্ষ্যই জড়িত—ভিশন-মিশন। সে-রাতেই আমি বাসায় এসে শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকি, বললো কী সে! আসলে কি তা-ই। আমি তখন এক লাফে দুহাজার নয় সালের নির্বাচনে চলে যাই। তারপর সেখান থেকে ধীরে ধীরে পিলখানা-ডেসটিনি-হলমার্ক-কালোবিড়াল ইত্যাদি ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করতে থাকি। বিশ্লেষণে যুদ্ধাপরাধ-শাহবাগ-মতিঝিল-আমার দেশ-রামু এগুলোও উঠে আসে। কিন্তু আমার চোখে কিছুই ধরা পড়ে না। সবখানেই যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাই। পরদিন ক্লাবে মাহমুদ রেজার সাথে বিষয়গুলো শেয়ার করলে, সে শব্দহীন হাসে। তখন তার মুখে এমন একটা ভাব ফুটে ওঠে, যা দেখে আমার নিজেকে তার সামনে অবোধ বালকের মতো মনে হয়। বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি, মহল্লার মানুষগুলো কেমন যেনো বদলে যাচ্ছে। কেউ কারো সাথে আগের মতো ভাব নিয়ে কথা বলে না। পরস্পর পরস্পরকে এড়িয়ে চলে। মুখের দিকে তাকালে মনে হয়, কেমন যেনো হতাশা হতাশা ভাব। কী হয়েছে? যাকেই জিজ্ঞেস করা হয়, বলে—ভাল্লাগে না।
বিষয়টা নিয়ে আমাদের সুহৃদ বিশিষ্ট সাইকোলোজিস্ট ডা. মুহিত কামালের সাথে কথা বললে তিনি জানান, এটাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে বলা হয় ডিপ্রেসিভ ডিজঅর্ডার। অর্থাৎ বিষণœতা রোগ। এটা সাধারণত চরম হতাশা থেকে জন্ম নেয়। এ রোগের সিমটম হচ্ছে—প্রতিদিনকার স্বাভাবিক কাজকর্ম থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে ইচ্ছে করে। নিজের কাছে নিজের অস্তিত্বকে অন্তঃসারশূন্য, অর্থহীন মনে হয়। প্রতিটি দিন ক্লান্ত-অবসাদ-অস্থিরতার বৃত্তে ঘোরপাক খায়। আশপাশের লোকজনকে চরম বিরক্তিকর লাগে, কারো সাথেই কথা বলতে ইচ্ছে করে না। কেউ যেচে কথা বলতে গেলে এক-দুই শব্দের ভেতরই সে ইতি টানতে চায়। তারপরও কেউ যদি তার কথা লম্বা করতে চায়, তখন সে ক্ষ্যাপে ওঠে। কারো কারো অবস্থা এমনো হতে পারে, হঠাৎ পরিচিত এলাকা ছেড়ে উধাও হয়ে যাবে। অবস্থার উন্নতি না হলে অথবা একান্ত দায়ে না পড়লে কখনো ফিরে আসবে না। এ-থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় হচ্ছে; পরস্পর পরস্পরের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া। যে-কোনো প্রকারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সমস্যাটা জেনে তাকে সাহায্য করা। যে-কোনো কৌশলে তাকে সমষ্টির ভেতর নিয়ে আসা। তবেই অবস্থার উন্নতি হতে পারে।
মুহিত ভাই যখন এ-কথাগুলো বলছিলেন, তখনই মনে হচ্ছিলো সম্ভবত এসব কারণেই মহল্লার লোকসংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। ময়রার দোকানের ক্ষিতিশ দা নেই। কোথায় গেলো? খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, বাসা-বাড়ি বিক্রি করে ইন্ডিয়া চলে গেছে। কারণ কী? তখন তার প্রতিবেশি পান-বিড়ি দোকানি কুদ্দুস জানায়, মহল্লার ছেলেরা নাকি প্রতিরাতেই তার দোকানে যেয়ে বিনা টাকায় মিষ্টি খেতো। টাকা চাইলেই পিস্তল দেখাতো। সে ভয়েই বেচারা...। আমাদের আফসোস—কাজটা ভালো করেনি ক্ষিতিশ দা। ছেলেরা অন্যায় করে থাকলে বিচার চাইতে পারতো। আমরা কিছু না করতে পারলেও ওদেরকে বিচার করার মতো মহল্লায় আরো লোক আছে। তারা নিশ্চয় হাত গুটিয়ে বসে থাকতো না। অন্তত রাজনৈতিক কারণে হলেও তাদের একটা বিচার হতো। তা না করে ক্ষিতিশ দা যে-পথে পা বাড়িয়েছে, তা কিছুতেই সমাধান নয়। আমাদের বিশ্বাস ক্ষিতিশ দা ওখানেও স্বস্থি পাবে না। এর আগেও যারা দেশ ছেড়ে গেছে, তারা কেউই ভালো অবস্থায় নেই। প্রফুল্ল-গণেশ-পরিমল তারা মাঝে-মধ্যে ফোন করে জানায়—দিদি, ভুল করে ফেলেছি। একূল-ওকূল দুটোই হারিয়ে এখন হাতের ওপর ভরসা। হাত চললে পেট চলে। বললে তোমরা বিশ্বাস করবে না, মাছ-মাংস-দুধ শেষ কবে যে খেয়েছিলাম, মনে পড়ে না দিদি।
পরিমলরা এক বিন্দুও মিথ্যে বলেনি। মাস দুয়েক আগে কবি রানোয়ারা আপা কলকাতা গিয়েছিলেন। সেখানে যেয়ে তিনি প্রফুল্ল দা’কে খোঁজ করতে থাকেন। দেশ থেকে যাওয়ার সময় প্রফুল্ল দা নাকি তাঁকে বাসার ঠিকানা দিয়ে যান। সেই ঠিকানা ধরে দু’তলা বিশিষ্ট একটা দালান পেয়েছেন বটে কিন্তু তাতে প্রফুল্ল নামে কেউ থাকে না। শেষে কলকাতা থেকে ফিরে আসার পথে এক বটগাছ তলায় প্রফুল্ল দা’র ছেলে তনয়ের সাথে দেখা হয়। সে বটগাছের ছায়ায় একটা ভাঙা চেয়ার পেতে ক্ষুরকর্ম করছে। তিনি হোটেল থেকে বেরিয়ে কিছু কেনা-কাটার জন্যে ধারে-কাছে কোথাও একটি শপিং মলে যাওয়ার জন্যে একটা রিক্সা খোঁজ করছিলেন, রিক্সা না পেয়ে ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে একটি বটগাছের ছায়ায় এসে দাঁড়ান। তখনই চোখে পড়ে প্রফুল্ল দা’র ছেলে তনয়। প্রথমে তো তিনি নিজের চোখকে বিশ্বাসই করতে পারেননি। স্কুলে পড়ার সময় ছেলেটা কতো নাদুস-নুদুস ছিলো। জুয়েলারি ব্যবসায়িক হিসেবে প্রফুল্ল দা’র সাফল্যও ছিলো ঈর্ষণীয়। সেই মানুষের ছেলে আজ রাস্তায় দাঁড়িয়ে ক্ষুরকর্ম করছে। এটা বিশ্বাসের বিষয়! পরে জানতে পারলেন, যে-লোকটাকে বিশ্বাস করে প্রফুল্ল দা টাকা-পয়সা দিয়েছিলেন, সে নাকি মেরে দিয়েছে। যে-কারণে তিনি পথের ভিখিরি হয়ে নানা রোগে ভুগে এখন বিছানায় শোয়া। একমাত্র ছেলেটা লেখাপড়া ছেড়ে সংসারের হাল ধরেছে। এভাবে সে কতোটুকু এগুতে পারবে আল্লা মালুম। বেশিদূর এগুতে পারবে বলে মনে হয় না। কারণ ওটা তার দেশ নয়। দেশহীন মানুষদের যে কী সিদ্দত, যারা ভুক্তভোগী শুধু তারাই জানে।
শুনলাম, আবদুল করিমও শহর ছেড়ে হোম ডিস্ট্রিক ময়মনসিংহ চলে গেছে। চলে গেছে মোয়াজ্জেম হোসেনও। মোয়াজ্জেম হোসেনের যদিও শহরের বাসা ছেড়ে কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, সেজন্যে সে ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে ধর্ম-কর্মে নাম লিখে তিন চিল্লার জন্যে তাবলিগে চলে গেছে। কে জানে তার মনে কী? হয়তো সেটা তার জীবন চিল্লাও হতে পারে। বাসা ছেড়ে আত্মগোপনে চলে গেছে মাহবুব রেজাও। খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, অনেকদিন ধরেই নাকি তাদের বাসার সামনে শাদা পোশাকধারী লোকদের আনাগোনা বেড়ে গিয়েছিলো। একদম হলিউড ফিল্মের পিশাচদের মতো। চুপচাপ ঘুরে বেড়ায় আর মাঝে মাঝে আড়চোখে বাসার দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে কী সব যেনো বলতো, দুতলা থেকে স্পষ্ট বোঝা যেতো না।
মাহবুব রেজাকে নিয়ে ভীষণ ভয় ছিলো আমাদেরও। এমন একটা কিছু হতে পারে, এটা আমরাও টের পাচ্ছিলাম। সে যেখানে সেখানে যার-তার সাথে তর্কে জড়িয়ে যেতো। মৃত্যু যে পেছনে ছায়ার মতো লেগে রয়েছে—বুঝতেও চাইতো না। কিছু বলতে গেলেও হেসে উড়িয়ে দিতো। বলতো—‘বাংলাদেশ হলো নরম মাটির দেশ। নরম মানুষের দেশ। এখানে কেউ যতোই হামকি-ধামকি করুক না কেনো সময় হলে ঠিকই দেখবেন কোমল হয়ে যাবে।’ কিন্তু দিন যে বদলে গেছে, কিছুতেই তাকে বোঝানো যাচ্ছিলো না। অনেকদিন ধরেই বলে আসছিলো—একটা উপন্যাস লেখবে। মগজের মধ্যে নাকি সাম্প্রতিক অনেক ঘটনা আর চরিত্রের মহড়া চলছে। সেটাকে দৃশ্যমান করতে হলে ছোটগল্পের মতো হা-ডু-ডু মাঠে চলবে না, চায় কুরুক্ষেত্র অথবা পানিপথ প্রান্তর। শুনে আমাদের হাসি পায়। আবার ভয়ও লাগে। না জানি কী থেকে কী লেখে ফেলে। স্রোতের বাইরে ঊনিশ-বিশ হলেই সর্বনাশ। এ-নিষিদ্ধ সময়ে সরকার বিরোধী কিছু লেখা মানে মৃত্যুকে ডেকে আনা। ক্রসফায়ারে ফেলে জঙ্গি বা চরমপন্থি বলে চালিয়ে দেবে।
চিন্তাটা মাথায় আসতেই বললাম, যা-ই লেখো আমাকে একবার দেখাইও। তখনই সে অফিস ব্যাগ থেকে স্টেপলিং করা ‘এ ফোর’ সাইজের কয়েকটা কাগজ বের করে দেখাতে দেখাতে বলতে লাগলো, প্রথমে যা ভেবে বসি, কিছুক্ষণ লেখার পর তা আর খুঁজে পাই না। কল্পনাগুলো মগজ খালি করে কোথায় যেনো পালিয়ে যায়। তার স্থলে অন্য আরেকটি কাহিনি এসে চরিত্রের পালসহ হাজির। তখন অনু পোকা হয়ে মগজের কোষে কোষে আগের চরিত্রগুলিকে শত খুঁজে বেড়ালেও পাই না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর যাও দু-একজনকে ধরে এনে কলমের ডগায় তুলে ধরি কিন্তু কাজ হয় না। ভয়ে জবুথুবু হয়ে গুটিয়ে থাকে। কোনো চরিত্রই জীবনের ঝুঁকি নিতে চায় না। যতোই জোর করি ততোই কড়াবাঁশের ঝিংলার মতো বেঁকে বসে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে আমি যেনো ওদের পায়ে শেকল পরিয়ে আবুগারিব কারাগার অথবা হাবিয়া দোযখে নিয়ে যাচ্ছি। জান থাকতে সেখানে যাবে না। তার চেয়ে মগজের তপ্ত কড়াইয়ে পুড়ে পুড়ে মরণই যেনো ভালো। সুযোগ পেয়ে আমিও বলি—বাদ দাও। অন্য কিছু ভাবো। প্রকৃতি নিয়ে লেখো। ‘আম পাতা জোড়া জোড়া মারবো চাবুক চড়বো ঘোড়া’ অথবা ‘আগডুম বাগডুম ঘোড়ার ডুম সাজে’—এসব লেখো। আমার কথা শুনে সে তখন এমন এক ভাব ঝুলিয়ে চেয়ে থাকতো; যেনো আমি তার সাথে মশকরা করছি। আমি তখন তার বাড়িয়ে দেয়া কাগজগুলোয় একবার চোখ বুলিয়ে নিই। দেখি—যা ভেবেছিলাম তাই। একাত্তরের পরবর্তী বিব্রতকর বিষয়গুলো নিয়ে সে উপন্যাস লেখতে চায়। নিশ্চিত মৃত্যুর ছায়া পড়েছে তার ওপর। তা না হলে আর কোনো বিষয় খুঁজে পেলো না?
(চলবে)