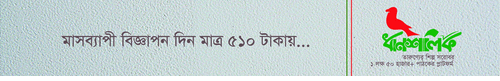পদাবলি

ক্রাইসিস
স্বপন শর্মা
সব খানে বিশুদ্ধ বাতাসের ক্রাইসিস;
ধোঁয়ায় ধুলিকণা আর লিড সালফাইড;
সূর্যটা বেমালুম ঢেকে যাবে-
নাইট্রাস অক্সাইড আর কার্বন মনোক্সাইডে।
মেঘে আর জল নেই শুধুই এসিড কণা!
জ্বালো হাইড্রোকার্বন ভাঙ্গো ওজন স্তর
ছেয়ে যাক পৃথিবী বিধ্বংসী জীবানু আর বিষে।
সব ভুলে যাই; ব্যস্ত হই বিষ নিবারনে।
পুড়ে যাওয়া ক্ষত, মুছে যাওয়া দাগ
সেলিম রেজা
ঠোঁটে ঠোঁট রেখে চুষে নাও অমৃত
নির্ভরতার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমাও
হাতে হাত রেখে পাড়ি দাও সুউচ্চচূড়া
ষোল আর ষাটে কী আসে যায়!
ইচ্ছে হলেই সাঁতার সাঁতার খেলায় মত্ত
আকাশ ছোঁয়ার অদম্য বাসনায় জাগো
বয়সে কী আসে যায় এমন
যুদ্ধমাঠে পরাজয় মানতে কে রাজী !
অনভ্যস্ত বালির পথে ফেলে যাওয়া
স্বপ্ন ঘুড়ির নাটাই
চৌরঙ্গি মাঠে প্রেমিকযুগল চুমু খায়
ছুঁয়ে দেয় চিবুক
খোলা রাস্তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে টিনেজ সময়
রোদে ভিজে পান করে ওয়াটার ম’ম
দীর্ঘ পথ হেঁটে হেঁটে পুষ্টিহীনতায় ভোগে চোখ
আয়না জলে দেখে নিষ্পাপ মুখ
ঢের আছে দেখা ঝরাপাতায় আগুন
পুড়ে যাওয়া ক্ষত, মুছে যাওয়া দাগ;
বেঁচে থাকার দীর্ঘ আয়ু ফিরে পায় স্বপ্ন বালক
নুজ্ব্য সময় বয়সের ভারেও উড়ে কপোতীর পালক...
বিরহী বর্ষা
এম এ ওহাব মণ্ডল
বর্ষা এলে শূন্যতা আহ্বান করে
নিখোঁজ হওয়া একটি নাম।
অথচ,অগণিত মানুষের পৃথিবীতে ওই নামের অবয়ব
হারিয়ে গেছে ফেলে আসা শৈশবের মতো।
এখন বর্ষা আসে গাল ভরা জল নিয়ে
থকথকে বিরহ মন্থন শেষে অস্ত যায়
প্রত্যেহ ডুবে যাওয়া আদিত্যের মতো।
বর্ষা এলেই বুকের ভেতর জেগে ওঠে
কালজয়ী কিছু ক্ষত।
জানালার শিক ভেদ করে আসা
বৃষ্টিভেজা কদমের পরিচিত ঘ্রাণ
কষ্ট বুনন করে যায় শূন্য বিছানায়।
বর্ষা এলেই ভীষণ বিরহ পালক হয়ে ওঠি।
যাতনা সহিষ্ণু গৃহিণীর মতো বিরহ সই
বর্ষার সংসারে।
কতদিন এমন করে ভিজিনি
নূরনবী সোহাগ
কতদিন যায়- স্মৃতিহীন হয়ে
অথচ আমাদের মেঘ দেখা হয়না আয়োজন করে
তেমন করে কি আর বর্ষাও নামে?
চুপচুপে শরীর চুয়িয়ে
নগরের কালোপিচে কখনো বা
হুটহাট নেমে বসে অঝোর ধারা
কই, আমাকে তো ছুঁয়ে দেয়নি কালোজানালা ভেদ করে কিংবা আমি
মরার বৃষ্টি; বলে চারিদিকে কেবল অপবাদ শুনি
আর তুমিও দিনে দিনে পোষ মানলে
ভোঁতা অনুভূতির খোপে
এত এত নি®প্রাণ শিকড় ছিঁড়ে
তুমি ছুটে যাওনি বৃষ্টি ছুঁতে।
আজ অসুখের নাম দাও খরা
পুড়ে যাচ্ছে যেন তোমার আমার নিজস্ব উঠোনটা
ভেবে নাও; ছাদ ঠেকেছে মেঘে
দুমুঠু বৃষ্টি নাও- কতদিন এমন করে ভিজিনি
তুমি আমি, তুমুল আগ্রহে
সময়ের আখ্যানে ছায়াগুলো সময়ের
নোনাজলে নীলপদ্ম
সময়ের আখ্যানে ছায়াগুলো সময়ের
ইলিয়াস বাবর
লেখার রচনাকাল ও এর প্রেক্ষিত মোটাদাগে ঐ সময়কে চিহ্নিত করতে সহায়তা করে। সাহিত্যের যেকোন মাধ্যমেরই রচনার সময় বড় একটা ফ্যাক্টর। কেননা, মানুষ সামাজিক জীব, সময়ের সমস্যা ও সম্ভাবনার ভেতর তাকেও যেতে হয়, তার ভাবনাকেও প্রলম্বিত করতে হয়Ñ সময়ের কষ্টিপাথরে। তাছাড়া মানবীয় প্রবৃত্তি এই, ভাবনায় থাকে বর্তমানÑ অতীত আর ভবিষ্যৎ চোরা¯্রােতের মতোন, প্রবলভাবে দৃশ্যমান হতে থাকে বর্তমানই। মিলন বনিকÑ প্রথম পরিচয় গল্পকার, আরো অনেক কাজে নিজেকে সংযুক্ত রাখেন সাহিত্যেরই নানা মাধ্যমে। নোনাজলে নীলপদ্ম তার প্রথম উপন্যাসÑ বৃহৎ ক্যানভাসে সময়কে ধরার, নিজেকে আবিষ্কার ও প্রকাশের সুযোগ। তার বয়স কত? প্রায় দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে তিনি কর্মজীবনে আছেন, সময়ের আর্বতে বদলে গেছে তার কর্মক্ষেত্র। কিন্তু তারও আগে প্রথাগত নিয়মের মতো, তিনিও হয়তো শিক্ষাজীবন শেষে খানিক সময় বেকার ছিলেন। যা নিজের জীবন দিয়ে যায় না, যাতে থাকে না হার্দিক সংশ্লেষ, তাতে প্রথমের আকুতি যুক্ত হবার কথা নয়। একজন কথাসাহিত্যিককে অনেক কিছুর ভেতর দিয়েই যেতে হয়; এক জীবনে ধারণ করতে হয় নানা জীবনের স্বাদ। মিলন বনিক নিজের অভিজ্ঞতা বটেই বর্তমানের পরিপার্শ্বকে মিলিয়ে দেখেন মানবিক আয়নায়Ñ রাহুলের মাধ্যমে। নোনাজলে নীলপদ্ম’র ভেতর দিয়ে মিলন বনিকের যে পর্যটন আমাদেরই বর্তমানতায় তাকে কে অস্বীকার করবে? শিক্ষাজীবন শেষে, সোনালী সময়ে জুতোর তলা খসে যায় চাকরি খুঁজতে গিয়ে। কর্মখালী নাইÑ ঝুলানো দেখে স্বাভাবিক উজ্বলতায় নেমে আসে আত্মহননের চিন্তা! বিষণœ রাতের পর সকাল হলেই আবারো শুরু হয় যুদ্ধÑ দিনশেষে মলিন মুখে ফিরে আসতে হয় ব্যাচেলর বাসার নিঃসঙ্গ খাটে। তাতে লেগে থাকে আশাবাদী ও আশাভঙ্গ হবার গল্প, রটিনের ভেতর থেকেও প্রতিনিয়ত তাকে কুঁড়ে খায় সময়ের কীট। অনাকাঙ্খিত মানবিক বোধের জয়-পরাজয়ের দ্বন্দ্বে আমাদের সামনে জেগে থাকে নোনাজলে নীলপদ্ম।
বেকারত্বের অমোঘ তথ্য সামনে রেখে রাজনীতিবীদেরা কথার খই ফোটান; শিল্পপতি-সমাজপতিদের কণ্ঠে ঝরে হাহাকারÑ অথচ তাদের সময় মেলে না রাহুলদের সিভিটা একটু দেখতে, সুযোগ থাকার পরেও বিদেয় দেয় এক কাপ চা খাইয়ে। হকার হাশেম এদের দুঃখ বোঝে, বোঝে না বড় সাহেবেরা। হলুদখামে জীবনবৃত্তান্ত ভরে দৌঁড়তে হয় সাহেবদের দরবারে; ওদিকে পিতা জগদীশের গর্বিত মুখে উচ্চারণ করে তাদের সন্তানদের ডিগ্রি পাশ দেয়ার খবর, ভবিষ্যতে বড় চাকরি প্রত্যাশার কথা। ঘোষবাবুদের মিষ্টি কথার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অফিসের একটুকু অবসরে সাময়িক শ্রান্তিতে আবারো ব্যস্ত হয়ে উঠে রাহুলেরা। দৌঁড়াতে হয় অফিস টু অফিস। তাতে যুক্ত হতে থাকে প্রেম এবং বন্ধুত্বের গল্প। প্রত্যাখান ও প্রত্যাশার গল্প। চৈতি, অনন্ত, মাহফুজ... জুড়ে থাকে আমাদের যাপনে। কত কথা, কত গান। অনন্তদা জেগে থাকে তার ভাতৃসুলভ মমতা দিয়ে। এ আরেক মায়ার খেলা। এরভেতরই রাহুলের মানে জেগে থাকে টিউশনিবিষয়ক নানা অভিজ্ঞতা ও বাড়ি থেকে লম্বা ফর্দের বিষয়াশয়। কোন কোন ছাত্রী প্রপোজ করে বসে রাহুলকেÑ যেমনি টিউশনি করতে গিয়ে জড়িয়ে যায় অনেক গৃহশিক্ষক। কেউ পার পায়, কেউ তলিয়ে যায় সময়ের চোরাগর্তে। রাহুল, যে কিনা চৈতির সাথে সম্পর্কে আবদ্ধ, তাকেই তার ছাত্রী প্রস্তাব না শুধু ইশারাও দিয়ে বসে প্রেমের; এবং তাদেরই মা-বাবা মনেমনে রাহুলকে পছন্দ করে আত্মজাকে। ছোট ছোট বাক্যে মিলন বনিকের শব্দখেলা শেষপর্যন্ত দারুন জমেই ওঠে। তার স্বভাবজাত সুস্বাদু গদ্যভাষা আমাদের নিয়ে যায় মায়ার অকল্পনীয় এক জগতে।
শুধু প্রেম আর মোহেই জীবন থেমে থাকে না। রাহুল বন্ধুদের সাথে মিশেÑ অনেকটা বেকারত্বের অভিশাপ থেকে বাঁচতে নিজেকে প্রতিস্থাপন করে ছিনতাইকারী দলের সাথে, যারা তার সাথে আগে থেকেই পরিচিত। সময়ের চামচিকায় রাহুল ভীড় করে অসৎ উপার্জনের পথে। যে ছাত্রী তাকে প্রেম নিবেদন করেÑ সে-ই তার বা তার দলের প্রথম প্রতারনার শিকার। চলতে থাকে এভাবেই, চিনতাই, নেশাÑ প্রভৃতি বিষয়ে জড়িয়ে রাহুল নিজেকে আবিষ্কার করতে থাকে অন্যরকম দুনিয়ায়। চলতিপথে দেখা হয়ে যায় তারই এক বান্ধবীর সাথে, যে কিনা স্কুলজীবনে ছিল দারুন চঞ্চল। সেখানে যোগ হতে থাকে নানাবিধ ঘটনা। নারীদের পুরুষবিষয়ক বিদ্বেষের গোমরও ফাঁস হতে থাকে বেখেয়ালি মনে। এর ভেতর দিয়ে কথাকার মিলন বনিক তার দেখার দৃষ্টিকে নিয়ে যান অনন্য উচ্চতায়। জগতের বড় বড় ঘটনার সাথে জনসাধরণের সংশ্লেষ বা দেখার আনন্দ থাকলেও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনা এড়িয়ে যায় সহজেই। সেখানেই একজন মহৎ সাহিত্যিক ডুকতে চেষ্টা করেন। তার দেখার চেষ্টাকে ক্ষুদ্রের ভেতরেও বড় প্রভাবে দেখান মিলন বনিক। একজন নেশাকারের মানবিকবোধ চলে যাবার ব্যাপারটুকু শুকনো জায়গায় জাল ফেলে মাছ ধরার মিছে আনন্দের মধ্যেও একধরনের কৌতুকবোধ চিহ্নিত করান মিলন বনিক। ছোটবোনের মৃত্যুজনিত কারণে রাহুলের শোক ও বেদনাকে সমান্তরালে তুলে এনে তাতে বেকারত্ব আর সংসারের বড়ছেলের দায়বোধের চিত্রকে দৃশ্যমান করেন ঔপন্যাসিক। রাহুল আহত হতে থাকে অথচ তার করার থাকে না কিছুই। কিন্তু একজন বাচ্চা মরে যাবার সময় ছায়াছবির মতোন করে বলে না, তার আকুতির কথা। মিলন বনিক বোধহয় সম্প্রতি অতি জনপ্রিয় বড়ছেলে নাটকের সমান্তরালে নোনাজলে নীলপদ্ম-এ আনেননি কিন্তু রাহুলের বোনের মৃত্যুক্ষণে যে কথপোকথন আনেন তা অতি নাটুকে হয়ে যায়, এমনকি এ নাটুকেপনা বজায় থাকে রাহুলের হাসপাতালে ভর্তিকালীন কথাপরম্পরায়ও।
নোনাজলে নীলপদ্ম’র কোন চরিত্রকেই প্রধান না ধরলেওÑ যদিওবা রাহুল নায়কের চরিত্রে দিব্যি মানিয়ে নেয় নিজেকে; সেখানে সময়কেই চরিত্র বলে ধরে নিতে পারে যেকোন পাঠক। তার নানাবিধ কারণও আছে। বেকারত্বের সামাজিক ও রাষ্ট্রীক প্রেক্ষিতে মিলন বনিকের এ কাজকে উল্লেখযোগ্য হিসেবেই চিহ্নিত করতে পারি আমরা। সময়ের সবচেয়ে বড় বিষবৃক্ষ নিয়ে যে আখ্যান ও তার ডালপালাÑ তা মিলন বনিক দেখাতে সক্ষম হয় নোনাজলে নীলপদ্মে। কিন্তু তার ব্যক্তিজীবনের সময়কে তিনি বোধহয় ডিঙিয়ে যেতে পারেননি! তা এভাবেই, রাহুল বিভিন্ন অফিসে যান, তার সিভি বিভিন্ন দফতরে জমা দেন কিন্তু আজকের দিনে বেকারেরা সিভি জমা দিতে সহজেই দফরে দৌঁড়ান না, সিভি জমা দেন অনলাইনে, মেইলে। আরো মজার বিষয়, এখনকার তরুণ চাকরির খবর পড়েন, তারচে বেশি লগ ইন করেন অনলাইনের বিভিন্ন চাকরির সাইটে। এটা আসলে সময়েরই দাবী, প্রযক্তির ডাকে সাড়া দেয়া। এখানেই সম্ভবত মিলন বনিকের দৃষ্টিপাতে কিছুটা ঊনতা দৃশ্যমান হতে পারে। তারচেয়ে বড় কথা, নোনাজলে নীলপদ্ম হয়ে উঠে আমাদেরই নগরযাপন, পার্থিব চাওয়া-পাওয়া, বেকারত্ব, প্রেম, হতাশা থেকে নেশার দিকে ছুটে চলা ইত্যাদিকে দারুণভাবেই আনেন আলোচ্য কথাকার। শেষপর্যন্ত রাহুলÑ হোক তা হাসপাতালের বেড়ে, সেখানেই তার চাকরিপ্রাপ্তির খবর পান, এবং ইতিবাচক শেষ দিয়েই আমাদের মাত করেন মিলন বনিক। সাহিত্যের কাজ প্রধানত আশাজাগানো, তা-ই একেবারে শেষে এসে দেখান নোনাজলে নীলপদ্ম-এÑ এজন্যই ঔপন্যাসিক মিলন বনিককে শ্রদ্ধা।
অনন্য এক শব্দচাষী নির্মলেন্দু গুণ
অনন্য এক শব্দচাষী
নির্মলেন্দু গুণ
ইসরাফিল আকন্দ রুদ্র
বাংলা সাহিত্যের কাব্যে যার অতুলনীয় অবদান, কাব্যের ভুবন, কবিদের কবি নির্মলেন্দু গুণ। যার ভাবনায় গড়ে উঠেছে নতুন এক কাব্যজগত। লোকের মুখে মুখে যার কবিতা শোনা যায়, মুঠোফোনে টিউন হিসেবে তাঁর কবিতা চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে (কিন্তু রয়্যালটি পায় না তিনি; কবি মূখ্যপুঞ্জি আর বিভিন্ন টকশোতে তা বলেছেন), জন্মদিনে যাকে জানানো হয় কয়েক গন্ডা ফুলেল শ্রদ্ধা সেই নির্মলেন্দু গুণ। তাঁর কোনো বিশেষণের প্রয়োজন নেই। তিনি কবি, চিত্রশিল্পী অভিনেতাও বটে।
‘আমি বলছিনা ভালবাসতেই হবে’ কবিতাটি প্রেমের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। ‘মানুষ’, ‘হুলিয়া’ তাঁর অমর সৃষ্টি। ‘স্বাধীনতা এ শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো?’ কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের নিজস্ব সম্পদ। তা জাতীয় শিক্ষাক্রম পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এর নবম-দশম শ্রেণীর বাংলা সাহিত্যের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। কালজয়ী কবি নির্মলেন্দু গুণ। কবিতার পাশাপাশি তিনি গদ্য ও ভ্রমণকাহিনীও লিখেছেন।
রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুলেছেন শান্তিনিকেতন। তেমনি নির্মলেন্দু গুণ গড়েছেন ‘কবিতাকুঞ্জ’। সমস্তটা তাঁর স্বাধীনতা পুরস্কার এর প্রাপ্ত অর্থায়নে। তাঁর ভাবনা পৃথিবীর সকল বিখ্যাত কবিদের বই থাকবে সেখানে। তিনি স্বাধীনতা পুরস্কার দেবার জন্য জোড় দাবি জানিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ‘আমি এর যোগ্য বিধায় আমি দাবি জানিয়েছি। সত্যিই ওনি তাঁর যোগ্য। যেন সুপাত্রে কন্যা দান।
অনেকে যা পারেনা নির্মলেন্দু গুণ সেটি করে দেখিয়েছেন। কবিতার জন্য কাটিয়েছেন ইচ্ছাধীন জীবন । তিনি বিশ্বাস করতেন না যে কবি হওয়া যায়। বড় কবিদের নামের পাশে তাঁর নাম বসবে এমনটা ভাবেনি। প্রথম দিকে গ্রাম্য কবিদের কবিতা সংগ্রহ করতো। তিনি বলেছেন, ‘আমি কবি হতে চাইনি, বরং চেষ্টা করেছি কবি না হওয়ার।
কবি নির্মলেন্দু গুণের ১৯৪৫ সালের ২১ শে জুন (বাংলা ৭ আষাঢ় ১৩৫২) নেত্রকোনার বারহাটা উপজেলার কাশবন গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর ছেলেবেলা কাটে নেত্রকোণার বারহাট্টা উপজেলায়। বাবা সুখেন্দু প্রকাশ গুণ এবং মা বিনাপানি । বাবা-মার তিন মেয়ে এবং দুই ছেলের মধ্যে নির্মলেন্দু ছোট ছেলে। চার বছর বয়সে মার মৃত্যুর পর তাঁর বাবা আবার বিয়ে করেন চারুবালাকে। তাঁর একমাত্র কন্যা- মৃত্তিকা গুণ।
প্রথমে মা চারুবালার কাছেই লেখাপড়ার হাতেখড়ি হয় তাঁর। এরপর তিনি বারহাট্টার করোনেশন কৃষ্ণপ্রসাদ ইন্সটিটিউটে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন। দুই বিষয়ে লেটারসহ মেট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ পান ১৯৬২ সালে৷ । মেট্রিক পরীক্ষার আগেই নেত্রকোণা থেকে প্রকাশিত ‘উত্তর আকাশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নির্মলেন্দু প্রকাশ গুণের প্রথম কবিতা ‘নতুন কান্ডারী’৷
মেট্রিকের পর আই.এস.সি পড়তে চলে আসেন ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে৷ আনন্দ মোহন কলেজ ভাল না লাগার কারণে , তিনি নেত্রকোনা ফিরে এসে নেত্রকোনা কলেজ এ ভর্তি হন। নেত্রকোণায় ফিরে এসে নির্মলেন্দু গুণ আবার ‘উত্তর আকাশ’ পত্রিকা ও তাঁর কবি বন্ধুদের কাছে আসার সুযোগ পান ।
নেত্রকোণার সুন্দর সাহিত্যিক পরিমন্ডলে তাঁর দিন ভালোই কাটতে থাকে৷ ১৯৬৪ সালের জুন মাসে আই.এস.সি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের ১১৯ জন প্রথম বিভাগ অর্জনকারীর মাঝে তিনিই একমাত্র নেত্রকোণা কলেজের ছাত্র ছিলেন ৷
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগে ভর্তির প্রস্তুতি নেন নির্মলেন্দু গুণ ৷ হঠাৎ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শুরু হয় ঢাকায়৷ দাঙ্গার কারণে তিনি ফিরে আসেন গ্রামে৷ ঢাকার অবস্থার উন্নতি হলে ফিরে গিয়ে দেখেন তাঁর নাম ভর্তি লিষ্ট থেকে লাল কালি দিয়ে কেটে দেওয়া৷ আর ভর্তি হওয়া হলো না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে৷ ফিরে আসেন গ্রামে৷ ১৯৬৯ সালে প্রাইভেটে বি.এ. পাশ করেন তিনি ৷
বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কারের মধ্যে তিনটি বড় পুরস্কার তিনি ইতিমধ্যে অর্জন করেছেন। এ ছাড়াও তিনি দেশে বিদেশে অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ১. বাংলা একাডেমী পুরস্কার-১৯৮২, ২. একুশে পদক- ২০০১, ৩. স্বাধীনতা পুরস্কার- ২০১৬, ৪. আলাওল সাহিত্য পুরস্কার-১৯৭৫. ৫. লেখক শিবির পুরস্কার-১৯৭২, ৬. বঙ্গবন্ধু পুরস্কার- ১৯৮৩
৭. মুজিব পদক-১৯৮৪, ৮. গৌরিকশোর ঘোষ সাহিত্য পুরস্কার, কলকাতা-২০১০
৯. শান্তিনিকেতন সম্মাননা- ২০১৪, ১০. হাসান হাফিজুর রহমান পুরস্কার-১৯৮৮, ১১. কবিতা পরিষদ-২০১১, ১২. আহসান হাবীব পুরস্কার-১৯৮৬, ১৩. খালেকদাদ চৌধুরী পুরস্কার- ১৯৯১, ১৪. উইলিয়াম কেরী, কলকাতা-১৯৯৭, ১৫. মহাদিগন্ত, কলকাতা, ২০০৫, ১৬. সিটি ব্যাংক-আনন্দ আলো পুরস্কার-২০০৮, ১৭. আড্ডা টোকিও, জাপান, ২০০৩, ১৮. কথা পুরস্কার, প্যারিস, ২০০৮
১৯. মেলবোর্ন সাহিত্য সংসদ সম্মাননা, অস্ট্রেলিয়া, ২০১১, ২০. সংহতি, লন্ডন, ২০১০, ২১.মার্কেন্টাইল ব্যাংক সাহিত্য পুরস্কার -২০১৮
তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : প্রেমাংশুর রক্ত চাই, বাংলার মাটি বাংলার জল, চাষাভূষার কাব্য, পঞ্চাশ সহস্র বর্ষ; ছোটগল্প: আপন দলের মানুষ। ছোটদের জন্য লেখা উপন্যাস: কালোমেঘের ভেলা, বাবা যখন ছোট ছিলেন। তিনি নিজ গ্রাম কাশবনে প্রতিষ্ঠা করেছেন কাশবন উচ্চ বিদ্যালয় (এর পূর্ব নাম ছিল কাশতলা মাইনর স্কুল ), রামসুন্দর পাঠাগার, সারদা বাসুদেব চিত্রশালা এবং শহীদ বেদী ।
ধারাবাহিক উপন্যাস : রামবন্দনা : পর্ব ০৪
রামবন্দনা
শাদমান শাহিদ
(গত সংখ্যার পর)
মেয়েটা তখন দিশেহারা হয়ে সোজা না যেয়ে হাতের বাঁ পাশে এমপি মহোদয়ের ভাতিজা মকবুল আহাম্মদের একান্ত সহযোগি শাহিন আলম ওরফে ঠেরা শাহিনের ওয়ার্কশপে আশ্রয় নেয়। ঠেরা শাহিন তখন তার শালা কাদেরকে নিয়ে লোডশেডিংয়ের কারণে অবসর সময় পেয়ে মেশিনের নানা যন্ত্রপাতি ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করছিলো। ঠিক এ-সময় ওয়ার্কশপের গেইটের কাছে একটা শব্দ হয়। দুজনেই উঠে গিয়ে দেখে আট-নয় বছরের একটি মেয়ে তাদের গেইটের ভেতরে ঢুকে কুকুরের ভয়ে জবুথুবু হয়ে কাঁপছে। তারপরের ঘটনা আমরা কল্পনায় আনতে পারি না। কেবল কান্না শুনতে পাই। শহরের কান্না। স্বাধীনতার কান্না। স্মৃতিসৌধের কান্না। ‘একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি’—এমন একটা কান্নার স্বর শহরের গলি-ঘুঁজিতে ছড়িয়ে পড়ে। এক সময় কান্নাটাকে থেমে আসতে হয়। তখন আমাদের কাছে মনে হয়, মেয়েটার লাশ পড়ে আছে শীতলক্ষ্যার তীরে শাদা কাশ বনের ভেতর, কখনো মনে হয় ম্যানহোলের ভেতর দিয়ে ময়লা-আবর্জনার সাথে ভেসে যাচ্ছে বুড়িগঙ্গার দিকে কিংবা তার লাশ ফোর কালারের ছবি হয়ে বেরিয়ে আসছে পত্রিকার পাতায়।
কল্পনার দৃশ্য কল্পনাতেই মিশে যায়। কোথাও হদিশ মেলে না মেয়েটার। অন্যদিকে আমাদের কল্পনার জোরও এক সময় কমে আসে, তখন একদিন শুনি বোবা বাতাসের কণ্ঠ খুলে গেছে। জুলাইয়ের সাতাশ তারিখ রাত সাড়ে বারো কি একটার দিকে ওয়ার্কশপের ভেতর ঠেরা শাহিন আর তার শালা কাদেরের মাঝে টাকা-পয়সার লেনদেন নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে কাদেরের মুখ থেকে একটা গোপন কথা বন্দুকের গুলি হয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়। যার আওয়াজে দুজনেই হতবাক। দুজনেই সতর্ক দৃষ্টি মেলে এদিক-ওদিক তাকায়। না, কেউ নেই। এতো রাতে আশেপাশে কেউ থাকার নয়। পরিবেশ নিরাপদ পেয়ে দুজনেই তওবা কাটে। জীবন থাকতে আর কোনোদিন এমন বোকামো করবে না। কিন্তু বাতাস? বাতাস বসে থাকে না। জীবনে এই প্রথম কণ্ঠে কথার অনুরণন পেয়ে নাচতে থাকে। তাক ধিনা ধিন করতে করতে মুন্সি বাড়ির মোয়াজ্জেম হোসেনের ছেলে সোহেলের রুমে গিয়ে হুচুট খেয়ে পড়ে। যদিও সোহেল তখন ইডেন মহিলা কলেজের অনার্স তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী সাদিয়া আক্তার ঝিনুকের সাথে মেসেঞ্জারে চেটিং করছিলো, ...ফাইনালের জন্যে টিকেট কাটবো কি?...মিরপুর স্টেডিয়ামে...অপু বলেছে তার সাথে জান্নাতও নাকি যাবে... তারপর শেফু আপার কথা বলো, ক্যামু দেয়ার কথা ছিলো, ডাক্তার কী বলে? চলবে কি, নাকি এ যাত্রাই...জানো, শাদা বেডে আপাকে নিথর-স্তব্ধ অবস্থায় দেখার পর থেকেই ভেতরটা যেনো কেমন করতে শুরু করে দিয়েছে...মাসুদ ভাইয়া কোথায়? সরকার কিন্তু পাগল হইয়া গেছে, বইললো একটু সাবধানে থাকতে...বিকেলে অনিতার সাথে দেখা...ওদের বাসার নিচতলার খোরলটায় নাকি সাপ ঢুকেছে, শুনেছো কিছু?...তা অবশ্য ঠিক বলেছো, সারাদেশেই...গতকাল তো স্টেডিয়ামেও একটা ঢুকে পড়েছিলো, ক্যামেরায় ধরা পড়লো বলেই না রক্ষা...এই একটা পিক দাও না...উঁ হুঁ এটা নয়, বুকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না...এভাবেই স্বাভাবিক কথাবার্তা শেষ করে ওরা যখন ক্রমশ অর্গাজমের দিকে এগুচ্ছিলো, ঠিক তখনই কাদেরের মুখ থেকে বেরিয়ে যাওয়া গুলিটা তার কানে গিয়ে শট করে। সঙ্গে সঙ্গে তার কান ফেটে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। তারপর কী ব্যাথা! সে-রাতে এক ফোটাও ঘুমুতে পারেনি। সকাল হতেই বিষয়টা পারুলের বাপ আবদুল করিমকে জানায়। তারপর ঘটনাটা কী হতে পারে, সহজেই অনুমেয়।
আবদুল করিম কসাই না হলেও কসাইয়ের সহযোগী। প্রতিদিন গরু-ছাগলের গলা কাটতে কাটতে তার মন তো এমনিতেই পাথরের মতো শক্ত, তার উপর মেয়ে হারানোর শোক। সব মিলিয়ে আমাদের কাছে বিষয়টা বাংলা সিনেমার শেষ দৃশ্যের মতো মনে হলো। আড়াই হাত লম্বা ছুরি হাতে তেড়ে যাচ্ছে সর্বহারা নায়ক আর জান বাঁচাতে মহল্লার অলি-গলি দিয়ে পালাচ্ছে কুখ্যাত ভিলেন গোষ্ঠি। দৃশ্যটা পূরবী কিংবা প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হলে আমরা হাততালি দিয়ে নিজেদের ক্ষোভ-উত্তেজনাকে প্রশমিত করতাম। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব নয়। পেছনে আইনের কালো অক্ষরগুলো দাঁড়ানো। যদিও এসব অক্ষর ভগবান-ভগবতিদের দেখলে তাবিজ দেখা সাপের মতো ফণা গুটিয়ে থাকে কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে ভিন্ন দৃশ্য। আমাদের কোথাও উনিশ-বিশ হলে সাথে সাথে উদ্যত ফণায় ছোবল মারতে মহূর্ত সময় নেবে না। সে ভয়েই আমরা আবদুল করিমকে আধ-পথে থামিয়ে দিলাম। বললাম, ক্ষ্যামা দাও করিম ভাই। আজাইরা মাথা গরম করো না। যে গেছে, গেছেই। সে আর ফিইরা আইবো না। এখন একজনের লাগি পরিবারের সবাইরে হারাইবার চাও নাকি? অপর দিকে মোয়াজ্জেম হোসেন আগ-পাছ না ভেবে তার ছেলে সোহেলকে বকাবকি শুরু করে দিলো। যে কারণে সোহেলের জীবনটা একটা হুমকির মধ্যে পড়ে।
তখন উভয় কূল রক্ষা করতেই আমাদের কেউ হয়তো থানায় গিয়ে মামলা করার জন্য আবদুল করিমকে পরামর্শ দেয়। কিন্তু আবদুল করিম থানায় যায় না। ভয় পায়। পুলিশ-উকিল-হাকিম এসব নাম শুনলেই নাকি তার ডর লাগে। বলে, আমি মুকখো মানুষ। তানিদের লগে কীভা কথা কইতে হয়, আমি তো কোনো ভাও খুঁইজা পাই না। টেহা-পয়সারও কাজ-কারবার। কত জানি লাগে— ইতস্তত করতে থাকে সে। তখন ভিড়ের ভেতর আরেকজন বলে ওঠে, করিম ভাই, বাদ দেও এইসব। তুমি গরিব মানুষ। দেন-দরবার বা মামলা-মুকদ্দমা কইরা তলা খুঁইজা পাইবা না। এইসব বড় লোকদের কাজ-কারবার। দুনিয়াডা তোমার-আমার লাগি না। আমাদের লাগি পরকাল। সেখানে আল্লা নিশ্চয়ই তাদের বিচার করবে। এখন আল্লার মাল আল্লা নিয়া গেছে। এই মনে কইরা চুপ মাইরা থাকো।
বস্তির শেষ মাথায় আবদুল করিমের ডেরার সামনে দাঁড়িয়ে মহল্লা বাসিরা যখন এসব বলাবলি করছিলো, ঠিক তখন আমার কাছে মনে হচ্ছিলো, যান্ত্রিক শহরের সবকটা তার বুঝি গিটারের মতো একসঙ্গে হেসে ওঠেছে। আমি তখন এদিক-ওদিক তাকিয়ে কিছুই দেখতে না পেয়ে আবার যখন তাদের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছি, এমন সময় আবার হাসির শব্দ। তখন আমার কিছুটা ভয় হয়। ভয়ে হেমন্তের অবিরল পাতার মতন কাঁপতে থাকি। তখন কী আর করা। বাসায় ফিরে নিজের অক্ষমতা চিবুই। তবে একবার ইচ্ছে হয়েছিলো, রেণু বলি। আরিফদেরকে ডাক দিই। আর কিছু না হোক একটা মানববন্ধন তো করতে পারি। পরে মনে হলো, সবটাই অরণ্যে রোদন হবে। কিছুলোক জড়ো হবে বটে, হয়তো কজন সাংবাদিকও ক্যামেরা উঁচিয়ে আসবে। রিপোর্টও হবে। রাস্তার শান্তি রক্ষার্থে ছুটে আসবে পুলিশও। তারপর তোতা পাখির মতো কিছু মুখস্থ কথা বলেই সবাইকে স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করবে। কিছু হবে তো দূরের কথা, আমাদের চিৎকার-নড়াচড়া পুলিশ থানায় যাওয়ার আগেই হাওয়ায় উড়ে যাবে, যেভাবে নদীর এপারের ঢেউ ওপারে পৌঁছার আগেই মিশে যায়।
এসব ভেবে একবারে চুপ হয়ে গেলাম। ধরি মাছ না ছুই পানি’র মতো প্রগতি দেখাতে মাঝে মাঝে পার্টির অফিসে যাই। টুকটাক কথা বলি। সবশেষে আগামিদিনের কিছু করণীয় বুঝে নিয়ে চলে আসি। বাকি সময় ফেসবুক-টিভি-পত্রিকায় খরচা হয়। বই-টই ইদানিং পড়তে ভালো লাগে না। মনে হয়, পৃথিবীর কোনো লেখাই আমাদের উপযোগী নয়। বাঙালির চরিত্রের কাছে এসে যেনো সব মার খেয়ে বসে আছে। কি দর্শন কি সাহিত্য কি ইতিহাস। কোনো কিছুই যেনো এখানে এসে হালে পানি পাচ্ছে না। দর্শন-সাহিত্য মাঝে-মধ্যে চিড়িক দিয়ে উঠলেও ইতিহাস একেবারেই নিষ্প্রভ। যার লেখাই পড়েছি, মনে হয়েছে মধ্যযুগের দোভাষী পুঁথি বুঝি। অলৌকিকতার ভোঁস ভোঁস ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না।
আমার মতো সবাই চুপ থাকলেও মৃত্যুদানব বসে থাকে না। মঞ্চে যমবাড়ির দৃশ্যের মতো পুরো মহল্লা কালচে-নীল আলোয় ঢেকে যায়। জমাবদ্ধ কালো রঙের ছোপের মতো কী যেনো মহল্লার রন্ধ্রে রন্ধ্রে পায়চারি করে। কেউ বলে, এগুলো অক্টোপাস। দেখো না কীভাবে আট পা ছড়িয়ে পিল পিল করে বিল্ডিংএর দেয়াল থেকে দেয়ালে বিচরণ করে। কেউ বলে, অক্টোপাস নয়, শিলপাঞ্জি। যেভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে দেয়াল টপকায়, তা কিছুতেই অক্টোপাস হতে পারে না। এক মাওলানা শোনায় ভিন্ন কথা, এগুলান শিলপাঞ্জি-বান্দর-ভাল্লুক কিছুই না, এগুলান হইছে গিয়া ইজুজ-মাজুজ। আমি তো দেখতাছি, শুধু দেয়াল টপকাইতাছে না, জিবলা দিয়া লেইতাছেও। আমার তখন কী হয় বুঝতে পারি না। দেখি আমাকে আমি হারিয়ে ফেলেছি। কোথাও খুঁজে পাই না। অন্তর্বাসের ভেতর বুকের বল্কলে, নাভীর নিচে, বার্থরুমের বড় আয়নায়, ড্রেসিং ট্রেবিলের সামনে, কিচেনের কৌটায় কৌটায়, বিছানায়, ভেন্টিলেটরের ফাঁক-ফোকরে, সোহাস-রেণুর সঙ্গমদৃশ্য দর্শনের লোভে ঝুলবারান্দায় রেলিং ধরে একঠাঁই দাঁড়ানো, কোথাও না। তখন পরিচিত গ-ি পেরিয়ে আমি বটতলার ওরশে ছুটি। সেখানে আবুল চাচা বায়স্কোপ দেখায়। মুখে গান আর হাত-চটির চেট্টর চেট্টর ছন্দে দর্শক ভেড়ানো চেষ্টা চালায়, কিন্তু দর্শক আসে না। তারা মজা পায় না। এন্ড্রোয়েড মোবাইল যুগে কাঠবাক্সের ভেতর পোস্টার দেখার সময় নাই তাদের। আমি আমাকে খুঁজতে বায়স্কোপের গোল আয়নায় চোখ রাখি। তখনই আবুল চাচা খুশিতে তার চিরাচরিত নতৃনামা শুরু করে দেয়। তখনই দেখি শাদা কাপড়ে আঁকা দৃশ্যগুলো সিনেমার রিলের ছবির মতো সব জীবন্ত হয়ে ওঠছে। দেখি শি জিন পিং এক অলীক পার্লামেন্টকে চাষ করে আজীবন প্রেসিডেন্ট হয়ে যায়, পুতিনের মিরমিরা হাসিই বলে দিচ্ছে মৃত্যুর আগে অবসরে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই, মিয়ানমারের অলৌকিক শক্তি, মহাসাগর থেকে বাতাসের জাহাজ বেয়ে আসে তামিল-আর্তনাদ, মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইলদের দানবীয় পদশব্দ—এসব দেখতে দেখতে কখন যেনো আমার কথা ভুলে যাই। তখন কেবলি ঘুম। আমি ঘুমাই। একসময় ভোর হয়। শহরের পিঠে রোদের ফিসফিস কথা। দরজা খুলে বাইরে পা রাখতে যাই, তখনই দেখি, আমি একটা দুঃসংবাদ নিয়ে ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে...অনুমান নির্ভর প্রাণিরা অদৃশ্য ইঙ্গিতে তথ্য-প্রযুক্তির যান্ত্রিক মেশিনের মতো হুকুম তামিল করে গেছে। মোয়াজ্জেম হোসেনের ছেলে সোহেলকে খুন করে চিতা ঘাটের নামায় ফেলে রেখে গেছে। ঘুম থেকে ওঠেই দুঃসংবাদটা শুনতে হলো। মনে হলো, এই বুঝি গান্ধি জী’র চরকার মতো ঘুরতে ঘুরতে পড়ে যাবো। নিজেকে কোনো রকম সংযত রেখে ভাবতে লাগলাম, কে করে থাকবে কাজটা। আমার জানামতে তার তো কোনো শত্রু থাকার কথা নয়। সে কারোর কাঁচা আইলে পা দিয়েছে, এমন কথাও শুনিনি কোনোদিন। মাথার মগজ তখন কাজ করে না। দৌড়ে যাই নদীর পাড়। গিয়ে দেখি চিতা ঘাটের নামায় মাথাবিহিন একটা লাশ পড়ে আছে। মাথা না থাকলে কার লাশ, চেনা বড় দায়। কিন্তু বাইশ আঙুলি লোকের লাশ চিনতে কারোর কষ্ট হওয়ার কথা নয়। মোয়াজ্জেম হোসেনেরও কষ্ট হয়নি। তার সাথে যোগ হয়েছে লাশের পরনের জামা-কাপড়। বিশেষ করে বাঘ কালারের গেঞ্জিটা। দুদিন আগে ওয়েস্ট-ইন্ডিজের সাথে বাংলাদেশের টেস্ট সিরিজ খেলা দেখতে গিয়ে ছিলো মিরপুর স্টেডিয়ামে। তখনই স্টেডিয়ামের আউট-সাইড থেকে গেঞ্জিটা কিনেছিলো সোহেল। আমরা তখন লাশটাকে খুঁটে খুঁটে দেখতে থাকি। তখনই ধরা পড়ে, কোপের ধরনটা বাম হাতের কাজ। আর আমাদের মহল্লায় কে যে বাওয়া একটা দুধের বাচ্চাকেও জিজ্ঞেস করলে আঙুলের ইশারায় দেখিয়ে দেবে। এখন কী করা যায়? বিষয়টা ভাবতে ভাবতেই খবর পেয়ে পুলিশ চলে আসে। আমরা তখন পুলিশকে বোঝানোর চেষ্টা করি যে, এটা বাম হাতের কাজ। আমরা এর বিচার চাই। বাওয়াখুনি’র ফাঁসি চাই।
(চলব)
আমার একটা দুঃখ ছিল !
আমার একটা দুঃখ ছিল !
মাহবুবা নাছরিন শিশির
বৃষ্টির কথা থাক, বিরহের কথা বলি...
আকাশের কথা থাক, হৃদয়ের কথা শুনি,
যদিও বিরহ তবু মিলনের স্বপ্নজালই বুনি..
আজ আমরা বিরহের কথা বলবো। বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান এ আছে ‘বিরহ’ শব্দটি বিশেষ্য পদ। এর অর্থ [১] বিচ্ছেদ (প্রিয়জনের সাথে); [২]অভাব, শূন্যতা, [৩] শৃঙ্গার রসের অন্যতম একটি অবস্থা। অভিধান মেনে হয়তো কারো জীবনে বিরহ আসেনা। তবে অনেক বিরহী-বিরহিণীর বিরহ অভিজ্ঞতা থেকেই এই অর্থ অভিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একদিন আগে অথবা একদিন পরে বিরহের সরব উপস্থিতি আলোড়ন তোলে প্রতিটি মানব-মনে । বিজ্ঞানীদের গবেষণামতে প্রেম-বিরহের অনুঘটক হিসেবে ‘অক্সিটোসিন’ নামে এক বিশেষ ধরনের রাসায়নিক হরমোন দায়ী। প্রেমে পড়লে যেমন এই হরমোন বিপরীত ব্যক্তির প্রতি আকর্ষণ তৈরি করে, তেমনি বিরহের সময় স্মৃতিকাতর করে তোলে।
সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি এক অপার বিস্ময়। একজনের পক্ষে এক জীবনে সমগ্রটা জানা সম্ভব নয়। তাই অন্যদের অভিজ্ঞতার সাহায্য নিতে হয়। নিজের ও চারপাশের মানুষদের দিকে তাকালেই জানা যায় কত বৈচিত্র্য মানবজীবনে। মানুষের অনুভূতিগুলো সংক্রামক। হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা-বিরহ। কারো মুখে এক চিলতে হাসি খেলে গেলে তা যেন অপরের ঠোঁটের কোণে হাসির কারণ হয়ে পড়ে । অন্যের কান্না দেখলে ব্যথিত মনে শোকভাব সঞ্চারিত হয়, হৃদয় করুণায় ভরে যায়। ভয়ানক দৃশ্যে ভয়, রক্তাক্ত দৃশ্য বা খুন জখম দেখলে শিহরণ জাগে, বীভৎস লাগে, একইভাবে কখনো ঘৃণা, কখনো মন খারাপের কারণে, মানবিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ কখনো সমান্তরাল, কখনো বৈরী আচরণ করে। বাইরে বৃষ্টি ঝরছে। কেউ কেউ এই বৃষ্টিতে আনন্দিত। বৃষ্টির ছন্দ তাদের মুগ্ধ ও মোহিত করেছে। কেউ ব্যথিত। কারো চোখের জল আর বৃষ্টির জলের সমান্তরাল ধারা বহমান। কেউ বৃষ্টিতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সময় পার করছে, কেউ কর্মব্যস্ত জীবনের তাগিদে বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে কর্মক্ষেত্রে ছুটছে। অর্থাৎ এক এক জনের এক এক মতিগতি; একই সময়ে সবাই বিরহী নয়। তবুও বিরহীর মনে ‘বিরহ’ অন্তরের অন্দরে খেলে যায় নিভৃতে। মন থাকেনা মনের ঘরে। প্রিয় সান্নিধ্যে ব্যাকুলপিয়া। যে বিরহবিধুর সেই বোঝে বিরহের কী অনুভূতি। বিরহসম্পর্কে যারা অজ্ঞাত তাদের কাছে ব্যাপারটা হলো এমন:
চিরসুখীজন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিতবেদন বুঝিতে পারে !
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে !
যতদিন ভবে, না হবে না হবে,
তোমার অবস্থা আমার সম।
ঈষৎ হাসিবে, শুনে না শুনিবে
বুঝে না বুঝিবে, যাতনা মম।
[বুঝিবে সে কিসে / কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার]
বিরহ কী? প্রিয় মানুষের বিচ্ছেদ, অনুপুস্থিতি, অবহেলায় আপনি যে শূন্যতা বা কাছে থেকেও দূরত্ব অনুভবের যাতনা ভোগ করেন তা-ই বিরহ। যখন আপনি একজনকে (যে কেউ) এত বেশি ভালোবাসেন যে, তার জন্য সব কিছু করেন, সে যখন যা চায় তাই করতে ভালোলাগে। কিন্তু তারপরও ওই মানুষটা বুঝতে পারে না আপনি তাকে কতটা ভালোবাসেন, সে যখন কারণে অকারণে খারাপ ব্যবহার করে তখন খুব কষ্ট হয়। আর এই কষ্ট টা আপনি যখন নিরবে সহ্য করতে থাকবেন তখন সেটা আস্তে আস্তে বিরহে পরিণত হয়। প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্ক ছাড়াও, এটা যে কোন সম্পর্কে হতে পারে। তবে মানুষেরর এই মানসিক দশা প্রেমিক-প্রেমিকার বিরহরূপে সাহিত্যে অধিক প্রচলিত। প্রিয় বিরহে মানুষ প্রথমে কষ্ট পায়, কষ্টে কাতর অনুভূতি পরবর্তীতে বিরহে রূপ নেয়। এই বিরহ সহ্য করার শক্তি কোনো কোনো বিরহী মানবকে মহামানব করে তোলে। ভাঙা-গড়ার এই ভবে তারা নবসৃষ্টির আনন্দে মেতে ওঠে। প্রেমের যে মহত্ত্ব, প্রাণশক্তি, তেমনি বিরহেরও রয়েছে নতুন সূর্যালোকে নতুন পৃথিবী গড়ার সঙ্গীত। যুগে যুগে প্রেম-বিরহের প্রাণশক্তি নিয়ে মহাপুরুষেরা বসুধা বিনির্মাণে মহৎ কীর্তি স্থাপন করে গেছেন।
মানবমানবির এই বীরহগাথা সবচেয়ে বেশি জানে স্বীয় মন। কিছু কথা কখনো ছড়িয়ে ছিটিয়ে, কখনো গুছিয়ে প্রচারিত হয়েছে মানুষের মুখে মুখে, সাহিত্যের পাতায়। কেউ সুরের মূর্ছনায় বিরহ প্রকাশ করেছে, কেউ ছড়া-কবিতা-গানে লিখে গেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে সাহিত্য রচিত হতো দেবদেবী নির্ভর। আধ্যাত্মিক(জীবাত্মা, পরমাত্মা) এইসব সাহিত্য মানুষের সৃষ্টি। এগুলো সম্পূর্ণ মানবিকতা মুক্ত কী? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো আজকের সাহিত্যিকদের মনেও প্রশ্ন জাগে :
সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহতাপিত। হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে?(১)
আলো-আঁধারি সান্ধ্যভাষায় চর্যাপদের কবি গুন্ডুরীপা যখন বলেন, ‘জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি’(২) অথবা বৈষ্ণব পদে রাধিকার মনের কথা জ্ঞানদাস প্রকাশ করেন:
‘রূপ লাগি আঁখি ঝরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ-পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে।
এই ব্যাকুলতা, প্রিয়জনকে কাছে পাবার কিংবা তার অনুপুস্থিতিতে তার বন্দনা..তার জন্য ক্রন্দসী বিরহিণীর দশা যতটা আধ্যাত্মিক, ততটাই মানবিক।
বিদ্যাপতি রাধার বিরহকে প্রকৃতির সাথে একাকার করে তুলে ধরেছেন। শারীরিক আনন্দের চেয়ে হৃদয়ের বিরহবেদনা তাঁর গভীর অনুভবে মিশেছে । সর্বযুগের বিরহীপ্রাণের দীর্ঘশ্বাস তিনি রাধার কন্ঠে বাণীরূপ দিয়েছেন :
এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা ভাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।
মধ্যযুগের অন্যতম নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বিরহ খন্ডে বিরহ জর্জরিত হয়ে রাধা বলেছে-
এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসার।
ছিন্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার,
মুছিআঁ পেলায়িবোঁ মোয়ে সিসের সিন্দুর
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শংখচুর ।
আধ্যাত্মিকতা বাদে মধ্যযুগের বিরহ দেহজ, আধুনিক যুগের মানুষের বিরহ মানসিক। তবে দেহকেন্দ্রিক ভালোবাসা যেমন ভালোবাসা নয়; তেমনি বিরহও বিরহ নয়। মনের আরাধনাহীন দেহকেন্দ্রিক যে প্রেম, তা কাম। যা দেহকেন্দ্রিক বিরহ, তা কামের বিরহ। দেহ ও মনের ত্রিমাত্রিক মেলবন্ধন প্রেমিকের প্রার্থনা। তাই কামুকের কামনা দেহ, প্রেমিকের প্রার্থনা মন। আধুনিক যুগে সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠেছে মানুষ ও মানুষের মনোবিশ্লেষন। তাই এ যুগে মানুষ প্রেমে-বিরহে প্রিয়জনের মনের সাথে অথবা আত্মার সাথে মিলিত হতে চায়। এ যুগের যুবক, প্রেমিক, কবিরা ভালোবাসে। ভালোবাসার মানুষ ছেড়ে গেলে, তার স্মৃতি আগলে রেখে বিরহবিলাস করতে ভালোবাসে। আধুনিক কবিতার প্রাণপুরুষ নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় বিরহের বহিঃপ্রকাশ :
অনন্ত বিরহ চাই, ভালোবেসে কার্পণ্য শিখিনি...
আমি কি ডরাই সখি, ভালোবাসা ভিখারি বিরহে?
প্রস্থান কবিতায় কবি হেলাল হাফিজ যখন বলেন, ‘এক জীবনে কতটা আর নষ্ট হবে/ এক মানবী কতটা আর কষ্ট দেবে।’ তখন বিরহের সহ্যশক্তি পাঠককে বিস্মিত করে! এই সময়ের পাঠকনন্দিত কবি হাবীবাহ্ নাসরীন-এর কবিতায় বিরহ প্রসঙ্গ এসেছে:
ভুল করেছি বাঁচতে শিখে, ভুল হয়ে যায় প্রেমে
ভুলের জলে ফুলের নৌকো কখন গেছে থেমে!
বেচতে গিয়ে ভুল লিখেছি চোখের জলের দাম
আমার একটা দুঃখ ছিল জীবন তাহার নাম।
বিরহ একপাক্ষিক তীব্র ভালোবাসা ও অপরপাক্ষিক অবহেলার কোমল অথচ যন্ত্রণাময় এক শোকের ছায়া। আরেকটি কবিতায় কবি বলেছেন :
তুমিহীন এই ব্যথিত জীবন জানে
আমিহীন তুমি কত বেশি নাবালক
তবু তুমি দূরে, তবু আমি খুব একা
হৃদয়ে হৃদয়ে তবু হারানোর শোক
-হাবীবাহ্ নাসরীন
উত্তরাধুনিক অর্থাৎ এখনকার কবিতায় বিরহ অঙ্গীভূত হয় মানবিক বেদনা থেকে উৎসারিত উপলব্ধিতে। বৈষ্ণব মতে বিরহিণীর দশা দশটি। বিরহী ও বিরহিণীর বিরহের এই দশাগুলো আধুনিক ভাবধারায় নান্দনিক সৌন্দর্য নিয়ে উপস্থাপিত হয় কবিতায়। কবিতা পুষ্ট হয় ভাবের সমাহারে। বিরহ মনের ভাবকে উদ্বেলিত করে। রচিত হয় কবিতা, গান। শিল্প-সাহিত্যের অপরাপর শাখাতেও এই ভাবধারা পরিপুষ্টতা দান করে। বিরহ মানবজীবনের চূড়ান্ত ভাব নয়। তবু এই খ- ভাব মানুষের জীবনের একটি মুহূর্তকে নিজের আয়ত্তে রাখতে সক্ষম । কেউ কেউ বিরহকে স্বীকার করতে অপ্রস্তুত। মানুষ স্বর্গীয় অপ্সরা, ফেরেশতা নয়। তাই সুখ-দুঃখ, ভালবাসা-বিরহের উপস্থিতি স্বাভাবিক জীবনের ইঙ্গিত বহন করে। প্রেম মধুর। সেই সৌভাগ্য একবার বিরহে পরিণত হলে আশাহত হওয়াটা অন্যায় নয়। বিরহের শোক মৃত্যু নয়, নবজীবনের আলোকবর্তিকা বয়ে আনতে পারে বিরহ । অতীতের পথ ধরে হেঁটে চলা পথিক নবোদ্যমে চলতে পারে নতুন স্বপ্নের পথে। মহাপুরুষ, সাধক, জ্ঞানী ও ধ্যানী ব্যাক্তিবর্গ প্রেম ও বিরহের যুগলস্পর্শেই ত্যাগের মহিমায় অধিষ্ঠিত। বিরহী পথিক সে পথের অনুসারী।
এক স্বতন্ত্র কাব্যধারা নির্মাণপ্রয়াসী কবি মহাদেব সাহা
এক স্বতন্ত্র কাব্যধারা নির্মাণপ্রয়াসী কবি
মহাদেব সাহা
রাহাত রাব্বানী
‘কবির কী আছে আর/ভালোবাসা ছাড়া,/সমস্ত উজার করে/হাতে একতারা।’, ‘তুমি যদি আমাকে না ভালোবাসো আর/এই মুখে কবিতা ফুটবে না,/এই কন্ঠ আবৃত্তি করবে না কোনো প্রিয় পঙক্তিমালা’, ‘একবার তোমাকে দেখতে পাব/এই নিশ্চয়াটুকু পেলে-/বিদ্যাসাগরের মতো আমিও সাঁতারে পার হব ভরা দামোদর’, ‘করুণা করেও হলে চিঠি দিও,খামে ভরে তুলে দিও/ আঙুলের মিহিন সেলাই/ভুল বানানেও লিখো প্রিয়, বেশি হলে কেটে ফেলো তাও,/এটুকু সামান্য দাবি চিঠি দিও’ এসব হচ্ছে মহাদেব সাহার প্রেমজ উচ্চারণ। প্রেমজ শব্দ উচ্চারণ সহজ হলেও প্রেমের কবিতা লিখা সহজলভ্য নয়। অত্যধিক জটিল। একইভাবে কবিতার মাধ্যমে প্রকৃতিকে ফুটিয়ে তোলা আরো কঠিন। এই কঠিন কাজগুলোই অতি সহজে করেছে ষাটের দশকের অন্যতম প্রধান কবি মহাদেব সাহা। মহাদেব সাহাকে বলা হয় প্রেম, প্রকৃতি ও সৌন্দর্যের কবি। প্রেম ও প্রকৃতির মাঝে খুঁজে পান জীবনের অন্যরকম মাদকতা।
প্রেম ও প্রকৃতি মানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যার মনে মানুষের প্রতি প্রেমবোধ জাগ্রত হয়না, থাকেনা মানুষের প্রতি ভালোবাসা- সে সাধারণত প্রকৃতির কাছে যেতে পারেনা। নারী প্রকৃতিরই অন্যতম এক অংশ। দুটোর মধ্যেই সৌন্দর্য,আকর্ষণ ও মুগ্ধতা আছে। আছে হৃদয়ের টান, আকুতি ও উচ্ছ্বাস। যে যত বেশি নারীকে ভালোবেসেছে, বুঝতে পেরেছে- সে ততবেশি প্রকৃতির সান্নিধ্য পেয়েছে। তবে নারী প্রেমের চেয়ে মানবপ্রেম কখনো কখনো সবকিছুকে ছাপিয়ে কবিসত্তাকে মহিমান্বিত করেছে।
প্রেমের পাশাপাশি কবি মহাদেব সাহা তাঁর কবিতায় অনুষঙ্গ করেছেন স্বদেশ প্রেম,স্বজাতি চেতনাও। ওঠে এসেছে বিদ্রোহ। তারই উজ্জ্বল প্রমাণ: ‘ফুল কই, শুধু অস্ত্রের উল্লাস’, ‘গর্জে ওঠে বাংলাদেশ’,‘তোমাকে কেন করে না বিদ্রোহী’, ‘কোথা সে প্রেম, কোথা সে বিদ্রোহ’-কবিতাগুলো। তাঁর কবিতায় ফুটে ওঠেছে বাঙালির গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্য।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাদেব সাহার কন্ঠে একবার স্বরচিত কবিতা শুনেছিলেন। পরম আদরে চুমো খেয়েছিলেন কবির কপালে। আশীর্বাদ করেছিলেন মহাদেব সাহা অনেক বড় কবি হবেন। স্রষ্টা তাঁর আশীর্বাদ ফেলেনি। মহাদেব সাহা কবি হয়েছেন, শুধু কবি নন, হয়েছেন-বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান কবি।
মুজিবুরের আশীর্বাদপুষ্ট কবি মহাদেব সাহার কবিতায় বারবার ওঠে এসেছে মুজিবের নাম। লিখেছেন বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যা ও সেই নির্মম ট্র্যাজেডির অশ্রুসজল পঙক্তিমালা। প্রাসঙ্গিক বিষয় যে, সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার প্রতিবাদে যে দুজন কবি প্রথম কবিতা লিখে প্রতিবাদ করেছিলেন; কবি মহাদেব সাহা তাঁদের একজন । মুজিবকে নিয়ে লিখা তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলোর মধ্যে- ‘আমি কি বলতে পেরেছিলাম’, ‘মুজিব হত্যার বিচার চাই’, ‘তোমার বাড়ি’ উল্লেখযোগ্য।
কৈশরে লেখালেখির শুরু হয় কবি মহাদেব সাহার। প্রেম, বিরহ, স্বদেশ ভাবনা, নিসর্গসহ জাগতিক জীবনের নানা অনুষঙ্গকে উপজীব্য করে কবি মহাদেব সাহা এখনো চলমান রেখেছেন তাঁর কাব্যচর্চা। বিরল কাব্যপ্রতিভা নিয়ে আপন মহিমায় নির্মাণ করেছেন রোদেল আলো ঝলমলে তাঁর কবিতার পৃথিবী। তাঁর কবিতায় ভেসে আসে ভিন্ন এক জগত। যে জগত অতি চেনা হয়েও অচেনা, কাছের হয়েও দূরের, ধোঁয়াশার আড়ালে থেকেও অতিসাধারণ, যার কারণে তাঁর কবিতা আলাদাভাবে শনাক্তযোগ্য। আর একারণেই তাঁর প্রতিটা কবিতাই পাঠকের কাছে হয়ে ওঠে হৃদয়গ্রাহী। তাঁকে নিয়ে কবিতা পাঠকেও আগ্রহও বিস্তর। তাঁর গ্রন্থসংখ্যা দেড়শতাধিক।
এক স্বতন্ত্র কাব্যধারা নির্মাণপ্রয়াসী কবি মহাদেব সাহার রয়েছে সরল মন, উদার ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁর কবিতায়ও এসবের সফল প্রতিফলন লক্ষ্যণীয়।
অত্যন্ত নির্মোহ এই কবি তাঁর নীতি থেকে সরে দাঁড়াননি নূন্যতম। এরশাদ শাসনামলে সাংবাদিকদের জন্য জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিলো। সাংবাদিক হওয়ার সুবাদে মহাদেব সাহাকেও এ জমি নেওয়ার অনুরোধ করলে তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। ইচ্ছে করলে গড়তে পারতেন-বাড়ি, গাড়ি। কিন্তু তিনি কবিতাকেই করেছেন চিরসাথী। কাব্যপ্রতিভার জন্য লাভ করেছেন-একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, কবি সুকান্ত সাহিত্য পুরস্কার, কপোতাক্ষ সাহিত্য পুরস্কারসহ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা। জানা মতে-কবি তাঁর সব বই, সম্মাননা, পুরস্কার বাংলা একাডেমি ও জাতীয় জাদুঘরকে দিয়ে দিয়েছেন। এবং তাঁর যাবতীয় উপার্জন গরীবদের মাঝে বিতরণ করেছেন। এ পর্যন্ত ভ্রমণ করেছেন জার্মানি, রাশিয়া, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা,উজবেকিস্তান।
কবি মহাদেব সাহা ১৯৪৪ সালের ৫ আগস্ট সিরাজগঞ্জের এক ছায়াঘেরা পাখিডাকা প্রকৃতির সুন্দর-মনোরম পরিবেশে আঁকা ধানগড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গদাধর সাহা এবং মাতা বিরাজমোহিনী। স্ত্রী নীলা সাহা এবং দুই পুত্র: তীর্থ ও সৌধ।
আগামী ০৫ই আগস্ট কবি মহাদেব সাহার ৭৫তম জন্মবার্ষিকী। কবিকে জন্মবার্ষিকীর আগাম শুভেচ্ছা। সৃষ্টিকর্তার নিকট কবির সুস্থ্যতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। এদেশের জন্য, এদেশের মাটি-জল-বৃষ্টির জন্য, কবিতার জন্য কবি আমাদের মাঝে বেঁচে থাকুক। সেই সাথে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ কবি তাঁর জীবনের শেষ সময়টুকু যেন তাঁর প্রিয় দেশের আলো-বাতাসে বসে কবিতা লিখতে পারেন সেই লক্ষ্যে কবিকে দেশে ফিরিয়ে আনা হোক। উল্লেখ্য যে, কবি মহাদেব সাহা গত আড়াই বছরের বেশি সময় ধরে নিজ দেশের ফুলের ঘ্রাণ,পাখির গান, মেঘ, বৃষ্টি হৃদয়বন্দী করে কানাডার শীতলতম এক শহরে নিঃসঙ্গ জীবন কাটাচ্ছেন। এ অনেকটা স্বেচ্ছা নির্বাসন। আমরা জানি, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাহিত্যের অনুরাগী একজন। নিজেও লেখক। বিশেষ করে কব্যানুরাগী। তাই মহাদেব সাহার পাঠক এবং গুণগ্রাহী হিসেবে এ আমাদের দাবি না, বিশ্বাস-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্মোহ কবি মহাদেব সাহাকে তাঁর প্রিয় দেশে ফিরিয়ে এনে কবিতা লেখার পরিবেশ করে দিবেন। কবি আবার তাঁর প্রকৃতি তুলে আনবেন কবিতায়।
কবি, আপনি ভালো থাকুন। আপনাকে এদেশ ভুলে থাকেনি। আমরা আপনাকে ভুলিনি। আপনি ছিলেন, আছেন, থাকবেন- কবিতায়, আমাদের মাথার উপর ছাদ হয়ে। আমরা আপনাকে ভুলবো না। ভালোবাসা ভুলা যায় না। ভালোবাসি দাদা, অনেক বেশি।
এতে সদস্যতা:
মন্তব্যসমূহ (Atom)