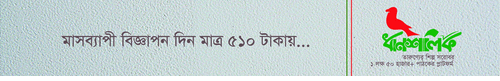ঋণফাহমিদা বারীআওয়াজ টা ভেসে আসছে এদিক থেকেই। একটা শিশুর কান্নার আওয়াজ। গগনবিদারী চিৎকার। মাসুম শিশুর বুকফাটা আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠেছে আকাশ বাতাস।
ময়লা কুড়ানোর পলিথিনটাকে মুখের কাছে গিঁট দিয়ে পেটিকোটের ফিতার সাথে শক্ত করে বেঁধে নিয়েছে করিমন। এভাবে বাঁধলে হাঁটতে সুবিধা হয়। এবড়োথেবড়ো পথটাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অজস্র নুড়ি, ভাঙা শামুকের খোল...বাবলার কাঁটাযুক্ত ঝাড়। পা কেটে রক্ত ঝরতে শুরু করেছে করিমন নেসার। সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে সে হেঁটে চলেছে শব্দ লক্ষ্য করে। তার বুকের মধ্যে যেন ঢাক পেটাতে শুরু করেছে সেই শিশুর কান্না।
পড়ে থাকা একটা বড় গাছের ডাল সরাতেই চোখে পড়লো একটা লাশ। ছিন্নভিন্ন। মাথার খুলি থেকে বেরিয়ে এসেছে বেশ কিছুটা মগজ। চোখ সরিয়ে নিলো করিমন। আরেকটু দূরে পড়ে রয়েছে আরো গোটা পাঁচ ছয়েক এমনি ছিন্নভিন্ন লাশ। বোঝা যায় বেশ কয়েকদিনের পুরনো। লাশের গায়ে পচন ধরেছে, গন্ধ ছড়াতে শুরু করেছে। সারাদেশই এখন এমন হাজার হাজার লাশের ভাগাড়। কত লাশ সরাবে মানুষ!
শিশুটির কান্না এখনো থামেনি। তবে এখন কাঁদছে কিছুটা বিরতিতে, থেমে থেমে। করিমন নেসা হাঁটার বেগ বাড়িয়ে দিলো। সামনে একটা ভাঙা পোড়ো ইটের ঘর দেখা যাচ্ছে। কান্নাটা ভেসে আসছে ওদিকটা থেকেই।
দিনের এই ঝকঝকে আলোতেও ঘরের ভেতরটাতে আলো আঁধারির খেলা। সেই আবছা আলোতেও করিমন দেখতে পেল মেঝেতে পড়ে রয়েছে ফুটফুটে একটা শিশু। শরীরে সদ্য পৃথিবীতে আসার চিহ্ন এখনো পরিষ্কার। দেখে বুঝলো শিশুটি মেয়ে। করিমন তার শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে শিশুটিকে ঢেকে নিলো। করিমনের দু’বছরের সন্তান এখনো বুকের দুধ খায়। বুকে তাই দুধ জমা আছে। শিশুটিকে বুকের কাছে তুলে নিলো সে। তৃষ্ণাকাতর শিশুটি প্রবল বেগে খুঁজে নিলো দুধের উৎস। চোঁ চোঁ করে টানতে লাগলো।
এদিক সেদিকে তাকিয়ে শিশুটির মাকে খুঁজতে লাগলো করিমন। বেশিক্ষণ লাগলো না খুঁজে পেতে। ঘরের এককোণায় রক্তমাখা ছিন্নভিন্ন শরীরে পড়ে আছে একটা শরীর। বুকের কাছে বেয়নেটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত বিভৎসতা। সন্তান জন্মদানের চিহ্নস্বরূপ পরনের শাড়িটি রক্তে মাখামাখি। চোখ দুটো খোলা, প্রাণহীন।
শিশুটিকে বুঝি বুক খুলে স্তন্যপান করাতে চেয়েছিল। হারামজাদারা তাই বুকজোড়াকেই ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। শিশুটিকে রেখে গেছে দয়া দেখিয়ে নয়, নিষ্ঠুর পরিহাস করতে।
করিমন এগিয়ে গিয়ে বন্ধ করে দিল নারীটির চোখের পাতা। আঁতিপাতি করে দেখতে লাগলো তার রক্ত জবজবে শরীরটা। তারপরে কিছু একটা খুঁজে পেয়ে খুশি হয়ে উঠলো সে। রেখে দিল নিজের আঁচলে গিঁট দিয়ে।
তারপরে বাচ্চাটাকে বুকের সাথে জড়িয়ে নিয়ে এদিক সেদিকে আরেকবার দেখে নিয়ে ফিরে এলো নিজের ডেরায়। তার সন্তানটি তখন ক্ষুধায় কাতর হয়ে মাটিতে শুয়ে কাঁদছে।
করিমন শিশুটিকে শুইয়ে দিল নিজের সন্তানের পাশে। যতœমাখা হাতে পরিষ্কার করে দিতে লাগলো তার শরীরের রক্ত আর পিচ্ছিল আঠালো পদার্থ।
তার বাচ্চাটি তখন কান্না ভুলে বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে আছে এই নতুন আগন্তুকের দিকে। করিমন স্বচ্ছ হাসিতে চারদিক আলোকিত করে বললো,
‘তোর বুইন। হ্যার নাম দিলাম আন্না।’ তারপরে ছড়া কাটতে লাগলো সুর করে,
‘এন্না পাতা ভেন্না পাতা...চিরল চিরল গা...ভেন্না পাতায় বসত করে ছোট্ট সোনার ছা...
চল্লিশ বছর পরে
এ্যানা ক্লান্তিহীন পায়ে হেঁটে চলেছে। মাঝে মাঝে থেমে যে একটু পানি খেয়ে নেবে সেই সময়টুকুও যেন তার নেই। প্রতিটি মুহুর্তকেই সে কাজে লাগাচ্ছে। আজ প্রায় এক সপ্তাহ ধরে সে খুঁজে চলেছে একটি নাম। আর সেই নামের পেছনে লুকিয়ে থাকা একজন মানুষকে।
দশ বছরের সুলতান মহা বিরক্ত হয়ে তাকে অনুসরণ করছে। শুরুতে সে যতোটা আগ্রহ আর উত্তেজনা নিয়ে কাজ শুরু করেছিল, তার সেই উত্তেজনা ফুরিয়ে যেতে সময় লাগেনি। মনে করেছিল, মেম সাহেব দুদিন খুঁজবে। খুঁজে পাবে না জানা কথা। আর তারপরই খোঁজখুঁজিতে ক্ষ্যান্ত দিয়ে ফিরে যাবে। মাঝখান থেকে সে নিজে কিছু মোটা অঙ্কের টাকা কামিয়ে নিতে পারবে। কারণ, সফল না হলেও তো আর টাকা না দিয়ে যাবে না! এইসব বিদেশী লোকজন খুব ভালো হয়। এরা সহজে ঠকায় না।
কিন্তু তার সেই ধারণা ভুল প্রমাণিত হতে বেশি সময় লাগেনি। এই মেমসাহেব নিজেও পাগল, তাকেও এই ক’দিনে পাগল বানিয়ে ছেড়েছে। যেখান থেকে যে তথ্য পাচ্ছে, তার পিছনেই ছুটে চলেছে। সুলতানকে রেখেছে পথঘাট চিনিয়ে দেবার জন্য। সুলতান মাঝে মাঝে তাকে ভুল পথে নিয়ে গিয়েও ক্ষ্যান্ত করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ইনি যেন পণ করে এসেছেন, দেখা না করে ফিরবেন না।
এ্যানা এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। তার গার্ডিয়ান মিসেস সুজানা ক্লিভস তার মৃত্যু শয্যায় তাকে একটা আংটি আর একটা ঠিকানা ধরিয়ে দেয়। কাঁপাকাঁপা গলায় বলে,
‘আমি এর কাছ থেকেই তোমাকে এনেছিলাম। আমি তাকে সামান্য কিছু অর্থ দিয়েছিলাম। সে তা রাখতে চাইছিল না। কিন্তু তার স্বামী টাকাটা রেখে দেয়। সে ছিল একজন অতি দরিদ্র মহিলা। ময়লা আবর্জনা ঘাঁটতো আর সেখান থেকে বিক্রি করার মতো কিছু পেলে সংগ্রহ করে দোকানে বিক্রি করতো। সে এই ঠিকানাতে থাকতো। আমি জানি না, এখনো সে সেখানে আছে কী না। সে আমাকে তোমার সম্পর্কে সামান্যই বলেছিল। তুমি যার গর্ভে জন্ম নিয়েছিলে সে তোমার জন্মের পরেই মারা যায়। তুমি জন্মেছিলে সে দেশের যুদ্ধের সময়। আর এই আংটিটা তোমার মা’র কাছে ছিল। সেই মহিলা তার স্বামীর কাছ থেকে এটাকে লুকিয়ে রেখেছিল। তুমি বড় হলে তোমাকে দেবে এই আশায়, তোমার মৃতা মায়ের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে।’
সুজানা ক্লিভসের কাছ থেকে আংটি আর ঠিকানাটা নেয় এ্যানা। সেখানে বাংলাদেশ নামের একটি দেশের ঠিকানা লেখা। ঠিকানাটি ইংরেজীতেই লেখা। তাই সে বুঝতে পারে।
এ্যানা সুজানাকেই তার মা’র মতো মনে করেছে। তিনি ছিলেন সন্তানহীনা। এ্যানাকে বড় করেছেন নিজের সন্তানের মতোই। কিন্তু তার কাছে তিনি সত্য গোপন করেননি কখনো, যেটা চাইলেই করতে পারতেন। বিবেকের একটা কোনো টানে তিনি এ্যানাকে জানিয়েছিলেন, তিনি এ্যানার প্রকৃত মা নন। তার মা বাংলাদেশ নামের একটা ছোট্ট দেশের মানুষ। সেই দেশের জন্মলগ্নে এ্যানার জন্ম হয়েছে।
এ্যানা সুপ্রতিষ্ঠিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা বড় ল’ফার্মের সে একজন নামকরা লইয়্যার। তার স্বামীও একজন লইয়্যার। ওদের ফুটফুটে একটা মেয়ে আছে। এ্যানার স্বামী মার্কিন। তার কাছে এ্যানার প্রকৃত পরিচয় গোপন ছিল না। তিনি সব জেনেশুনেই এ্যানাকে তার জীবন সঙ্গী বানিয়েছিলেন।
এ্যানা তার স্বামীকে জানায়, সে বাংলাদেশ যেতে চায়। হয়তো তার মা’র পরিচয় সে বের করতে পারবে না, কিন্তু যে মানুষটি তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছে তাকে সে একবার দেখতে চায়। তার হাত ছুঁয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতে চায়। এ্যানার স্বামী সংবেদনশীল মানুষ। তিনি না করেননি।
বাংলাদেশে নেমে এ্যানা প্রথম যে সমস্যাটি বোধ করে তা হচ্ছে ভাষা। সে মোটেও বাংলা জানে না। তবে এ্যানা বুদ্ধিমতী। সে জানে কীভাবে অপরিচিত দেশে অজানা ভাষায় টিকে থাকতে হয়। সে প্রথমেই যোগাযোগ করে আমেরিকান এ্যাম্বেসীর সাথে। তারা তাকে ভালো কিছু গাইড সাজেস্ট করে। এ্যানা দুদিনেই বুঝতে পারে এদের কাউকে দিয়েই তার আসল কাজ হবে না। সে যা চাচ্ছে তা তো মোটেও সহজ কিছু নয়। কোনো গাইডই তাকে ঢাকা শহরের অলি গলি বস্তি এত সময় নিয়ে দেখাবে না। তারা ব্যস্ত। এত সময় তাদের কারোরই নেই। তখন সে এদের একজনের কাছেই এই সুলতানের সন্ধান পায়।
সুলতান খুব চালু ছেলে। ইয়েস নো ভেরি গুড টাইপের অল্প বিস্তর ইংরেজিও জানে। এ্যানা’র মনে হয় তার কাজের জন্য এই ছেলেই উপযুক্ত।
যেটুকু তথ্য এ্যানা’র কাছে আছে তা যৎসামান্য। একটা বস্তির ঠিকানা আর সেই মহিলাটির নাম। এ্যানা সেই ঠিকানাতে প্রথমেই হাজিরা দিয়েছে। সেখানে এখন সুউচ্চ ভবন। এ্যাপার্টমেণ্ট। সেই এ্যাপার্টমেন্টও নাকি তৈরি হয়েছে দশ বছর আগে। এ্যানা এ্যাপার্টমেণ্টের বিল্ডার্স কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করে। তারা এ্যানার কথা শুনে হাঁ হয়ে বসে থাকে। একজন ভুলভাল ইংরেজীতে বলে,
‘ম্যাডাম, সম্ভাবনা খুবই কম আপনি যাকে খুঁজছেন তাকে আদৌ খুঁজে পাবেন। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগের কথা। সেই মহিলা বেঁচে আছে কী মরে গেছে কে জানে! আপনার গার্ডিয়ান কাদের মাধ্যমে বাচ্চাটির সন্ধান পেয়েছিলেন তাদের খোঁজ জানা গেলে ভালো হতো।’
ভালো প্রস্তাব। এটা বেশ মনে ধরে এ্যানার। একটা চ্যারিটি মিশনারীর মাধ্যমে এ্যানার গার্ডিয়ান সুজানা ক্লিভস এ্যানার সন্ধান পেয়েছিলেন। এটার নাম তিনি এ্যানাকে আগেই বলেছিলেন। এ্যানা তাদের সাথে যোগাযোগ করে। কিন্তু তারাও খুব বেশি কিছু উপকার করতে পারেন না। সব শুনে বলেন,
তখন যিনি এই চ্যারিটি মিশনারীর দায়িত্বে ছিলেন তিনি মারা গেছেন। তারা যুদ্ধের সময়ে ও পরে জন্ম নেওয়া বেশ কিছু শিশুকে সন্তানহীন এবং দত্তক নিতে ইচ্ছুক দম্পতিদের কাছে দত্তক দিয়েছিলেন। এ্যানা হয়তো তাদেরই একজন।
কিন্তু এ্যানার জিজ্ঞাস্য ভিন্ন। তাকে যে মহিলাটি এখানে নিয়ে এসেছিলেন তার কোনো সন্ধান তাদের জানা আছে কী না। তারা একটা বড় রেজিস্ট্রার খাতা খুলে বসেন। আশাহত হতে হয়। সেখানে ১৯৭৪ এর পরে থেকে তথ্য সংগ্রহ করা আছে। এ্যানা প্রচণ্ড নিরাশ গলায় জানতে চাইলো,
‘এর আগের কোনো রেজিস্ট্রার নেই?’
এ্যানার ব্যাকুলতার কারণেই হয়তো তারা আরো খুঁজে দেখতে সম্মতি জানান। এ্যানা অপেক্ষা করতে থাকে। সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা পেরিয়ে যায়। একসময় তাকে জানানো হয়, খুঁজতে একটু সময় লাগছে। পুরনো কাগজপত্র অনেক নীচে চাপা পড়ে আছে। এ্যানা একদিন পরে যোগাযোগ করলে তাদের জন্য সুবিধা হয়।
এ্যানা তিন সপ্তাহের ছুটিতে এসেছে। ইতিমধ্যেই একসপ্তাহ পেরিয়ে গেছে। আর আছে মোটে দুই সপ্তাহ। এর মধ্যে সন্ধান না পাওয়া গেলে এ্যানাকে হয়তো ব্যর্থ হয়েই ফিরে যেতে হবে। সে তাদের কাছে অনুরোধ জানায় একটু দ্রুততার সাথে খুঁজে দেখার জন্য।
মাঝের এই একদিনেও বসে থাকে না এ্যানা। যুদ্ধশিশু বা যুদ্ধের সময় জন্ম নেওয়া শিশুদের তৎকালীন সমাজকল্যাণ বিভাগের মাধ্যমে বাইরে বিভিন্ন দেশে দত্তক হিসেবে পাঠানো হতো যা বর্তমানে ‘সমাজসেবা অধিদপ্তর’ নামে পরিচিত। বেশ কিছু তথ্য সে পায় এ্যাম্বেসীর মাধ্যমে। সেখানে গিয়েও খোঁজ নেয় এ্যানা। করিমন নেসার কোনো সন্ধান তারা দিতে পারেন না। যেসব শিশুকে মিশনারীজ অফ চ্যারিটির মাধ্যমে দত্তকায়ন করা হয়েছে তাদের কোনো তথ্য সেখানে নেই।
পরদিন এ্যানা আবার ফিরে আসে সেই চ্যারিটি মিশনারীতে। তারা এ্যনাকে এবার পুরোপুরি হতাশ করে না। করিমন নেসা নামক একজন মহিলা একটি শিশুকে একবার তাদের কাছে নিয়ে আসে। সেটা যুদ্ধের প্রায় দুই বছর পরে। তার নাম এবং ঠিকানা তাদের কাছে নথিবদ্ধ আছে। একটা অতি পুরাতন ফাইলে।
এ্যানা সেই ফাইলটি খুলে দেখে। হুবহু এই ঠিকানাটিই তার হাতেও ধরা রয়েছে। তবে একটা নতুন জিনিস খুঁজে পায় সে। প্রায় হলদে হয়ে আসা একটা সাদাকালো ছবি। সেখানে একজন মহিলার কোলে একটা ছোট্ট শিশু। দেড় দু’বছর বয়স। মহিলাটির পাশে একজন লোক। সম্ভবত তার স্বামী। ছবিটির উপরে তারিখ দেওয়া। শুধু সালটা বোঝা যাচ্ছে, ১৯৭৩।
এ্যানা তাদের কাছে অনুরোধ জানায়, এই ছবিটি তাকে দেওয়ার জন্য। প্রথমে মৃদু আপত্তি করলেও একসময় তারা ছবিটি এ্যানাকে দিতে রাজী হন।
চ্যারিটি মিশনারী থেকে বেরিয়ে এ্যানা কিছুটা আশান্বিত হয়। অন্ততঃ তার কাছে এখন একটা ছবি আছে। যদিও দীর্ঘ পুরনো সেই ছবির মানুষকে এখন আর বাস্তবে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, তবু আশা ছাড়তে রাজী নয় এ্যানা। এই আশাটুকুই তো তাকে নিয়ে এসেছে এত দূরে...এত বছর পরে।
আরো আগে আসতে পারতো এ্যানা। কিন্তু সুজানার মৃত্যুর পরেই সে যেন প্রথম উপলব্ধি করে জীবনের তাৎপর্য। বেঁচে থাকার মর্মার্থ। আর এই বেঁচে থাকাটা সম্ভব হয়েছে যে মানুষটির কারণে, তার ঋণের ভার সে যেন আর বইতে পারছিল না। তার হাত ছুঁয়ে একবার সে শুধু তার প্রাণভরা কৃতজ্ঞতা জানাতে চায়।
এ্যানা সুলতানকে ছবিটা দেখায়। কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না তার। না হওয়ারই কথা। এই জনবহুল শহরে এমন হাজার হাজার করিমন নেসার বাস। তাদের বহু অতীতের কোন ছবি দেখে বর্তমানের কোনো কিশোরের মনে কোনো রেখাপাত হওয়ার কথা নয়।
সুলতানের ধৈর্য শেষ। তার বোঝা হয়ে গেছে যে সে এক মহা গাট্টায় পড়েছে। তার স্টকের সেরা ইংরেজী বের করে সে এ্যানাকে বলে,
‘নাইস মিট। নাউ আই গো। মাই মানি।’
এ্যানা সুলতানের মনোভাব মুহুর্তেই বুঝে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে ওঠে,
‘নো নো প্লিজ স্টে। অকে আই উইল গিভ ইয়্যু মোর মানি...’
বলে সুলতানের হাতে ধরিয়ে দেয় কয়েকটি পাঁচশো টাকার নোট। সুলতানের চোখ চকচক করে ওঠে। মন ভরে ওঠে খুশিতে। নিজের মনকে সান্তনা দেয়, হোক একটু ত্যাড়া। মানুষ ভাল আছে। সুলতান থেকে যায়। আবার খোঁজ শুরু হয় এই বস্তি থেকে ঐ বস্তি।
দেখতে দেখতে চলে যায় আরেকটা সপ্তাহ। শেষ সপ্তাহের আজ দ্বিতীয় দিন। এ্যানা ধীরে ধীরে বুঝতে পারছে, তাকে হয়তো ব্যর্থ হয়েই ফিরতে হবে। তাকে এক মহা ঋণের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে একজন মানুষ এই পৃথিবীর বুকে চিরতরে হারিয়ে গেছে। যার কাছে সে আজীবনের ঋণী। তার মা তাকে জন্ম দিয়েছে, এই মানুষটি তাকে দিয়েছে জীবন।
ধীরে ধীরে সুলতানও জানতে পেরেছে, এই মেমসাহেব এই দেশেই জন্মেছেন। যুদ্ধের সময়ে। তাকে যে বাঁচিয়েছিল, সেই মানুষের খোঁজেই তিনি এখানে এসেছেন। সেই মানুষটার নামও তিনি ঠিকমত উচ্চারণ করতে পারছেন না। ক্রেমন্নিসা...এই নাম শুনে বস্তির কোনো মানুষ তার সন্ধান দিতে পারছে না।
মনে মনে কেমন একটু কষ্ট লাগে মেম সাহেবের জন্য। আহারে! মা নাই...বাপ নাই...কারা বাপ-মা তাও জানা নাই! তার তো তবু বাপ-মা আছে। রাতে কাজ শেষে ঘরে ফিরে গেলে মায়ের স্নেহের আঁচলটুকু আছে। তার টাকা নাই এই মেমসাহেবের মতো, তবু মা বলে ডাক দেবার মানুষটা তো আছে!
একদিন খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে ভরদুপুরবেলা বস্তির পাশের পথের ধারেই বসে পড়ে এ্যানা। টিপটপ আধুনিক পোশাক পরিহিতা এক মহিলাকে এভাবে পথের ধারে নোংরা পরিবেশে বসে থাকতে দেখে লোকজন ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে থাকে।
এক রিক্সাওয়ালা কাছে এসে হর্ণ বাজাতে থাকে। সুলতান হাঁক ছাড়ে,
‘যাইবো না। ফুটেন।’
রিক্সাওয়ালা তবু ফুটে না। সুলতানের কাছেই জানতে চায়,
‘ঐ কী হইছে?’
‘হেইডা দিয়া আপনের কী?’
‘ঐ ক কইলাম। দিমু নাইলে এক থাবড়া...’
সুলতান তবু চুপ করে থাকে। রিক্সাওয়ালা ক্রিং ক্রিং করতে করতে চলে যায় একসময়।
এ্যানা অশ্রুসজল চোখে তার ব্যাগে হাত দিয়ে মোটা বাণ্ডিলটার অস্তিত্ত খুঁজে পায়। আগামীকাল সকালে তার ফ্লাইট। চলে যেতে হবে তাকে। তার নতুন দেশ, যা তাকে পরিচয় দিয়েছে সেখানে তাকে ফিরতে হবে। কিছু টাকা এনেছিল করিমন নেসার জন্য। কে জানে কেমন অবস্থায় আছে এখন! হয়তো কিছু কাজে লাগতো! এটা তার ঋণের কিছুমাত্রও লাঘব করতে পারবে না এ্যানা জানে...তবু তার মন কিছুটা শান্তি পেত।
অল্প কিছুক্ষণ ভাবে এ্যানা। তারপরে টাকার মোটা বাণ্ডিলটা প্যাকেটসহ তুলে দেয় সুলতানের হাতে। সুলতান বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে। এ্যানা তার চুলে হাত বুলিয়ে আদর করে। তারপর সুলতানের মতো করে বলে,
‘গো স্কুল। রিড... ওকে? আই গো মাই হোম...’
সুলতান তাকিয়ে থাকে এ্যানার চলে যাওয়া পথের দিকে। বাড়িতে ফিরে চেঁচিয়ে ডাকতে থাকে,
‘মা...দাদী...বাপজান...’
সুলতানের চিৎকারে ছুটে আসে সবাই। ওদের পরিবারটি অনেক ঠিকানা পাল্টে গতমাসেই এই ঝুপড়িতে এসে উঠেছে। এখনো কেউ ওদের তেমন একটা চেনে না। সুলতান প্যাকেট খুলে টাকাগুলো মেলে ধরে প্রত্যেকের হাঁ হয়ে থাকা মুখের সামনে। সবিস্তারে খুলে বলে তার টাকা প্রাপ্তির গল্প আর সেই মেমের ক্রেমন্নিসা কে খুঁজে বেড়ানোর ইতিহাস।
সুলতানের দাদী করিমন নেসা ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে আসে সামনে। টাকাগুলো হাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখে। নাতির গল্প শুনে তার ছানি পড়া চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রু।
হোটেলে বসে এ্যানা তখন তার ব্যাগ গোছাতে ব্যস্ত। হলদে হয়ে আসা করিমন নেসার ছবিটাকে সে পরম যতেœ তুলে রাখে ব্যাগের বুক পকেটে।
যেন ওর নিজেরই বুকের গহীনে...গভীর মমতায়।