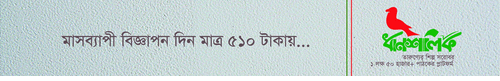সেলিনা হোসেনের উপন্যাসে ভাষা আন্দোলন
সেলিনা হোসেনের উপন্যাসে ভাষা আন্দোলন
অনন্ত পৃথ্বীরাজ
প্রাক্ সাতচল্লিশ ও বিভাগোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯), সোমেন চন্দ (১৯২০-১৯৪২), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১) থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্তÑ বিগত সাত দশকে যাঁরা গদ্য লিখেছেনÑ তাঁদের সাহিত্য পর্যালোচনা করলে আমরা বাংলাদেশের বাংলা কথাসাহিত্যের অঙ্কুরিত অবস্থান থেকে বৃক্ষপ্রতিম হয়ে ওঠার বিষয়টি সহজেই উপলব্ধি করতে পারি।
পঞ্চাশের দশকে বাংলাদেশের কথাসাহিত্য যে অর্ধস্ফূট আবছা অবয়ব নিয়ে দেখা দেয় ষাটের দশকে তা’ সুস্থির মৃত্তিকার উপর দ-ায়মান হয়। গ্রামীণ বিষয় ও ঘটনার উপকরণের পাশাপাশি নাগরিক মধ্যবিত্তের বহির্জীবন ও অন্তর্জীবন এই কালের কথাসাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের (১৯০৭-১৯৭৪) ক্ষমতা দখলজনিত কারণে সৃষ্টি হয় এক ভীতিকর বাক্রুদ্ধ পরিবেশ। এই পরিবর্তমান সমাজপ্রেক্ষিত ও রাজনৈতিক বাক্রুদ্ধকর পরিবেশে ষাটের কথাশিল্পরা পরোক্ষরীতির আশ্রয় নেন এবং নির্মাণ করেন ভিন্নতর প্রতিবাস্তবতা। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের ইতিহাসে ষাটের দশকই সবচেয়ে সফল ও নিরীক্ষামূলক দশক। বিশ্বযুদ্ধোত্তর শিল্পরীতির অঙ্গীকারে ষাটের দশকের কথাসাহিত্যিকেরা আধুনিক। আবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯১১-১৯৮৮), শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮), আবদুল হক (১৯১৮-১৯৯৭), আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩), আনোয়ার পাশা (১৯২৮-১৯৭১), আহমদ রফিক (জন্ম: ১৯২৯), শামসুর রহমান (১৯২৯-২০০৬), মুর্তজা বশীর (১৯৩২-২০২০), হুমায়ুন কাদির (১৯৩২-১৯৭৭), হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩), জহির রায়হান (১৯৩৩-১৯৭১), আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী( জন্ম: ১৯৩৪), সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬), আল মাহমুদ (১৯৩৬-২০১৯), বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (১৯৩৬-২০২০), হাসান আজিজুল হক (জন্ম: ১৯৩৯), জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত (জন্ম: ১৯৩৯), আব্দুস শাকুর (১৯৪১-২০১৩), রশীদ হায়দার (১৯৪১-২০২০), আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১), আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০), সেলিনা হোসেন (জন্ম: ১৯৪৭) প্রমুখ ঔপন্যাসিক ও গল্পকার এ দশকে দ্রুতি ছড়িয়েছেন। ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ বাংলার রাজনীতিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ৫২’ এর ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি আত্ম-উন্মোচন করতে সক্ষম হয়। আর একাত্তরের রক্তাক্ত মুক্তির সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা পাই স্বাধীন সার্বভৌম একটি দেশ; বাংলাদেশ। তাই শিল্প সাহিত্যেও ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। বাদ যায়নি বাংলা ছোটগল্প ও উপন্যাস।
মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ ও অনন্য শিল্পদ্রষ্টা সেলিনা হোসেন (জন্ম: ১৪ জুন, ১৯৪৭)। সেলিনা হোসেনের জন্ম রাজশাহীতে। পৈতৃক নিবাস লক্ষীপুর জেলার হাজিরপাড়া গ্রাম। পিতা এ. কে মোশাররফ হোসেন ও মাতা মরিয়ম-উন-নিসার নয় সন্তানের মধ্যে সেলিনা হোসেন ছিলেন চতুর্থতম। শৈশব ও কৈশোর কেটেছে করতোয়া ও পদ্মা বিধৌত নদী অববাহিকা রাজশাহী শহরে।
রাজশাহীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন শেষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ¯œাতক (সম্মান) ও ¯œাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময় প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততা যেমন ছিল, ততোধিক আগ্রহ ছিল সাহিত্যে। ১৯৬৯ সালে ছোটগল্পবিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্য সেলিনা হোসেন ড. এনামুল হক স্বর্ণপদক লাভ করেন। জীবনের নানামাত্রিকতায় তিনি অনুধাবন করেছেন সমাজ, রাষ্ট্র ও পরিবেশকে। সেই অনুধাবনের বিরল ঐশ্বর্য বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ শোনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, এ চেতনাতেই লালিত হয়েছেন জীবনব্যাপী।১
নিজের জন্ম ও সাহিত্য সাধনা সম্পর্কে সেলিনা হোসেনের সহজ স্বীকারোক্তি স্মরণযোগ্য :
‘১৪ জুন, ২০১৭। একাত্তর বছরে পা দিলাম। জন্মগ্রহণ করেছিলাম সাতচল্লিশ সালে। বড় হয়ে জেনেছি দেশভাগ হয়েছে। পাকিস্তান নামের একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। এই অর্থে আমি দেশভাগ দেখেছি। ভাষা আন্দোলন বুঝিনি। বাহান্নোর সেই সময়ে নিজের ভাষায় কথা বলেছি। কিন্তু মাতৃভাষার মর্যাদা বোঝার বয়স ছিল না। মহান মুক্তিযুদ্ধের একাত্তর আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। একাত্তর আমার জীবনের একটি সংখ্যা বা শব্দ মাত্র নয়। শব্দটি আমার অস্তিত্বের অংশ। এ কারণে একাত্তর বয়সের সূচনার জন্মদিন আমি ভিন্নমাত্রায় দেখছি।’২
সাহিত্যের নানা শাখায় বিচরণ করলেও কথাশিল্পী হিসেবেই তিনি সমধিক খ্যাত। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের নিরন্তন শিল্পসাধনায় তিনি নির্মাণ করেছেন নিজস্ব এক শিল্পভুবন। কথাকার সেলিনা হোসেন বিষয়গৌরবে যেমন বিশিষ্ট্য, তেমনি প্রকরণকলাতেও অনন্য। সেলিনা হোসেন সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক বিশ্বজিৎ ঘোষ- এর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য:
ইতিহাসের গভীরে সন্ধানী আলো ফেলে ঔপন্যাসিক প্রতিবেদন সৃষ্টিতে তাঁর সিদ্ধি কিংবদন্তীতুল্য। বস্তুত ইতিহাসের আধারেই তিনি সন্ধান করেন বর্তমানকে শিল্পিত করার নানামাত্রিক শিল্প-উপকরণ। সমকালীন জীবন ও সংগ্রামকে সাহিত্যের শব্দ¯্রােতে ধারণ করাই সেলিনা হোসেনের শিল্প-অভিযাত্রার মৌল অন্বিষ্ট। এক্ষেত্রে শ্রেণি অবস্থান এবং শ্রেণিসংগ্রাম চেতনা প্রায়শই শিল্পিতা পায় তাঁর ঔপন্যাসিক বয়ানে, তাঁর শিল্পÑআখ্যানে। কেবল শ্রেণিচেতনা নয়, ঐতিহ্যস্মরণও তাঁর কথাসাহিত্যের একটি সাধারণ লক্ষণ। উপন্যাসে তিনি পৌনঃপুনিক ব্যবহার করেছেন ঐতিহাসিক উপাদান, কখনো-বা সাহিত্যিক নির্মাণ।৩
সাহিত্যিক নির্মাণকে ভেঙ্গে নতুন সাহিত্য সৃষ্টির ধারায় সেলিনা হোসেন রেখেছেন প্রাতিস্বিক প্রতিভার স্বাক্ষর। তাঁর উপন্যাসে রাজনৈতিক সময় বা আন্দোলন অধিকতর পরিপ্রেক্ষিত অর্জন করে। নারীর শাশ্বত দৃষ্টি, সনাতন আদর্শ বজায় থাকে তাঁর লেখায়। তবে রাজনৈতিক অনুপ্রেরণাটি অর্জিত হয় সমকালীন বুর্জোয়া শ্রেণিচরিত্রের স্বার্থান্বেষী রূপটি অতিক্রম করবার প্রচেষ্টায়। এ ক্ষেত্রে তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির ঐতিহ্যের প্রতি দৃঢ় ও দায়িত্বশীল। এমন প্রত্যয়ে স্বাধীন ভূখন্ড, স্বায়ত্তশাসিত-বৈষম্যহীন সমাজ ও জাতীয় আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল পর্বগুলো উন্মোচিত হয় কাহিনীগোত্রে। কখনো কখনো জাতীয় চরিত্র প্রতীকায়িত হয় আদর্শের আশ্রয় থেকে। এরূপ প্রস্তাবনায় তাঁর উপন্যাস অনেকক্ষেত্রে সরলকৃত কিংবা পূর্বফলপ্রসূত। ইতিহাসের পুননির্মাণ কিংবা স্বেচ্ছাচারী স্বৈরশাসকের প্রতিমূর্তির প্রতীকায়ন তিনি যেভাবে ঘটান সেটা অনবদ্য এবং অভিনব। ইতিহাসের নান্দনিক প্রতিবেদন বিনির্মাণে সেলিনা হোসেনের সিদ্ধি শীর্ষবিন্দুস্পর্শী। সেলিনা হোসেন তাঁর ‘নিজস্ব ভাবনায় ইতিহাসকে সমকালের সঙ্গে বিম-িত করেছেনÑইতিহাসের কঙ্কালেই নির্মাণ করেছেন সমকালের জীবনবেদ। ইতিহাস ও শিল্পের রসায়নে সেলিনা হোসেন পারঙ্গম শিল্পী। ইতিহাসের সঙ্গে সমকালীন মানবভাগ্য বিম-িত করতে গিয়ে সেলিনা হোসেন, অদ্ভুদ এক নিরাশক্তিতে, উভয়ের যে আনুপাতিক সম্পর্ক নির্মাণ করেন , বাংলা উপন্যাসের ধারায় তা এক স্বতন্ত্র অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। তাঁর উপন্যাস পাঠ করলে বিস্মৃত হতে হয় কোনটা ইতিহাস আর কোনটা কল্পনা।৪
সেলিনা হোসেনের প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা চল্লিশটি। এসব উপন্যাসে যে শুধু ইতিহাস আর রাজনীতিই উঠে এসেছে তা কিন্তু নয়Ñতাঁর লেখনিতে আমরা জীবন ও সমাজ বাস্তবতার চমৎকার মিলবন্ধন লক্ষ্য করি। ‘জীবন যেখানে যেমন’ সেলিনা হোসেন এই আদর্শে বিশ্বাসী। তাই শিল্পমানের চেয়ে জীবনের রূঢ় বাস্তবতা আর উপন্যাসে গল্পের প্রাণ সঞ্চার করে। ইতিহাসের পরতে পরতে যে রিরংসা, লোভ, ধ্বংসের হাতছানি তিনি তাঁর উপন্যাসে এ বিষয়গুলো উপজীব্য করেছেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাঙালির জাতীয় জীবনে এক বেদনাঘন অথচ গর্বের দিন। এ দিনে বাংলার দামাল ছেলেরা নিজের জীবনকে তুচ্ছ করেÑ মায়ের মুখের ভাষার জন্য বুকের রক্তে ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত করেছিল। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে গবেষক অনিক মাহমুদ লিখেছেন:
বাঙালির জাতীয় চেতনার উদ্বেলনে যখন ঘনীভূত হল রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, তখন নিরুপায় শাসকচক্র নতুন করে শুরু করল ষড়যন্ত্র। সা¤্রাজ্যবাদের জটাজালের মতই হিং¯্র হয়ে উঠল তাদের জাতিসত্তাবিরোধী সাংস্কৃতিক তত্ত্ব। বাংলা বানান সংস্কারের নামে উদ্ভট পরিকল্পনা কিংবা আরবী হরফে বাংলা লেখার ষড়যন্ত্র করতেও তারা দ্বিধা করল না। এভাবে ক্রমাগত তিনটি বছর রাজনৈতিক ডামাডোলে বাংলা ভাষার আন্দোলনকে ধামাচাপা দিয়ে তারা এ ভাষার মূলোৎপাটনে অনমনীয় হয়ে ওঠে। ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের (১৮৯৬-১৯৫১) তিরোধানের পর খাজা নাজিমউদ্দীন (১৮৯৪-১৯৬৪) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯৫২ সালে ২৬ জানুয়ারি ঢাকার এক জনসভায় বক্তৃতাকালে তিনি জিন্নাহ্’র কথার পুনরাবৃত্তি করেন এবং উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার পূর্ণ ঘোষণা দেন। তখন দেশব্যাপী শুরু হল দুর্মর আন্দোলন। ছাত্র-যুবক-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে কৃষক-শ্রমিক-সাধারণ মানুষ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল এই সংগ্রামের দাবদাহ : ‘রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই’। এর মধ্যে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি ৪ঠা ফেব্রুয়ারিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ২১ শে ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী ভাষার দাবীতে ধর্মঘট পালিত হবে। ২০ শে ফেব্রুয়ারি সরকারী ভ্যান থেকে সন্ধ্যার আগে ঘোষণা করা হল যে, সরকার দেশে ১৪৪ ধারা জারী করেছে। সভা-সমিতি, মিছিল কিংবা একসঙ্গে দশজন একত্র হওয়া নিষিদ্ধ। ১৪৪ ধারা শুধু ঢাকা শহর নয় একমাসব্যাপী সমগ্র দেশ জুড়ে। ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারিতে দেশব্যাপী হরতালের ডাকে শাসকচক্র আশ্রয় নিল দমননীতির। মাতৃভাষার মহাসংগ্রামে ক্ষাত্রশক্তির জারীকৃত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ধাবমান ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ চালল গুলি। ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত হল রফিক, সালাম, জব্বার, বরকতের মতো তরণ ছাত্র-যুবার বুকের রক্তে।৫
১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ঘটনা প্রবাহে ঔপন্যাসিক জহির রায়হান লিখেছেন ‘আরেক ফাল্গুন’ (১৯৬৯) এবং কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমান লিখেছেন ‘আর্তনাদ’ (১৯৮৫) প্রভৃতি উপন্যাস। সেলিনা হোসেনের ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক দুইটি উপন্যাস হচ্ছে ‘যাপিত জীবন’ (১৯৮১) ও ‘নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি’ (১৯৮৭)। ‘যাপিত জীবন’ উপন্যাসে সমকালীন রাজনীতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বস্তুরূপের উপস্থাপনার সাফল্য নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করা হলেও এ উপন্যাসে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যতিক্রমী প্রাণ প্রবাহের সুর অনুরণিত হয়েছে। এ উপন্যাসের শুরু উনিশ সাতচল্লিশ সালের দেশ বিভাগের পর। আর সমাপ্তি ঘটেছে বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। সেলিনা হোসেন সময়ের ইতিহাসকে চরিত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট করেন। সেখানে ‘সময়’ই চরিত্র। সোহরাব হোসেন, মারুফ ও তার স্ত্রী সুমনা, জাফর, আঞ্জুম এসব চরিত্র পারিবারিক জীবনে দৈনন্দিনতার ভেতরে নিজস্ব মূল্যবোধ ও রুচির চর্চা করে। সেখানে রাষ্ট্রের আন্দোলন সংগ্রামের সাথে তাদের সম্পৃক্তিও বাড়ে। চরিত্রগুলো যেন সমস্ত ঘটনার অংশ হয়ে যায়। ‘যাপিত জীবন’ উপন্যাস প্রসঙ্গে প্রথমা রায় ম-লের মন্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য:
নতুন দেশে জীবনযাপন শুরু হয় নতুন অস্তিত্বে। ব্যক্তিগত ভালোবাসা ও স্বদেশ প্রেমে একাকার হয়ে বাঙ্গময় হয়ে ওঠে; সঙ্গে আসে সমকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও রাজনৈতিক ঘূণাবর্ত। উপন্যাসের সূচনায় যে ভয়-ভীতির চিত্র উদ্ভাসিত তা থেকে বেরিয়ে আসার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি।৬
‘যাপিত জীবন’ উপন্যাসের পটভূমি ’৫২-র ভাষা আন্দোলন। উপন্যাসের নায়ক জাফর জীবনের কথা বলে জীবনেরই বিনিময়ে। ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন জাফরের স্বচ্ছ প্রতীকচিত্রে বাঙালির শেকড় আর অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করেছেন তাঁর এ উপন্যাসে। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞাপনের এ যুগল মাত্রায়, তরঙ্গসঙ্কুল রাজনৈতিক পটভূমিতে দাঁড়িয়ে নিজের চাষের ভূমিতে প্রতিনিয়ত ঘুরে ঘুরে একজনশিল্পীর অজানা প্রদেশের নিত্য উদ্ভাবন-কর্মের শিল্পীতরূপ ‘যাপিত জীবন’। এ উপন্যাসের নায়ক প্রতিটি মুহূর্তে ঘোষণা করে বেড়ায় তাঁর বাঙালি অস্তিত্ব। এখানেই তাঁর শেকড় প্রথিত রয়েছে। উত্তরাধিকারসূত্রে এদেশেই তাঁর বসবাস ও বেড়ে ওঠা। জন্মের পর থেকে এদেশের আলো-বাতাসে সে বড় হয়েছে। মুখে বুলি ফোটার সাথে সাথে সে শিখেছে নিজের মায়ের ভাষা বাংলাকে। তাই মায়ের ভাষাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে রাষ্ট্রীয় ফরমান সে মেনে নিতে পারে নি। নিজের মৃত্তিকারসে জারিত স্বকীয় বিকাশের সমস্ত প্রয়াস ভর করে বাঙালি জাতিসত্তার প্রতিনিধি জাফরের মাঝে। জাফর তখন হয়ে ওঠে বাঙালির প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। জন্ম নেয় নতুন শ্লোগান : রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। পটভূমির দিক থেকে বিচার করলে এ উপন্যাসের কাহিনী আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য খুবই গুরুত্ববহ। পড়তে পড়তে ভাষা আন্দোলনের অগ্নিঝরা দিনগুলোতে চলে যাওয়া যায়। বিশ^বিদ্যালয়ে পড়–য়া একজন ছাত্রের জীবনে ভাষা আন্দোলন; পারিবারিক ও রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে ‘যাপিত জীবন’ উপন্যাসে। ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাসের একটি প্রধান বাধা হলো কল্পনায় চরিত্রগুলোর মধ্যে ইচ্ছে মতো প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা। মূল চরিত্র জাফরের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটেছে। কাহিনীর যোগসূত্রে জাফরের চাইতে উপন্যাসে তাঁর বাবা-মা অথবা বড় ভাইয়ের চরিত্র যেন বেশি জীবন্ত মনে হয়। ‘যাপিত জীবন’ উপন্যাসে একটি সাধারণ পরিবারের টুকরো টুকরো নানা ঘটনার সাথে জাতীয় আন্দোলনের সম্পৃক্ততা আমাদের হাজার বছরের পারিবারিক বন্ধন ও রাজনৈতিক সচেতনতার ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছে।
শ্রেণিবিন্যস্ত বেড়িপরা সমাজে উৎকণ্ঠিত জাফরের বিবেক-কল্পনা ও মণীষা। মহৎ আদর্শের জন্য ছোট ছোট জাগতিক মোহকে বিসর্জন দিয়ে উপবাসী জাফর জন্মের ঋণ পরিশোধ করে রাজপথে-মিছিলে মৃত্যুর সাথে আত্মীয়তা করে। ঔপন্যাসিক ঐতিহাসিক সত্যকে সাহিত্যে জীবন্ত করে রাখার জন্য ভাষা আন্দোলনে যোগদানকৃত ভাষা শহিদদের প্রতীকী চরিত্র হিসেবে জাফরকে সার্থক করে তুলেছেন। স্থির, নিথর, নিশ্চল, নিস্পন্দ, নিঃশব্দ দৃষ্টি তাঁর। বিহ্বল, অবিন্যস্ত অর্থনীতির জমাট ধূসর মেঘের মাঝখানে সচেতন ধারালো তির্যক আলোকরশ্মির মতো সেলিনা হোসেন যেন পরিব্রাজকের দৃষ্টিতে এ উপন্যাসের চরিত্রগুলো নির্মাণ করেছেন। ইতিহাসের সাথে মিল রেখে কল্পনা ও বাস্তবের এক অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে ‘যাপিত জীবন’ উপন্যাসের ঘটনা আবর্তে।
ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেনের রাজনৈতিক সচেতনতা এবং ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে আরও একটি সার্থক উপন্যাস হলো ‘নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি’। ১৯৮৬ সালে উপন্যাসটি রচিত হলেও এর কাহিনী ও ঘটনা বাঙালির অতীত ঐতিহ্য স্পর্শ করেছে। ১৯৪৭-এ দেশভাগের পরে ঢাকা কেন্দ্রীক সাহিত্যচর্চা; রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দিয়ে উপন্যাসের কাহিনী শুরু। ঘটনা আবর্তিত হয়েছে উনিশ বছর বয়সী টগবগে যুবক ও তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দকে নিয়ে। দ্বিতীয় বিশ^যুদ্ধকালীন সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়া সা¤্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে কয়জন মস্তিষ্ক চাষি কলম ধরেছিলেন সোমেন চন্দ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন মার্কসবাদী আদর্শের অনুসারী। মিডফোর্ট মেডিকেল কলেজের মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও টাকার অভাবে পড়াশোনা শেষ করতে পারেন নি। তবু, কারও কাছে দ্বারস্থ নন। অন্যায়ের কাছে কখনো মাথা নত না করা এই যুবক বরং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন দৃঢ়ভাবে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বলি হতে হয় সচেতন এই মানুষটিকে। উপন্যাসের বর্ণনায় তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া কিছু পরিবারের চিত্র নিখঁতভাবে আঁকা হয়েছে। ‘নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি’ উপন্যাস সম্পর্কে গবেষক আমিনুর রহমান সুলতান লিখেছেন:
‘নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি’ উপন্যাসে সেলিনা হোসেন মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রস্তুতিকাল এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবে তাঁদের উত্থানের সাফল্য ঐতিহাসিক চরিত্র (সোমেন চন্দ) বিকাশের মধ্য দিয়ে নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। ‘নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি’ উপন্যাসে ঢাকার প্রগতিশীল আন্দোলনের পটভূমিতে ভাষা আন্দোলনে প্রগতিশীল মধ্যবিত্তের যে ভূমিকা এবং ক্রমবর্ধমান গতিবেগ সঞ্চারিত ছিল তা উঠতি মধ্যবিত্তশ্রেণিকে কেন্দ্র করেই সংঘটিত হয়েছে। এ উপন্যাসের প্লট রচিত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু পূর্বকাল থেকে এবং সমাপ্তি ঘটেছেÑ ১৯৫৩ সালে জেলখানায় বসে মুনীর চৌধুরীর ‘কবর’ নাটক লেখা হচ্ছে এ পটভূমিতে।৭
উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিশ্ববিদ্যালয় পড়–য়া ছাত্রনেতা মুনীর। আসাদ, সালাম, রাহাত, বেণু, নীলা, রেণু এরা উপন্যাসের মূল কাহিনির সাথে কেন্দ্রীয় ভূমিকার সহায়ক শক্তি রূপে কাজ করেছে। মাত্র তিন দিনের ঘটনা প্রবাহে আমরা দেখতে পাই একুশের চেতনা কীভাবে তিমির বিনাশী আয়োজনে প্রগতিশীল ছাত্রদের আগামীর পথ নির্মাণে এগিয়ে যায়। তিন দিনের কাহিনীতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষক গোষ্ঠীর নিপীড়ন, দমননীতি, পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শোষকগোষ্ঠীর নিপীড়ন ও দমননীতি পাশপাশি মুক্তিকামী বাঙালির অপ্রতিরোধ্য সাহসিকতা যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি বাঙালির চেতনাকামী ঐতিহ্য কিভাবে উত্তরাধিকার খুঁজে পেয়েছে তা বিধৃত হয়েছে। এ উপন্যাসের ভূগোল নির্মিত হয়েছে ঢাকার বুকে। ব্যক্তিগত অনুভব, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পথ আবিষ্কার করেছে প্রেমময় পথ ধরে, রোমান্টিক মনের আবহে।
বাংলার ইতিহাস হাজার বছরের ইতিহাস। ব্রিটিশ রাজত্বে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে বাঙালি তাঁদের আত্মপরিচয়ের সন্ধান পায়। বঙ্গভঙ্গ রদ হয় বটে কিন্তু বাঙালির বুকে নিজেদের অস্তিত্ত্ব অনুসন্ধানের বাসনা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এদেশের মানুষ অবদান রাখতে শুরু করে। কিন্তু ধর্ম তাঁদের কাছে আজীবন পরম শ্রদ্ধার জায়গা। আর ব্রিটিশ বেনিয়া এই ধর্মকে পুঁজি করেই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়ে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। অবশেষে হিন্দু-মুসলমানের বৃহৎ ঐক্য বিভক্ত করার মানসে ১৯৪৭ সালে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের মাধ্যমে পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান (ভারত)-এর জন্ম হয়। এরপরও বাঙালির জাতীয় জীবনে স্বস্তি আসেনি। শুধু ধর্মের মিলের কারণে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পাকিস্তানের সাথে যৌথ জীবনযাপন শুরু করলেও তা বেশি স্থায়ীত্ব লাভ করেনি। বাঙালির মানসে প্রথমেই যে আঘাত আসে তা হলো, ভাষার প্রশ্ন। পশ্চিম পাকিস্তানিরা ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশের ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এক করতে গিয়ে বাঙালির ওপর চাপিয়ে দেয় প্রবল বৈষম্য। পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮) উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলে দেশভাগের পরপরই ঢাকা উত্তাল হয়ে ওঠে। মিছিলের নগরীতে পরিণত হয় পুরো ঢাকা শহর। ছাত্র সমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সে দিনের সেই আন্দোলনে সোমেন চন্দ ছিলেন না; কিন্তু মুনীর চৌধুরী ছিলেন। উপন্যাসের প্রথমাংশে সোমেন চন্দ, আসাদ, সালামদের প্রাধান্য থাকলেও দ্বিতীয়াংশের নায়ক লেখক মুনির। সোমেন চন্দের লেখার প্রশংসা করতেন মুনীর। তিনি নিজেও লেখালেখি আর রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। বায়ান্নার ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন বলে তাকে জেলে যেতে হয়। কারাগারের অন্ধকার কুঠিতেও তাঁর কলম থামেনি। তিনি লিখতে শুরু করেন ‘কবর’ নামে একটি নাটক। লেখা তখনও শেষ হয়নি। উপন্যাসে এই অংশের বর্ণনায় সেলিনা হোসেন লিখেছেন:
এখনো শেষ হয়নি নাটক, মুনীর লিখছে, আর অল্প বাকি। বাহান্নর একুশের পটভূমিতে রচিত হচ্ছে নাটক। জেলখানায় ঘণ্টা ঢং- ঢং করে জানিয়ে যায় সময়। থেমে থেমে ঘণ্টা বাজে লেখা থামে না, কলম এখন যাদুর প্রদীপের ঘষা, একটা শিল্পিত দৈত্য বেরুচ্ছে। রচিত হচ্ছে মুনীরের ‘কবর’।৮
বাংলাদেশের সাহিত্যের ধারায় সেলিনা হোসেন, প্রকৃত প্রস্তাবেই নির্মাণ করেছেন নিজস্ব একটা শিল্প ভুবন। সাহিত্যিক হিসেবে তিনি সামাজিক দায়বদ্ধতাকে কখনই ভুলে যাননি। ফলে তাঁর সকল রচনার পশ্চাতে আমরা অনুভব করি সামাজিক অঙ্গীকার, থাকে প্রগতিশীল ভাবনা। তাঁর শিল্পীমানসে সবসময় সদর্থক ইতিহাস চেতনা জাগ্রত থাকে বলে মানুষকে তিনি ম্যাক্রো-ভাবনায় আয়ত চোখ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। মাইক্রোভাবনা প্রাধান্য পায়নি বলে তাঁর মানুষেরা কখনো খ--জীবনের আরাধনায় মুখর হয়নি, নষ্ট হয়নি জীবনের উপাসনা। যে জীবন সাধারণের কিংবা বড় কারো সে জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে আন্দোলিত হয় তাঁর বিষয়-বৈচিত্র্য। প্রবল মুন্সিয়ানায় ঘোরেন চেনা জগতের অচেনা পথে। ফিরে ফিরে দেখেন আপন-আলোয় উদ্ভাসিত নানা জীবনের কল্পরূপ। ষাটের শেষপ্রান্ত থেকে ঘর্মাক্ত কলমে, অগ্রসরমান, প্রস্তুতিতে প্রতিক্ষণের জায়মান জীবন-সমস্যার সমাধানকল্পে প্রতিবাদের পোস্টার সেঁটে চলেছেন গদ্য-মজুর সেলিনা হোসেন। নিজের অন্তর্গত রক্তক্ষরণের বিন্দু বিন্দু ঋণ পরিশোধ করেন তিনি নিজেরই প্রতিবাদী দর্শনের শিল্পিত রূপ দিয়ে। তাই সেলিনা হোসেন সমকালীন বাংলা কথাকলার অন্যতম প্রতিভাধর বহুমাত্রিক শিল্পী অভিধায় ভূষিত হয়েছেন।
সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রিকা :
১ . কামরুল ইসলাম, ‘বহুমাত্রিক কথাশিল্পী সেলিনা হোসেন’ বঙ্গীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত সেলিনা হোসেনের ৭০তম জন্মবার্ষিকী পত্রিকা। প্রকাশকাল: ১৪ জুন, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।
২ . সেলিনা হোসেন, ‘ফিরে দেখা আপন ভুবন’ বঙ্গীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত সেলিনা হোসেনের ৭০ তম জন্মবার্ষিকী পত্রিকা। প্রকাশকাল: ১৪ জুন, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।
৩ . বিশ্বজিৎ ঘোষ, ‘সেলিনামঙ্গল’ বঙ্গীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত সেলিনা হোসেনের ৭০তম জন্মবার্ষিকী পত্রিকা। প্রকাশকাল: ১৪ জুন, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।
৪ . শহীদ ইকবাল, ‘বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাস’ (১৯৪৭-২০০০), ২০১৪, পৃষ্ঠা ১৫৫-১৫৬, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।
৫ . অনিক মাহমুদ, শওকত ওসমানের কথাসাহিত্যে জাতীয় আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৯১, ঢাকা, উত্তরাধিকার, ১৯শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ সম্পাদিত), কার্তিক-পৌষ ১৩৯৮/ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯১, বাংলা একাডেমী, পৃ. ৩-৪
৬ . প্রথমা রায় ম-ল, ‘সেলিনা হোসেন ও বাংলা সাহিত্য’, সঞ্জীব কুমার বসু সম্পাদিত, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বৈশাখÑআষাঢ় ও শ্রাবণ, আশ্বিন সংখ্যা, ১৪০৫, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৮২ ।
৭ . আমিনুর রহমান সুলতান, ‘বাংলাদেশের উপন্যাস নগরজীবন ও নাগরিক চেতনা’, ২০০৩, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১১৯।
৮ . সেলিনা হোসেন, নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি, ১৯৮৭, কথামেলা প্রকাশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১২০।
* অনন্ত পৃথ্বীরাজ, কবি, কথাকার ও এম ফিল গবেষক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর। মোবাইল নং : ০১৭২৫৪১২১৮৬ , ইমেইল : ধহড়হঃড়ঢ়ৎরঃযারৎধল@মসধরষ.পড়স
একটি জীবননাশের গল্প !
একটি জীবননাশের গল্প
অনুপম হাজারী
মিতুর কবরের পাশে মারুফ হাঁটুগেরে বসে আছে। দু’হাত মেলে দিয়ে আকাশের দিকে মুখ করে বেশ খানিকক্ষণ ধরে অঝোরে কাঁদছে। ক্লান্ত দু’চোখে সব কিছু যেন ঝাপসা, তবু মনের মধ্যে অনুশোচনার অনুভূতিটা বেশ স্পষ্ট। মিতুর জন্য আল্লাহর কাছে বিচার চাইতে চাইতে সেদিনকার কথাগুলোই একের পর এক মনে পড়ে যাচ্ছে মারুফের।
মারুফ- হ্যালো।
মিতু- হ্যাঁ, হ্যালো কেমন আছ?
মারুফ- জানি না, তুমি এখন পার্কের পাশের কাজী অফিসটাতে চলে আসতে পারবে? আজকে বিয়ে করব।
মিতুর বোধহয় ব্যাপারটা মজা লেগেছে, মজা নিয়েই সে বলল,
-অবশ্যই পারব, তা আজকে বিয়ে হলে কালকে কি হবে?
মারুফ ভীষণ গম্ভীর। সে জানে মিতু এটা বিশ্বাস করছে না, মজা ভাবছে, তবু সে কিছু বুঝানোর চেষ্টা করছে না, জবাব দিয়ে যাচ্ছে। কিছু বিষয় সে নিজে বুঝে নিক, তাতে তার আগ্রহ কতটুকু সেটা প্রকাশ পাবে।
-কালকে ফুলশয্যা।
-পরের দিন?
-সংসার।
এবার মিতু কিছুটা গম্ভীর হয়ে এল, সে বোধহয় বুঝতে পারছে।
-তা কতদিন চলবে সে সংসার?
-আজীবন।
-তুমি কি সত্যিই আজকে বিয়ে করার জন্য বলছ?
-বলছি, আসতে কতক্ষণ লাগবে বলে দিও, সবকিছু হাতের নাগালে করে রাখতে হবে।
-ঠিক আছে, আমি তাহলে ১১ টা নাগাদ পৌঁছে যাব। তুমি সব ঠিকঠাক করে রেখ।
-রাখব।
মিতুর তৎক্ষণাৎ সাড়ায় মারুফের বুকের বড় একটি চাপ যেন সরে গেল। ফোন কেটে সে বড় একটা দম নিল। যাক, এবার বাবা রাজি না হলেও তার আর দরকার নেই। দেড় বছর ধরে সে বেসরকারি একটি অফিসে মোটামুটি ভাল বেতনে চাকরি করছে, অল্প কিছু টাকাও জমিয়েছে ,তবুও আজ দেড়টা মাস ধরে তমার ব্যাপারে বলে বলেও বাবাকে কোনভাবেই রাজি করানো যাচ্ছিল না। তার সেই এক কথা, মেয়ে বেশি লম্বা, তার উপর হয়েছে সুন্দর আর বড়লোকের মেয়ে, এমন মেয়ের জমিনে পা পড়বে না, শ্বশুর-শাশুড়িকে বাঁকা বাঁকা কথা শোনাবে, কোনভাবেই রাজি হওয়া যায় না। না! আর ধৈর্য্য ধরা যাচ্ছে না, পালিয়েই বিয়ে করে নিতে হবে। আজ বাবাকে দেখিয়ে দিতেই হবে তার ভালবাসায় কতখানি জোর আছে, ঠিক কতখানি জোর, আর বাবার পুরনো দিনকার ধারণাটায় কতখানি ভুল আছে, ঠিক কতখানি ভুল! ভালবাসাটাই এখন ইম্পর্টেন্ট, কোন মিথ্যা অহংকার না।
মিতু সেদিন নিজের মায়ের লাল বেনারসিটি পড়ে পার্কে হাজির হয়েছিল, কাজী অফিসে ঢুকল মারুফকে সাথে নিয়েই। তারপর বন্ধু-বান্ধব আর কিছু পরিচিতজনদের উপস্থিতিতে মারুফ আর মিতুর বিয়ে হয়ে গেল। তখন সবার মনে খালি একটাই দোয়া ছিল, ‘দুজনের সংসারটা অনেক সুন্দর হোক!’ সে সৌন্দর্য্য যে কোথায় গিয়ে শেষ হওয়ার ছিল তা কি কেউ আন্দাজ করতে পেরেছিল?
সেদিন বিয়ের পর মারুফ মিতুকে নিয়ে নতুন বাসায় উঠল, তাদের বাসর হল, নতুন বাসায় তাদের নতুন সংসার শুরু হয়ে গেল। কোন ঝামেলা ছিল না, মিতুর পরিবার মিতুকে খুঁজে পেয়েও কিচ্ছুটি বলল না, তাদের একমাত্র চাওয়া মেয়েটা সুখী হোক। মারুফের অফিস নিয়ম মতোই চলতে থাকল। সকালে অফিস, রাতে বাসায় ফেরা, তারপর মিতুর সাথে কখনো ছাদে বসা, ছাদে বসে ঠান্ডা হাওয়ায় আকাশ দেখা, কখনো বা খুঁনসুটি আর গল্পে মজে থাকা, কখনো কখনো শখের বশে দু’জনে একসাথে রান্নাবান্না করা, ছুটির দিনে ইচ্ছেমতো জায়গায় ঘুরতে যাওয়া, সব মিলিয়ে দুজন মিলে স্বপ্নের মতো সুখী একটি সংসার পাতা।
সুখের ঘোরেই যখন দুজনের সুখী সংসারটা চলছিল তখনই বিশ্বব্যাপী একটু একটু করে গুঞ্জন শুরু হচ্ছিল নতুন এক বিপর্যয়ের। যে বিপর্যয়ের কথা মানুষ আগে শোনেনি, যে ঝড়, সর্বনাশা ঝড় মানুষ আগে দেখেনি, যে দিনের কথা মানুষ আগে কখনো ভাবতে পারে নি এমন দিন, কালো একটি ছায়া ধেঁয়ে আসছিল সবার জীবনের দিকে, যে কালো ছায়া এমনই হাজার-লক্ষ বা হয়ত কোটি কোটি সংসার, স্বপ্নকে হুমকির মুখে ফেলে দেবে। সে গুঞ্জন ধীরে ধীরে বাড়তে থাকল। সে গুঞ্জনের নাম দেয়া হল নভেল করোনা ভাইরাস, একটি ভাইরাস যেটা খুব সহজেই মানুষ থেকে মানুষে ছড়াবে আর একেকজন মানুষকে একেকটি যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু দেবে।
মাস কয়েক পর টেলিভিশন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, মানুষের গল্প-আড্ডা সবখানেই এ ভাইরাসের খবর, মূলত এ খবরটাই শুধু শোনা যেতে লাগল। কিছুদিন পর সরকার সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে দিল, সেনাবাহিনী, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী সে নির্দেশনা অনুযায়ী মানুষকে ঘরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে যেতে লাগল। কয়েক মুহূর্তে আমাদের পরিচিত পৃথিবীটা পুরোপুরি পাল্টে গেল যার কথা মানুষ আগে কল্পনা করে নি, এ যেন ভিন্ন এক গ্রহ যেখানে বাঁচতে হলে এভাবেই বাঁচতে হয়। মারুফদের অফিসটাও বন্ধ ঘোষণা করা হল। তবে মারুফের চিন্তা ছিল না। কয়েকমাস বন্ধ পড়ে থাকলেও তার খেয়ে পড়ে চলতে সমস্যা হত না, চিন্তা যা ছিল তা শুধু এই যে তার চাকরির নিশ্চয়তাটা তারা দিতে পারল না। হতে পারে সব স্বাভাবিক হয়ে গেলে তাকে নতুন চাকরি খুঁজে দেখতে হবে। আরেকটা চিন্তা, আরেকটা! সে চিন্তা সকলের, তার যত আপন প্রিয় মানুষ, তারা সবাই এ মহাবিপর্যয় কাটিয়ে টিকে থাকতে পারবে তো? একদিন মিতুর সাথে বসে রাতের খবরটা দেখতে দেখতেই মারুফের মন কেমন করে উঠল। বাবার সাথে রাগ করে কথা বলা হয় না অনেকদিন, আজকে একটা ফোন দিয়েই দেখা যাক।
-আব্বা!
মারুফের গলা শুনেই তার বাবা যেন একেবারে আবেগাপ্লুত হয়ে উঠল। হওয়ারই কথা, বিয়ের পর পরিবারের সাথে সব যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছিল মারুফ, হঠাৎ করে যোগাযোগ করে বসলে বাবার মনে আবেগ তো উতলে উঠবেই।
-বাবা রে, কেমন আছিস বাবা?
-ভালো আছি আব্বা, তোমরা কেমন আছ?
-আল্লাহ্ ভালো রাখছে। বৌমা কেমন আছে রে?
-আছে, ও ভালো আছে।
-তোরা তো একা থাকিস, দেখছিস তো দেশের কি অবস্থা, আশেপাশে কেউ না থাকলে দরকারে কেউকে হুট করে পাবি না, চলে আয় না বাবা।
-আব্বা এখন তো আর সম্ভব না, সবকিছু বন্ধ। তোমরা সাবধানে থেকো, বাইরে যেও না, বাজার লাগলে আবিরকে বলো, ও অনলাইনে অর্ডার করে নিবে। আর বাসায় সবাইকে বলবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে।
-করতেছি বাবা, সেভাবেই করতেছি, তোরাও সাবধানে থাকিস, আর কোন দরকার হলে ফোন করিস, কোন না কোন ব্যবস্থা হবে।
-ঠিক আছে আব্বা, আম্মা কোথায়?
-তোর আম্মা ঘুমায়, দাঁড়া ডাকি।
-না না আব্বা, থাক, পরে কথা বলে নিব। আম্মাকে আমার সালাম জানিও, আর আবিরকে বলো এ সুযোগে আউটসোর্সিংটা শেষ করে নিতে।
-বলব। শোন বাবা, একটা কথা বলি, বৌমার সাথে বিয়ের জন্য আমাদের মত ছিল না ঠিকই, কিন্তু ঐ মেয়েকেই যদি তোর বিয়ে করার ছিল সেটা আমাদের তখন বুঝাতেই পারতিস, একটা মত বজায় রাখার জন্য তো ছেলেকে ফেলে দিতে পারতাম না। তাই বিয়ের পর তোর ফিরে আসা উচিত ছিল বাবা। যাই হোক, যা হবার হইছে, তোর আম্মা নতুন বৌ ঘরে তোলার জন্য মুখিয়ে আছে, সবকিছু আগের মতো হলে বৌমাকে নিয়ে চলে আসবি, ঘরের বৌকে আর বাইরে রাখতে দেব না।
বাবার কথায় এমন মহাবিপর্যয়েও মারুফের মনে শান্তির একটা সজোর হাওয়া বয়ে গেল।
-ঠিক আছে আব্বা, তোমার কথা আর ফেলব না। যা করেছি তার জন্য ক্ষমা করে দিও।
-দিলাম বাবা, আর মন খারাপ রাখবি না, ভালো থাকিস।
-আচ্ছা আব্বা, তোমরাও সাবধানে থেকো।
-আচ্ছা।
-আচ্ছা রাখছি।
সেদিনের পর মারুফ আরো স্বস্তি, আরো বিশ্বাস নিয়ে দিন কাটাতে লাগল। একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে, সব ঝড় থেমে যাবে, একদিন সবাই একই ছাদের নিচে বসে গল্প করবে, এক টেবিলে বসে ভাত খাবে, আর তার মা কথায় কথায় শুধু নতুন বৌয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে, আর রাতে খাওয়ার পর শুতে গিয়ে মারুফের বুকে মুখ গুঁজে মিতু ইচ্ছেমতো কাঁদবে, তার জীবনের প্রবল সুখের কান্নাটি কাঁদবে।
দিন যেতে লাগল, সপ্তাহ কেটে গেল, কেটে গেল একটি মাসও। ভালোই হত যদি এমন করেই কয়েকটা মাস কেটে যেত, তারপর সব ঝড় থেমে গেলে মারুফ বৌ নিয়ে তার পরিবারে গিয়ে উঠত, আপন মানুষগুলোর সাথে গিয়ে মিশত। কিন্তু মাস কেটে যাওয়ার পরের কয়েকটা দিন যেন আর কাটতে চাইল না। মিতুর একটা সমস্যা ছিল। তার হঠাৎ হঠাৎই শ্বাসকষ্ট উঠে যেত, বিশেষ করে ধূলো-বালি কিংবা রাঁধতে গিয়ে পোঁড়া মশলার ধোঁয়াটা সহ্যই হত না একেবারে। অ্যাজমার সমস্যাটা চরমে গিয়ে উঠত। কিন্তু তার জন্য মিতুর কখনো দুশ্চিন্তা হয় নি, ইনহেলারটা তো সাথেই থাকে সবসময়। একটা চাপ দিয়ে শ্বাসের সাথে ওষুধটা টেনে নিলেই সব ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু এমন বন্ধের মধ্যে ইনহেলারের ভেতরের ওষুধটা গেল শেষ হয়ে। মারুফকে পাঠাবে পাঠাবে করেও মিতু পাঠালো না বাইরে, ভাবল কয়েকদিন পর আবার বাজারে গেলে ফর্দের সাথে ইনহেলারের কথাটাও তুলে দেবে একপাশে। দিন কয়েক কেটে গেল, এদিকে মিতুর শ্বাসের সাথে সাথে সাঁ সাঁ শব্দ হওয়াটাও শুরু হয়ে গেল। এখনি যদি নতুন একটা ইনহেলার এনে পাশে পাশে রাখা না যায় তাহলে বিপদ এই ঘটল বলে! মারুফ কিছু টের পেল না, মিতুও তেমন গুরুত্ব দিল না, তবু সেদিন শুতে গিয়ে মারুফকে একবার বলল,
-বাজারে গেলে একটা ইনহেলার নিয়ে এসো তো, আমার ওটা শেষ হয়ে গেছে।
-তোমার কি সমস্যা হচ্ছে নাকি? নইলে বলছিলাম কালই গিয়ে নিয়ে আসি।
-না হচ্ছে না, তবে মনে হচ্ছে যেন শ্বাস ছোট হয়ে আসছে। তুমি চিন্তা কোরো না, ওতে আমার অভ্যাস আছে। পরের বার বাজারে গেলে তখন আনলেই হবে।
-দেখছি।
মারুফ অবহেলা করল না, মিতুর কথায় ঠিক আশ্বস্ত হতে পারল না। পরের দিনই ইনহেলারের জন্য সে বেরিয়ে গেল। পথে দেখা হল তার বাসার জমিদারের সাথে।
-কই যাচ্ছ মিঞা?
-জ্বি, আমাকে একটু ফার্মেসীতে যেতে হচ্ছে। মিতুর কাল থেকে একটু শ্বাসকষ্ট লাগছে তাই।
কথা শোনামাত্রই জমিদার কিছুটা পিছিয়ে গেল। জেনে শুনেই যেন কথা বাড়ালো না আর, বলল।
-ঠিক আছে যাও, যাও।
মারুফ জমিদারের অবস্থা বুঝে সেদিন হেসেছিল ঠিকই, কিন্তু মনে একটু অস্বস্তিও হল। তবু বেশি কিছু না ভেবে সে ফার্মেসীর দিকে আগালো। দুর্ভাগ্যবশত তাদের এলাকার ফার্মেসীটা সেদিন খোলা পাওয়া গেল না। ফার্মেসীর মালিক করোনায় আক্রান্ত, কাজেই সেটি বন্ধ। এতদূর এসে কাজ না হওয়ায় মারুফ আর আগালো না। মিতু বলেছে দুয়েকদিন ইনহেলার ছাড়া থাকতে তার সমস্যা হবে না, কাল না হয় বাজারে যাওয়ার পথে কোন একটা ফার্মেসী থেকে কিনে নেওয়া যাবে!
মারুফ সেদিন ফিরে গেল। কিন্তু বাসায় ফিরে মিতুর মুখের দিকে তাকিয়ে তার মন পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেল। মিতুর মুখ ভীষণ শুকিয়ে গেছে। তার শরীরটা মনে হয় খারাপ করতে শুরু করেছে। মারুফ বুঝতে পেরেছে যে সে ফিরে এসে আসলে ভুল করেছে, বড় ভুল। তৎক্ষণাৎ সে আরেকবার বেরুতে চাইল কিন্তু মিতু হাত ধরে ফেলল। বাঁধা দিয়ে বলল,
-যাচ্ছ কোথায়?
-মিতু তোমার ইনহেলার এলাকার ফার্মেসীটাতে পাওয়া যায় নি, ভেবেছিলাম কাল বাজার করতে গেলে ওটাও নিয়ে আসব কিন্তু এখন বুঝতে পারছি সে অবহেলাটা করা ঠিক হয় নি, তোমার কষ্ট বাড়ছে,আমি এক্ষুণি গিয়ে অন্য দোকান থেকে নিয়ে আসছি।
-পাও নি! আচ্ছা থাক, পরে যেও। দুপুর হতে বেশি বাকি নেই, দুপুরের খাবারটা খেয়ে একটু বসে তারপর না হয় যেও!
-যেতে হবে যখন এক্ষুণি গিয়ে নিয়ে আসি।
-আহা! দাঁড়াও না, একটু দেরি করে গেলে আমি মরে যাব না, খেয়ে কিছুক্ষণ পর বের হলে কিছুই হবে না।
-এমনভাবে বলছ কেন মিতু! আচ্ছা খেয়ে তারপর যাব।
-হুম, ঠিক আছে। এসে একটু ফ্যানের নিচে বস।
মারুফ বসল, হয়ত একটু অবহেলাই করল। কিন্তু সেদিন সে অবহেলার কত বড়, কত নির্মম মূল্য তাকে দিতে হয়েছিল সেটা মনে করতেই চরম অস্থিরতায় তার বুক চাপড়াতে ইচ্ছে করে। চাপড়াচ্ছে! হ্যাঁ এখনো মিতুর কবরের পাশে বসে মারুফ এলোপাতাড়ি তার বুকটা চাপড়াচ্ছে, পৃথিবীর যত কষ্ট সব যেন সে নিজের বুকে ধারণ করে নিতে চাচ্ছে। খুব জোরে চাপড়াতে চাপড়াতে মারুফের কাশি চলে এল, কাশতে কাশতে একটু ঝুঁকে সে পড়ে গেল, তারপর গা এলিয়ে মিতুর কবরের পাশে মাটিতেই শুয়ে পড়ল। তারপর.... তারপর আবার সে কঠিনতম, যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতির কথা ভাবতে লাগল।
সেদিন একসাথে ভাত খেতে বসে দুজন মাত্র কয়েকটা গ্রাসই মুখে তুলেছিল, অমনি একটা হট্টগোলে দুজনের কান বাজতে লাগল। মনে হচ্ছিল যেন বড় কোন মিছিল দূর থেকে কাছে চলে আসছে। মারুফ উঠে দাঁড়াল, দেখতে হবে এত হৈ-চৈ কিসের। দরজা খুলে সে বেরিয়ে এলো, বেরিয়ে এসে যে ভয়ানক দৃশ্যটি দেখতে পেল সেটি দেখার জন্য সে কোনভাবেই প্রস্তুত ছিল না। এরা করছে টা কি! মারুফের বুঝতে বাকি রইল না যে এই আতঙ্কের দিনে জমিদারকে মিতুর শ্বাসকষ্টের কথাটা বলে সে কত বড় ভুল করেছে। তার আভাস এবার কিছুটা পাচ্ছে। জমিদার কয়েকজন স্থানীয় লোকজন নিয়ে এসে অনেক হৈ-চৈ করে গলির মুখের গেইটটিতে তালা লাগিয়ে দিল। তার পাঁচতলা বিল্ডিংয়ের প্রতিটি তলায় একটি করে গলি আছে, প্রতিটি গলির মুখে একটি করে গেইট আছে, কিন্তু তালাটা তিনি এই চারতলার গেইটে এসেই লাগালেন। রাকিব ছুটে গেল, ছুটে গিয়ে সে গেইটটা ধরতেই সবাই যেন একপ্রকার লাফিয়েই পিছিয়ে গেল। জমিদার বলে উঠল,
-ভয় পাইয়ো না মারুফ মিঞা, আমরা হইলাম সচেতন নাগরিক। ঢাকা থেকে যতক্ষণ টেস্ট করার লোক না আইবো ততক্ষণ তুমি বাইর হইতে পারবা না।
-কিসের টেস্ট! কিসের লোক!
-কেন? তোমার বৌয়ের না শ্বাসকষ্ট! কয়দিন ধরে শ্বাসকষ্ট? এতদিন পরীক্ষা করাও নাই ক্যা?
-নাজমুল সাহেব, আপনি যেরকম ভাবছেন সেরকম কিছুই না, এটা করোনা নয়। মিতুর অ্যাজমার সমস্যা আছে, মাঝেমধ্যেই শ্বাসকষ্ট ওঠে, এটা ওর আগে থেকেই ছিল। এর জন্য ডাক্তার ওকে ইনহেলার দিয়েছে আর সেটার জন্যই আমি ফার্মেসীতে গিয়েছিলাম, পাই নি। আপনি প্লীজ গেইটটা খুলে দেন, আমি গিয়ে নিয়ে আসি।
-ধুর মিঞা রাখো তো। এমন ভাব করছ যেন আমরা তোমারে বন্দি বানাইতেছি। বেশিক্ষণ তো না। কাল সকালে টেস্ট করার লোক আসা পর্যন্ত। এর মধ্যে আমরা কোনো সুযোগ নিতে চাই না। একটা রাত কিছু হইবো না, একটা রাত ঘরে থাকলে কেউ মারা যাইবো না।
রাগের স্বরে মারুফ বলে উঠল,
-যদি হয় সে দায় কি আপনি নেবেন!
-তুমি মিঞা কথা প্যাঁচাও ক্যা? ভাবছিলাম একবার কইলেই তুমি বুঝবা আর অপেক্ষা করবা। কিন্তু তুমি তো উল্টা আমার উপর দিয়া যাইতে চাও। এটা ঠিক না মিঞা, আমি ভালো মানুষ বইলাই বের কইরা না দিয়া টেস্ট করার জন্য অপেক্ষা করতে বলতেছি। আমি হইলাম গিয়া সচেতন নাগরিক, নির্দয় না।
-সচেতন নাগরিক! এর অর্থ বুঝেন আপনি! এমন সময়ে গাদাগাদি লোক নিয়ে এসেছেন, আর নিজেকে দাবি করছেন সচেতন নাগরিক! গেইটটা খুলে দিন, ওষুধটা আনতে না পারলে বড় কোন অঘটন ঘটে যেতে পারে। নাজমুল সাহেব, অনুরোধ করছি।
কথা শুনে নাজমুল সাহেবের কথিত সচেতন জনতা আওয়াজ দিয়ে উঠল, নিশ্চিত না হয়ে কোনভাবেই বের হতে দেওয়া যাবে না। হ্যাঁ এরা সচেতনতার লেভেলধারী, যারা জানেই না সচেতনতা কি! যাদের অনেকের মধ্যেই মাস্ক, গ্লাভস্ পড়ার কিংবা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বালাই নেই। এরা ভাবতেও পারছে না যে এখানে কোনভাবে একজনও যদি সংক্রমিত থাকে তাহলে বাকিদের কি অবস্থা হবে, কতটা ঝুঁকির মধ্যে পড়বে! নাজমুল সাহেব বললেন,
-এসব বলে আমার কাছ থেকে পার পাইবা না মারুফ মিঞা, তোমারে বাইর হইতে দেওন যায় না, নইলে বৌয়ের জন্য ওষুধ আনার নাম কইরা সবাইরে রোগ দিবা।
ঘটনার এ পর্যায়ে মারুফ হতভম্ব। এরা তো কিছুই বুঝতে চাইছে না, কি হবে এখন! মিতুর অবস্থা তো ভালো না, অপেক্ষা করার প্রশ্নই ওঠে না, এই মুহূর্তে অপেক্ষার অর্থ হতে পারে মৃত্যু। না! সেটা কোনভাবেই হতে দেওয়া যায় না। মিতুর প্রকৃত সমস্যাটা মারুফ আরো কয়েক ধাপ তাদের বোঝানোর চেষ্টা করল। কিছুতেই কিছু হল না, বিশ্বাসও করল না, বুঝতেও চাইল না। ক্ষুব্ধ হয়ে মারুফ তখন গেইট ঝাঁকাতে লাগল, আর ক্ষেপে গিয়ে জমিদার বাসা ছাড়াবার হুমকি ধমকি দিয়ে দলবল নিয়ে চলে গেল, গেইটটা তবু খুলে দিল না। আশেপাশের লোকজন কেউ বেরই হল না, প্রতিবাদ তো দূরের কথা। তারা বোধহয় ভয়ে আছে যদি করোনাই হয়!
ঘটনার আকস্মিকতায় মারুফ ভীষণ আতঙ্কিত, সে ছুটে গিয়ে বাসার ভেতর ঢুকল। মিতু খাবারের থালাটা সরিয়ে রেখে মুখ নিচু করে বসে আছে, ভীষণ মৌন হয়ে। মারুফ তার কাছে গিয়ে বসে পড়ল, অসহায় অপরাধীর মতো মিতুর দিকে তাকিয়ে বলল,
-মিতু ওরা আমাদের আটকে দিয়েছে।
মিতু সঙ্গে সঙ্গে শব্দ করে কেঁদে উঠল, মারুফকে ভীষণ করে জড়িয়ে ধরল, তারপর গোঙাতে গোঙাতে বলল,
-আমার খুব কষ্ট হচ্ছে মারুফ, শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে।
মারুফ হঠাৎ মেয়েদের মতো গোঙিয়ে উঠল। ঐ অবুঝ, মূর্খ মানুষগুলোকে এখন কে বোঝাবে! যে কাজটি করে, যে জেদ ধরে তারা নিজেদের সচেতন প্রমাণ করার চেষ্টা করছে সে জেদ, সে কাজ কোন প্রাণ বাঁচাবে না বরং একজনকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে। দিলও বটে। সেদিন সন্ধ্যার পর মীরার শ্বাসকষ্টটা প্রচন্ডরকম বাড়ল, মারুফের সামর্থ্য শুধু ছোটাছুটি, গেইট ঝাঁকাঝাঁকি, মাঝেমধ্যে চিল্লাচিল্লি এসবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল। মীরার জন্য এর চেয়ে বেশি কিছু করা গেল না, কেউ এসে একবার খোঁজ নিয়েও গেল না। মারুফের একবারের জন্য মনে হল নিজের বুক থেকে ফুসফুসটা খুলে সে মীরার বুকে লাগিয়ে দেয়, কিন্তু সেটা সম্ভব হল না। সম্ভব হলে বোধহয় সে সেটাই করত, নিজের প্রাণ যাওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও। এ দৃশ্য চেয়ে থাকার মতো নয়, এ দৃশ্য সহ্য করার মতো নয়। মারুফ কি করবে বুঝতে পারছিল না, কিছু করারও হয়ত ছিল না, তার চিন্তা-ভাবনা সব এলোমেলো হয়ে এল। একে-ওকে, অনেককেই ফোন করল, কিন্তু কাছাকাছি কেউ না থাকায় তৎক্ষণাৎ কোন সাহায্য সে পেল না, অপেক্ষায় রইল কখন কেউ একজন ইনহেলার নিয়ে এসে তার হাতে দেবে, কখন তার ভেতরের জীবন বাঁচানোর ওষুধ মীরার ফুসফুসে ঢুকবে, কখন মীরার বুকের চাপটা আবার বুকেই মিলিয়ে যাবে। কাঁদো কাঁদো গলায় মারুফ মীরাকে সাহস দিল,
-মীরা একটু অপেক্ষা কর, বাবাকে ফোন দিয়েছি। উনি আবিরকে নিয়ে আসছেন, যত রাতই হোক তিনি একটা ইনহেলার নিয়ে চলে আসবেন, একটু অপেক্ষা কর।
মীরা কোন সাড়া দিতে পারল না, তার হাত-পা ছাড়া। মারুফ আরেকবার গোঙিয়ে কেঁদে উঠল,
-মীরা, এই মীরা, তুমি কিছু বলছ না কেন!
মীরা তবু কিছু বলছে না, বলার শক্তিটাই যে আর থাকছে না। পুরো শক্তি তার ঐ শ্বাস নিতেই চলে যাচ্ছে, তবু যদি শ্বাসটা পুরোপুরি নেওয়া যেত! তাও নেওয়া যাচ্ছে না।
মারুফ ছুটে আরেকবার গেইটের কাছে গেল, কিছুক্ষণ চিৎকার করে সাহায্য চাইল, তারপর শেষটায় কোন ফল না পেয়ে গেইট ঝেঁকে দিয়ে চলে এল। মারুফ আবার বসে মীরার মাথাটা কোলে নিতেই মীরা একবারের জন্য কেমন কেঁপে উঠল। দুজন সে অবস্থাতেই ঘন্টাকয়েক বসে রইল, তারপর মারুফ লক্ষ করল মীরার শ্বাস আর অত জোরে চলছে না, বুকের চাপটা আর তেমন বোঝা যাচ্ছে না, গায়ের তাপটা আর স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না, ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে। শ্বাস চলছে খুব ধীরে, এতই ধীরে যে খুব ভালভাবে খেয়াল না করলে বুঝাও যাচ্ছে না, কতক্ষণ পর পর একটা করে। মারুফ বেশ শান্ত স্বরে ডাকল,
-মীরা!
কোন সাড়া এল না। আবার বলল,
-তুমি কেন আমার এক কথায় সেদিন চলে এসেছিলে?
মীরা একবার ‘উঁ!’ জাতীয় শব্দ করল, আর কিছুই শোনা গেল না। মারুফ বিলাপ করতে থাকল,
-আল্লাহরে! তোমাকে বিয়ের জন্য ফোন করার আগে এক্সিডেন্টে আমার মৃত্যু হল না কেন? সেদিন আমার এক কথায় তুমি চলে এসেছিলে কেন?
এভাবে আরো কিছুক্ষণ কাটল। তারপর দেখা গেল মীরার পুরো শরীরটা বারবার কেঁপে কেঁপে উঠছে। হাত-পা টানটান হয়ে গেছে, পা দুটো একটি আরেকটির সাথে জড়াজড়ি খাচ্ছে, একেকটি শ্বাস নিতে গিয়ে মীরা একেকবার মাথা উঁচিয়ে কেঁপে উঠছে। মাথাটা মারুফের কোলে থাকছে না। এ দৃশ্য দেখে মারুফ পাগলপ্রায় হয়ে গেল। সে শুধু ‘মীরা’ ‘মীরা’ বলে চিৎকার করেই গেল। মীরা এভাবে কিছুক্ষণ কেঁপে কেঁপে উঠার পর হঠাৎ ধপাস করেই যেন পড়ে গেল। তারপর আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না, নীরবেই পড়ে রইল, একেবারে নীরব, নিস্তব্ধ, নিথর একটি দেহ। মারুফের বুঝতে কিছু বাকি রইল না, একদিন মারুফের এক কথায় যে মেয়েটি নির্দ্বিধায় ছুটে চলে এসেছিল তার পাশে দাঁড়ানোর জন্য, তার জীবনসঙ্গী হওয়ার জন্য, তার হাজার ডাকেও সে আর সামান্য সাড়াটুকুও দেবে না। অনেক সাহস দিয়েও মীরাকে সে ধরে রাখতে পারল না, মীরা মারা গেল। ছোট ছোট ভুল, ছোট ছোট অবহেলা, কিছু মানুষের মূর্খতা কত সহজেই না কেড়ে নিল মীরার প্রাণ! মারুফ মীরার নিস্তেজ মাথাটিকে কোলে তুলে নিল, তারপর ঠাঁই বসে রইল পাথরের মতো।
ঘন্টাখানেক পর গেইট খোলার শব্দ হল। বাবা এসেছে, মারুফের বাবা, হাতে ইনহেলার, বৌমার জীবন বাঁচানোর ওষুধ। কিন্তু জীবনই যে নেই, বাঁচাবে কী! খোলা দরজায় ঢুকে দেখা যায় একটি মানুষ পাথরের মতো স্তব্ধ, চরম বিস্ময় নিয়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে, তার কোলে নিস্তেজ একটি শরীর হাত-পা ছেড়ে শুয়ে আছে। মারুফের বাবা রহমত আলীর বুক ফাঁটা কান্না বেরিয়ে এল। মারুফ তখনো পাথর, তেমনি নিস্তেজ যেন তার প্রাণ থাকা শরীর প্রাণহীন শরীরের মানুষটির সাথে এক হয়ে মিশে থাকতে চায়।
মারুফ আর কিছু ভাবতে পারল না, অজ্ঞান হয়ে পড়ল। এটি তার নতুন একটি সমস্যা, হঠাৎ হঠাৎই অজ্ঞান হয়ে যায়, তারপর হুট করে জ্ঞান ফিরে আসলে আবুল-তাবোল বকে। এ সমস্যাটা প্রথমবারের মতো হয়েছিল সেদিন, যখন মিতুকে নিয়ে যাওয়ার জন্য লোক এলো। মারুফ মাথা ঘুরে পড়ে গেল। তার বাবা ছেলেকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মিতুর লাশ নিতে কেউ বাঁধা দিল না, বাঁধা দেওয়ার মতো অবস্থাও তখন ছিল না। যে সন্দেহ, যে আতঙ্ক সবার মধ্যে সৃষ্টি হয়ে গেছিল তার শেষ না দেখে কেউ ছাড়ত না। একসময় রিপোর্ট এল, সেটা এল নাজমুল সাহেবের ঠিকানায়। তিনি বোধহয় একটু বাড়িয়েই বলেছিলেন, পরীক্ষার ফল নেগেটিভ শুনে খুব বিস্মিত হওয়ার ভান করে বললেন,
-এটা কেমনে সম্ভব! মেয়ের তো কয়েকদিন ধরে জ্বর, গলাব্যথা সবই ছিল। ওর স্বামী মারুফ কয়বার যে আমার কাছে জ্বর-সর্দির ট্যাবলেট নিতে আইছিল!
রিপোর্ট নিয়ে আসা লোকটি বলল,
-তাহলে তো আপনারও টেস্ট করা উচিত।
-হ করমু নে।
নাজমুল সাহেবেরও টেস্ট করা হল, সাথে তার সঙ্গে সেদিন দলে থাকা কয়েকজন লোকজনের। দেখা গেল প্রায় সবার শরীরেই করোনা হানা দিয়েছে, সবার করোনা পজিটিভ। তাদের সচেতনতার ফল তারা পেল। কিন্তু মারুফ যা হারাল তার কথা সে ভুলতেও পারছে না, মেনে নিতেও পারছে না, কোনোভাবেই তা আর সহ্য করা যাচ্ছে না। সে ঠিক করল সে মারা যাবে, স্বেচ্ছায়। তবে মারা যেতে যেতেও যত পারে মানুষের সেবা করে যাবে। ভাবনা অনুযায়ী সে করোনা চিকিৎসার জন্য নিয়োজিত কিছু স্বেচ্ছাসেবকের দলে গিয়ে ভিড়ল। খামখেয়ালি, ক্ষত-বিধ্বস্ত মন নিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করল করোনা রোগীদের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার। কিন্তু সে সেবা বেশিদিন আগাল না, তাকেও শেষমেষ করোনা পজিটিভ পাওয়া গেল। তাকে একঘরে করে দেয়া হল, মারুফ একা থাকতে শুরু করল, কিন্তু কোন স্বাস্থ্যবিধি, ডাক্তারের কোন পরামর্শ সে মানল না। তার যে মরে যাওয়াই ইচ্ছা। তার শরীরের অবস্থা খুব খারাপের দিকে গেল, বেঁচে যাওয়াটা এখন যেন একটা দুরাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই মারুফ আজ শেষবারের মতো মিতুর কবর দেখতে এসেছে, দেখতে এসে সেখানেই হুশ হারিয়ে পড়ে আছে। এ হুশ আর ফিরবে না, এ শরীরও আর নড়বে না, তার বুক মিতুর জন্য আফসোসে আফসোসে আর অস্থির হয়ে উঠবে না। ব্রেনস্ট্রোকে সে মারা গেছে, মিতুর মতো সেও পরপারে চলে গেছে, সেখানে কোন শুভক্ষণে হয়ত মারুফ-মিতুর ফের মিলন হবে! সেখানে থাকবে না কোন অজ্ঞতা, কোন মূর্খতা। যা থাকবে তা শুধু সুখ, শান্তি আর পরিপূর্ণতা, প্রাপ্তির পরিপূর্ণতা।
ছায়ার দিকে তাকিয়ে কায়া!
ছায়ার দিকে তাকিয়ে কায়া!
হাসনাত আসিফ কুশল
১.
এরপর আর কখনো দেখে নি তাকে কায়া। সেই যে একবার ধমকে বিদায় করে দিয়েছিলো তাকে আর আজ এই বৃষ্টিভেজা বিকেলবেলায় জবুথবু হয়ে সে তার বাসার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটু সন্দেহ হলো তার। হঠাৎ পুরনো কোনো ফাইলে ছেলেবেলায় লেখা কোনো কবিতা পেলে যেমন অনুভূতি সঞ্চারিত হয় সে খেয়াল করলো অবিকল অনুভূতি সে অনুভব করছে। এক মিনিট সে এভাবেই তার দিকে তাকিয়ে থাকলো। এক মিনিট পর কায়ার মনের বিপ্লব যেন শিহরণ জাগালো। আপাত অপরিচিত লোকটি বললো, ভাবছো তোমার ধমকে আমি কিছু মনে করেছি কিনা। কায়া কিছু মনে না করে দরজা খুলে দিলো। কায়া তার শয্যাকক্ষে চলে গেল। আপাত অপরিচিত লোকটি এসে বৈঠকখানায় বসে থাকলো। টিভিটা অনবরত চলছে। দেখার কেউ নেই আবার বন্ধ করার কেউও নেই। লোকটি সোফায় একঘেঁয়ে বসে থাকলো। কায়াও আসছে না। অবশ্য লোকটির মনের মধ্যে কোথাও কায়ার অস্তিত্ব আছে কিনা সন্দেহ আছে। কিন্তু তাহলে কেন এসেছে সে ? সোফায় যেখানে সে বসে আছে তার সামনেই একটা আয়না। আয়নায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তাকে। আয়নায় তার প্রতিবিম্ব বলে উঠলো, কেন এসেছো এখানে ? ভালোবাসো কায়াকে ? সে মনে মনে উত্তর দিলো, না তো। তখন তার প্রতিবিম্ব বলে উঠলো, তাহলে কেন এসেছো ? সে বললো, এসেছি...কারণ, উম। উম। আসলে কারণ সে জানে না। সেই যে ২০০৯ সালে অফিসার্স ক্লাবে কায়ার সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল কি একটা কারণে। এখন পর্যন্ত সে ভুলতে পারছে না। অথচ কায়া বোধহয় তাকে বেমালুম ভুলে বসে আছে। মনে মনেই বললো সে। প্রতিবিম্ব তখন জানালো, কায়া তোমাকে ভোলে নি। শয্যাকক্ষে গিয়ে দেখ ও কি মনে করে কাঁদছে। এবার লোকটি অবাক হলো। এটা কি কোনো দিবাস্বপ্ন ? একটু ইতঃস্তত করলো। আড়ষ্টভাব কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করলো সে। পারলো না। এভাবে দরজার সামনে গিয়ে টোকা দিলো। এরপর আরও অবাক হলো যখন সে কান্নার শব্দ শুনতে পেল। সে ভাবলো, যাবো কি যাবো না। শয্যাকক্ষের চৌকাঠ থেকে দুই পা এগোতেই কায়া তার দিকে তাকালো। তারপর কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো, আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। তুমি ক্ষমা করো আমাকে। সে বললো, আচ্ছা ঠিক আছে। এরপর সে বললো, তোমার জন্য আমি দশ বছর ধরে অপেক্ষা করছি। কায়া কি মনে করে আলমারির দিকে গেল। কি যেন খুঁজছে ও। কি খুঁজতে পারে ও। প্রশ্ন আসলো লোকটির মনে।
কায়া আবার খালি হাতেই ফিরে আসলো। লোকটি বললো, কি খুঁজছিলে তুমি ? কায়া কিছুই বললো না। তারপর লোকটি বললো, তোমার শয্যাকক্ষে আসার জন্য দুঃখিত। আমাকে ক্ষমা করো। আমি লজ্জিত। কায়া তাকালো একবার তার দিকে। তারপর বললো, তোমার যেতে ইচ্ছে করলে চলে যাও। আমি এখানেই অপেক্ষা করবো। সে বৈঠকখানায় গেল। টিভি চলছে। সে টিভির রিমোট হাতে নিলো। টিভির দিকে মনোযোগ দিতে চেষ্টা করলো। নাহ। টিভির দিকে মন যায় না। একটু পর কায়া আসলো তার কাছে। বসলো তার সামনে। তারপর বললো, আগামীকাল তার বিয়ে। পাত্রপক্ষ তড়িঘড়ি করছে বিয়ের জন্য। পাত্র নাকি লন্ডনে চলে যাবে। সে বড় মাপের আর্টিস্ট। গান করে। কিন্তু এই বিয়েতে সে রাজি না। ফ্যামিলি তাকে জোর করে বিয়ে দিচ্ছে। লোকটি সব শুনলো। তারপর তাকে বললো, দেখ আমার এখানে কি করার আছে ? কায়া তাকে বললো, তুমি আমাকে বিয়ে করে ফেল। লোকটি এবার বিব্রত হলো। বললো, দুঃখিত বুঝতে পারি নি। আবার বলো। কায়া বললো, তুমি আমাকে বিয়ে করে ফেল। লোকটি বললো, নাহ। এই মুহূর্তে আমার পক্ষে বিয়ে করা পসিবল না। কায়া এবার আর কোনো কথা বললো না। লোকটিও চুপ। অনেকক্ষণ পর কায়া বললো, আমার কোনো কিছু ভালো লাগছে না। আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম। আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করা প্রয়োজন। লোকটি বললো, আমি তো তোমাকে ক্ষমা করেই দিয়েছি। কায়া বললো, না আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। অন্তত আমাকে বাঁচানোর জন্য বিয়েটা করো। লোকটি বললো, ভেবে দেখছি। তারপর উঠে দাঁড়ালো লোকটি। লোকটি দেখলো, এখানে থাকলে সে নিজেও পাগল হয়ে যাবে। তারপর তার জন্য কত অর্থ খরচ হবে পরিবারের। দ্রুত প্রস্থান করলো সে। কায়াও ছুটলো বারান্দার দিকে। বারান্দায় এসে ডাকছে তাকে। কায়া কিছুতেই তাকে হাতছাড়া করতে চায় না। কিন্তু লোকটি এমন দ্রুত প্রস্থান করলো কায়া তার নাগাল পেল না। কিন্তু কায়ার তাকে প্রয়োজন খুব। কারণ লোকটি যে কায়ার খুব ভালো বন্ধু আয়ুশ। কায়া ওকে ভালোভাবেই চেনে। কিন্তু দশ বছর আগের একটা ভুল সিদ্ধান্ত এখন কুরে কুরে খাচ্ছে তাকে। এখন তার মনোজগত ভেঙে পড়েছে। সে বারান্দায় আরামকেদারায় বসে পড়লো। একটু কিছুক্ষণ বসে থাকলো। তার পথের দিকে সে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে আরম্ভ করলো। একটি সিদ্ধান্তে সে অটল থাকলোই। তাকে ওর সাথেই বিয়েটা করতে হবে। যেমন করেই হোক।
২.
স্বভাবত কায়া কখনো হুটহাট সিদ্ধান্ত না নিলেও এই প্রথমবার সে এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলো। সে আয়ুশকেই বিয়ে করবে। কিন্তু বাসায় বলতে পারছে না। কি করবে ভেবে পেল না। এমন সময় সে ভাবলো সিধায়াকে ফোন করলে হয়তো লাভ হবে। সিধায়া আয়ুশের এক বন্ধু। ওর সঙ্গে আয়ুশের সূত্রেই পরিচয়। আয়ুশের সঙ্গে তার পরিচয় ২০০২ সালে নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় থেকে। এরপর একসাথে ওরা কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি পাস করেছে। ইউনিভার্সিটিতে পরিচয় সিধায়ার সঙ্গে। তখন থেকেই সিধায়ার সঙ্গে খাতির তার। সিধায়াকেই তাই সে বেছে নিলো আয়ুশকে বিয়ের ব্যাপারে বলার জন্য। কায়ার সঙ্গে ওই ভাবে আয়ুশের খাতির না থাকলেও সিধায়ার সঙ্গে গলায় গলায় ভাব।
‘সিধায়া ?
‘হ্যাঁ বল।
‘আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।
‘কি কাজ ?
‘আয়ুশের সঙ্গে তোর সম্পর্ক কি এখনো আছে ?
‘হ্যাঁ। কেন ?
‘আমি ওকে বিয়ে করতে চাই। সেদিন বাসায় এসেছিলো। আমি ওইদিন বলেছিলাম। তারপর কি মনে করে ও আমার সঙ্গে কথা শেষ না করে পালিয়ে গেল।
‘পালিয়ে যাবে কেন ? তুই কি ওকে সামনাসামনি প্রপজ করেছিস ?
‘হ্যাঁ।
‘আরে, ও তো ব্রহ্মচর্য নিয়েছে। ও কখনো বিয়ে করবে না বলে ঠিক করেছে। (হুট করে সিধায়া মিথ্যা কথা বলে ফেলল।)
‘বলিস কি ?
‘হ্যাঁ।
‘আচ্ছা তাহলে...।
ফোন রেখে দেয়।
আসলে সিধায়া ওকে ভালোবাসে। কিন্তু বলতে পারেনি। একারণেই কায়াকে এ কথা জানাতে চায় নি। কিন্তু সে ভাবলো আয়ুশকে এ কথা বলা খুব জরুরি। না হলে আয়ুশকে অন্য কেউ বিয়ে করে ফেলবে। আজ কিংবা কালÑবিয়ের কথা বলবেই।
৩
কিন্তু আয়ুশ যে কোথায় গেছে তা কেউ বলতেই পারছে না। আয়ুশ ওই দিন থেকে তার বাড়ির লোক থেকে লাপাত্তা। কেউ জানে না কোথায় গেছে সে। সিধায়া ফেসবুকে নক করলে দেখলো সে অনলাইনে নেই। অপেক্ষা করতে থাকে সিধায়া। আবার কায়াও বটে। কারণ কায়া জানে আয়ুশ কখনো এমন কোনো ব্রত নিতে পারে না।
আয়ুশের বাবা জিডি করলো। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। পুলিশের সন্দেহ হলো কোনো জঙ্গিসংগঠনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়লো কিনা। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ওর বাবা বলে উঠলো, ও কখনো ওদিকে যাবে না। ওকে আমরা চিনি।
তবে কায়া ভীষণ মুষড়ে পড়লো। বাসায় বিয়ে। তাকে লাল পাড়ের শাড়ি পরে বসে থাকতে হচ্ছে। শুনেছে যার সাথে ওর বিয়ে হচ্ছে তার নাকি একটা গিটার ও একটা ভায়োলিন আছে। মোহরানা হিসেবে সে ওকে ওই গিটার ও ভায়োলিনটাই দেবে। কিন্তু গিটার-ভায়োলিন কোনোটাই ওর পছন্দ না। এর মধ্যে একটা কা- হলো। আয়ুশ কোত্থেকে এসে কোনো মতে কায়ার ঘরে ওকে একা পেয়ে বললো, আমি বুঝতে পেরেছি তোমার ওই ছেলের সঙ্গে বিয়ের কোনো ইচ্ছে নেই। কিন্তু আমি তখন তোমার কথায় রাজি ছিলাম না। এখন রাজি আমি। তোমার বাবাকে আমি বলছি। কায়া বললো, তুমি না ব্রহ্মচর্য নিচ্ছো ? আয়ুশ তখন বললো, কে বলেছে এসব কথা। কায়া বললো, সিধায়া বলেছে। আয়ুশ বললো, ও মিথ্যে বলেছে। কায়া শুনে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লো। কিন্তু কায়ার মামী এই মুহূর্তে এসে দেখে ফেললেন ওদেরকে। তারপর সে বললেন, তোমরা এখানে কেন ? আয়ুশ তখন বললো, কায়ার সঙ্গে যার বিয়ে হচ্ছে তাকে কায়ার বিয়ের ইচ্ছে নেই। মামী তখন বললেন, সেটা আমাদের ব্যাপার। কিরে কায়া সত্যিই কি তোর ইচ্ছে নেই ? কায়া বললো না কিছুই। মামী এবার ধরতে পারলো কায়া কি চায়। তারপর মামী বললেন, এ ছাড়া কিই বা করার আছে ? কিন্তু ছেলেটা তো ভালোই। পড়াশুনায় উচ্চশিক্ষিত, গানও পারে। তাহলে ?
কায়া কিছুই বললো না।
কারণ সে জানে এসবকিছুই স্বপ্ন তার। আর তাই আয়ুশ তার জীবনে এসেছে এটাই তার জন্য বড় কথা। আয়ুশের ছায়ার দিকে তাই তাকিয়ে সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।
পদাবলি
খাটুনি
শরীফ সাথী
তোমার সংসারে কত খাটুনি খাটলাম
ঘুম থেকে উঠে কাঁথা বালিশ গুছিয়ে
ঘর উঠোন ঝাড়–, থালা বাসন মাজা
রান্নাবান্না, ছেলেমেয়েদের একের পর হুকুম
ত্রুটি হলে তোমার চোখ রাঙানো
বুঝলেনা আমার, সারাদিন বিরাম নেই
এত খাটুনি তবুও একবার ও নাম হলো না।
বনলতা
মাসুদ পারভেজ
এই তো ঘুরে আসলাম বনলতা হয়েই
বনলতা এখনো জীবনানন্দময়ী--
চিরায়ত চিরকাল
জীবনের কথা কয়
কিন্তু ‘জীবনানন্দ দাশ’-এর কবিতার মতোই
বিরহবিধুর বাঁশি বাজাচ্ছ এ হৃদয়!
আমিও একদিন ঝরে যাব বনলতা আক্ষেপ বুকে লয়ে-
হৃদয়ের জমাকৃত শিশিরজল
রাঙাবে ঘাস- পথ-
আমি ধুলো হয়ে মিশে রব এ-ই বাংলায়!
আহা মিটিবে না মিটিবে না
আর- বনলতা- তোমার দেখার সাধ!
বিভাজন
কামাল আহমেদ
প্রিয়, মিথ্যে স্বপন করিনা বপন,
কারো খ্যাতি-চন্দন করিনা মোচন।
দেশ-মাতা-মাটি যত পরিপাটি,
স্বপনের হাঁটাহাটি রাখি তত খাঁটি।
আপনারে তাই ছোট ভাবি ভাই,
স্বপন সাজাই, ঘাস পথে যাই,
গালিচাতে হাঁটিনা ভাবি তা বারণ।
পথে পথে যার গালিচা সোনার ,
অধম কি আর পথ মাড়ে তার?
তারই সুখ-গান করি বিরচন।
তুমি-আমি-ওরা সুখে-দুঃখে জোড়া,
এক ভবে মোরা এক মাটি-গড়া।
তবু কেন প্রিয়জন এতো বিভাজন?
শব্দমালা : শোভন মণ্ডল
সিঁড়ি
এইমাত্র একটা সিঁড়ি দেখতে পেলাম
সুউচ্চ, ঘোরানো
তুমি দাঁড়িয়ে আছো আকাশের কাছে
সিঁড়ির শেষ প্রান্তে
ধাপে ধাপে ওঠার সময় মনে হলো
মাধ্যাকর্ষণ নয়
তোমার টানই বেশি
সর্বনাশা
ছুঁড়ে দিয়েছি গোপন চিঠি
পুরনো দাগ, ক্ষত
আর যা-কিছু তোমারই স্পর্শ
সর্বনাশা...
শুধু সহ্য করেছি আজও
এই যে আমার প্রতিটি স্বপ্নে
তোমার অনায়াস
যাওয়া-আসা
স্বপ্নের মর্মধ্বনি শুনতে পাই
স্বপ্নের রঙ কি ধূসর?
জানা নেই।
ভাঙা পাঁচিলের গায়ে হেলান দিয়ে আছে বাতিল সাইকেল
একটা ফেলে আসা ভাবনার গল্প শোনায়
সেখানেও স্বপ্নের মর্মধ্বনি শুনতে পাই
অচেনা লাগে।
কোন কোন দিন ঘুমের মধ্যে আলোর রেখা দেখি
চুলের মতো, ভীষণ তীক্ষ্ণ
অন্ধকারেও জ্বলে ওঠে তুষের আগুন
সেঁকা হয় বালিশ
নরম ঘামে
সে সব দিনে মাটিতে নেমে আসে ঘোরানো চাঁদ
আর বহুদিন পর এক বাতিল স্টেশনে অলৌকিক ট্রেন এসে থামে
আহত পতাকার কান্না
আহত পতাকার কান্না
মুহাম্মাদ মাসুদ
কান্নার শব্দে থেমে গেলাম। বোবা কান্নার মতো। শব্দ যেন ভিতর থেকে বের হতেই চা”েছ না। ঠিক যেন মোমবাতিতে আগুন জ্বালালে কোন ধোঁয়া আসে না। শুধু নিভু নিভু করে আগুন জ্বলতেই থাকে। মোম গলে যেমন মোমবাতি চুইয়ে চুইয়ে পরে ঠিক তেমনি চোখের অশ্রু নামক রক্তগুলো গাল বেয়ে চুইয়ে চুইয়ে পরছে। বারবার গামছা দিয়ে চোখের রক্তগুলো মুছলেও আবার এক নিমেষেই পূরণ হয়ে যা”েছ।
পুরনো একটি ব্যাগ। ধুলাবালি, মাটি আর এটাসেটা লেগে অন্যরকম একটা রুপ নিয়েছে ব্যাগটি। একটা বোতল। পানির বোতলই হবে। মনে হচ্ছিল অনেকদিন ধরে বোতলটি ব্যবহার করলেও কোনরকম ঘষামাজা বা ধোয়া হয়নি। আর্সেনিকের কারনে হয়তো বোতলটা হলুদে ভরে গেছে। তবুও যেন বোতলটিই নিত্য সঙ্গী।
সাদা একটি চাদর। আসলে চাদরকে চাদর বলে সম্বোধন করা ঠিক হবে না। কেননা, চাদরের গায়ে লাল রঙের অনেক লেখা, কালো রঙের অনেক শোকাহত স্মৃতিচারণ, সবুজ রঙে দেশের কথায় ভরে গেছে চাদরটি। তাছাড়া, চাদরটি এক নাগাড়ে শরীরে দেওয়ায় ময়লায় অন্য রকম একটি ছবিতে পরিপূর্ণ হয়েছে। তবে লেখাগুলো এখনো ফুটে আছে। লাল রঙের লেখাটি ঠিক রক্তের মতো লাগছে। মনে হচ্ছিল দুই একদিন আগে আঁকা হয়েছে। চাদরে নানান রকমের ইতিহাসের চিহ্ন। ধীরে ধীরে আমার মনে প্রচন্ড আগ্রহ হচ্ছিল প্রকৃত ঘটনাটি জানার। সেজন্য একটি ট্রেন মিস করেও বসেছিলাম।
হাতে কিছু পাথর ছিলো। একটু দূরে বসে থাকার কারণে বুঝতে পারছিলাম না। একটি সিগারেট জ্বালিয়ে পাশে গিয়ে দাড়ালাম। কখনও লাল রঙের পাথরের টুকরো দিয়ে লিখেই আবার পরক্ষণেই মুছে ফেলছে। আবার কখনও কালো রঙের পাথরের টুকরো দিয়ে লিখেই আবার পরক্ষণেই মুছে ফেলছে। আমার কাছে সবকিছুই গন্ডগোল লাগছিলো। তবে, মুছে ফেলা লেখাগুলো আমাকে খুব নাড়িয়ে দিয়েছে। বাম হাতে থাকা কাপড়ের টুকরোটি মুছে মুছে অনেক ক্ষয় করে ফেলেছে। মনে হ”িছল কাজটি অনেকক্ষণ ধরেই একনাগাড়ে করছিলো।
হাতে মুকুট বিড়ি। ব্যাগের ভেতর কি যেন খুঁজছিল? ব্যাগের মধ্যে যা কিছু ছিলো তন্নতন্ন করে খুঁজেও পা”িছলো না। পকেটের ভিতর হাত দিয়েও যখন পেলেন না তখন আর কি করা? বিড়িটা আবার রেখে দিলেন।। কিন্তু ততক্ষণে বেশ নেশা হয়ে গেছে। কেমন যেন একটা অসস্তি অনুভব করছিল। প্রথমে নেশাগ্রস্ত মনে হচ্ছিল। কিন্তু না। সেরকম কিছু না। একটু পরেই আবার আগের মতো...।
সিগারেটের আগুন দেখেই মুচকি হেসে উঠলো। যেন জীবন জীবদ্দশায় কিছুটা দম ফিরে পেয়েছে নিশ্বাস
নেওয়ার মতো। ততক্ষণে পকেটে রাখা বিড়িটা বের করেছে। বুঝে উঠতে দেরি হলনা আমার তখন.....। তবে এরকম মলিন হাসি অনেকদিন দেখিনি। হয়তো আবার দেখতে পাবো কিনা সেটাও জানিনা। মনে হয় পৃথিবীতে যারা অল্প কিছু নিয়ে সুখে থাকার চেষ্টা করে শুধুমাত্র তাদের মধ্যে এই হাসিটা পাওয়া যায়।
বাম হাতে বিড়ি, ডান হাত দিয়ে সিগারেটের আগুনটা নিয়ে ধরাবে এমন সময় কেউ একজন এসে সিগারেটের উপর পা দিয়ে সামনের দিকে হাটতে থাকে। রেলস্টেশনতো অনেক মানুষের ভিড়।
আকাশে মেঘ জমালে যেমন পৃথিবীটা স্তব্ধ ও অন্ধকার হয়ে যায় ঠিক তেমনি এমন মুচকি হাসি মুখ নিমেষেই নিশ্চুপ হয়ে গেল। দুয়েক মিনিট শুধু আগুনের দিকে চেয়ে রইলেন। আর জোরে জোরে নিশ্বাস ছাড়তে লাগলেন।
গ্যাস লাইট। চোখের সামনে ধরতেই আবার পুনরায় সেই হাসি। খুবই ভালো লাগছিলো এরকম হাসি দেখে। সময়টা যদি ফ্রেমে বন্দী করা যেতো তাহলে আরও বেশি আনন্দমুখর হতো। আমার হাত থেকে গ্যাস লাইট নিয়েই বিড়ি ধরালো।
বিড়ি টানা শেষ। এতো তারাতাড়ি বিড়ি টেনে শেষ করতে এই প্রথম দেখলাম। ক্ষুদার্ত হাতির সামনে যেমন হালকা কিছু খাবার খেতে দেওয়া। কয়েকটি ছবি তুলে রেখেছিলাম। কিন্তু মোবাইল নষ্ট হওয়ার কারণে সব কিছু ডিলিট হয়ে গেছে।
এবার একটু উঠে দাঁড়ালো। খুব সহজেই যে উঠতে পারলো তেমন কিন্তু নয়। লোহার খুঁটি ধরে ধরে উঠতেই যেন মিনিট দুয়েক লেগে গেল। মনে হ”িছল অনেকসময় ধরে বসে থাকার কারণে হাত-পা গুলো জ্যামে পরে গেছে।
কাকা ধরবো?
কথাটা শুনে কেমন যেন একটু ইতস্তা বোধ করলো। ডান হাত নাড়িয়ে ইশারায় বললো না না। উঠতে গিয়ে হঠাৎ টোলে পরে যাওয়ার মতো হওয়ায় আমি গিয়ে ধরে ফেলি। তখন অবশ্য কাঁধে হাত রেখে দাঁড়ালেন। আমি আর কিছু বলিনি।
বেশকিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকার পরে আবার বসে পরলেন। এইবার মনের মধ্যে কেমন যেন একটা কৌতুহল এসে বারবার ডেকে যাচ্ছে।
কোনরকম সংকোচ না করেই বললাম, কাকা কিছু খাবেন?
কোন উত্তর পেলাম না। ভাবলাম হয়তো শুনতে পায়নি।
পূনরায় বললাম, কাকা কিছু খাবেন?
এবারও কোন সাড়াশব্দ নেই। মনের মধ্যে একটু রাগ হলো।
তারপরও শেষবারের মতো বললাম, কাকা কিছু খাবেন?
এইবার বলার আগেই মাথা নাড়িয়ে দিলো।
আমি আর দেরি না করে হুট করে পাশের দোকান থেকে রুটি, কলা আর কেক পানি নিয়ে হাজির।
কাকা খাচ্ছে। আর আমি বসে শুধু দেখছি।
কাকার খাওয়ার তালে তালে জিগ্যেস করলাম, ‘কাকা কোথায় যাবেন?’
কিন্তু কাকা কিছুই না বলার কারণে বুঝতে পারলাম এমনিতেই কথা বলে না তারপর আবার খাচ্ছে।
হঠাৎ চোখ দুটো কেমন যেন বড় বড় করে তাকালেন। আমিও বেশ ভয় পেয়ে গেলাম। কি যেন বলতে চাচ্ছে? কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না। তবে, মনে হচ্ছিল কিছু একটা হয়েছে। মাটিতে লুটে পরতেই বুঝতে আর দেরি হলো না কি হয়েছে? পাশে রাখা পানির বোতল তারাতাড়ি খুলে মুখে দেওয়ায় স্বস্তি ফিরলে একগাল হেঁসে বলল, ‘বাবা তুমি আমার জীবনটা পূনরায় বাচিয়ে দিলে।’
তালা দেওয়া মুখের কুলুপ যেন এবার খুলে গেল। লটারির পুরুষ্কারের মতো। সুযোগটা হাত ছাড়া করিনি। আস্তে আস্তে ভাব জমাতে শুরু করলাম। শিকলে বাঁধা মনের গোপন কথাগুলো বের হতে থাকলো।
বাড়ি নিতাইগঞ্জ। বাবার নাম কেষ্ট ঠাকুর। তিনিও নাকি যুদ্ধের আগেই গত হয়েছে। মা ছিলো তবে দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগে ভুগে তিনিও ওপাড়ে চলে গেছেন।
বয়স ৫২ ছুঁই ছুঁই। শরীরটা যে খুব ভালো যাচ্ছে সেটাও নয়। তবে এখনো কারোরই দারস্থ হয়নি। এক ছেলে আর মেয়ে নিয়ে সংসার। গৃহকর্ত্রী বছর দুয়েক হলো নিশ্বাস ছেড়ে দিয়েছে।
ইতিমধ্যে চোখের কোনায় অশ্রুজলের ছড়াছড়ি। টপটপ করে কয়েক ফোটা অশ্রুজল পরে গেলো। ভাবলাম কথাগুলো মনকে নাড়িয়ে দিয়েছে। ডান হাত দিয়ে চোখদুটো মুছে ফেললেন। আবেগ আপ্লুত কন্ঠে কি যেন গড়গড় করে বলতে চেয়েও থেমে গেলেন।
-কাকা, কাঁদছেন কেন? প্রিয়জনের কথা মনে পরেছে?
-জি, বাবা। সবসময়ই মনে পরে। তবে যারা জীবিত আছে তাদের কথায় মনে পরে বেশি। আর মনে পরলে বুকের ভেতরটা দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। হৃৎপিন্ডটা পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। যেটুকু বাকী থাকে সেটুকুও ধীরে ধীরে পচেগলে গন্ধ ছড়াতে থাকে।
-কাকা এতো কষ্ট কিসের? কিসের জন্য বুকে এতো হাহাকার?
-আর বলিস নারে বাপ! এতো কষ্ট করে রোজগার করে যাদের মানুষ করালাম তারাই আজ ফাঁকি দিতে শুরু করেছে। পিতৃত্বের পরিচয় বোধ হয় তাদের আর দরকার নেই। বাবা অক্ষরের দুটি শব্দের মানুষটি যে আজও বেঁচে আছে হয়তো তারও কোন খোঁজখবর নেই তাদের কাছে। জমিজমা যেটুকু ছিলো সবইতো নিয়েছে। দেহটাও পারলে বোধহয় এতোদিনে নিয়ে নিতো। ভাসিয়ে দিয়ে আসতো কলাগাছের ভেলায়। বাবারে! মেয়ের কথা বাদই দিলাম। অভাবী সংসারে ছেলে সন্তান নিয়ে কেমন করে আমার সেবাযতœ করবে। তবে যেটুকু সামর্থ্য আছে তার সেবাযতœ করে।
-আর ছেলে?
-ন্ডমম, আর ছেলে! ছেলের কথা বলিস নারে বাপ। বুকের হাড়গুলো ধস্তাধস্তি জবরধস্তি করে ভেঙে যেতে চায় তার কথা শুনে। কুলাঙ্গারটা আমার জমিজমাটুকু লিখে নিয়ে শশুর-শাশুড়ী আর বউ নিয়ে আমোদ প্রোমোদে ব্যস্ত। আমাকে খাওয়াতে নাকি তার অনেক খরচ পরে। বলতে বলতে আবার ধুকধুক করে কেঁদে উঠলেন। কাঁদতে কাঁদতে আবার বলতে শুরু করলেন...।
চোখের কোনায় অশ্রু নামক শব্দটি এসে ভিড় করছে। চোখের পাতা নড়তেই দুই ফোটা অশ্রুজল পরে গেল। নিজেকে হয়তো সংযত রাখতে পারিনি। রাখার কোন কৌশল আছে বলেও আমার জানা নেই। অসহায়ত্বের গল্প বুঝি এরকমই। পুঁজি বলে শুধু হাউমাউ করে কাঁদতে পারা আর দুঃখগুলো বুকের ভিতর চাষ করাটাই মুখ্য বিষয়।
চোখমুখে পানি দিয়ে আবার একটি সিগারেট জ্বালিয়ে পাশে বসে টানছি। দুঃখগুলোকে বিদায় জানানোর জন্য একটি অহেতুক চেষ্টা। ভুলে থাকার বাহানা শুধু। অভিনয় সে-তো অনেক আগেই হৃদয় পুড়ে পুড়ে রপ্ত করেছি।
-বাবা! আমাকে একটা দেওয়া যায় না?
কোন রকম চিন্তা না করেই সিগারেটের প্যাকেট বের করে হাতে দিলাম। একটি পকেটে রাখলেন আর একটি...।
সত্যি কথা বলতে কি এরকম বন্ধুত্ব হয়তো আগে কখনও হয়নি। একজন ৫০ উর্ধ্ব আর একজন যুবক। অভাবনীয় ব্যাপার।
-কাকা, ঢাকায় এসেছেন কেন? কার কাছে এসেছিলেন?
কোন কথায় বলছিলেন না। মনে হচ্ছিল ধোঁয়ার মাঝে নিজেকে মেলে ধরেছে। আশেপাশে তাকানোর কোন সুযোগ নেই। একনাগাড়ে টেনে সিগারেট শেষ করে ফেললেন।
তারপর বললেন,
-বাবা, কি যেন বলতে ছিলে?
-বলছিলাম ঢাকায় কেন এসেছিলেন?
কাকা গড়গড় করে বলতে শুরু করলেন।
বললেন,
- বাবা, আমি মুক্তিযোদ্ধা। হয়তো কাগজ কলমে কোন প্রমাণ নেই। তবে সত্যি বলছি স্বাধীনতা যুদ্ধে দলবেঁধে যুদ্ধ করেছি।
প্রিয় কয়েকজন বন্ধু, সহযোদ্ধাকেও হারিয়েছি মুক্তিযুদ্ধে। ছোট ভাইকেও তো হারিয়েছি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমরা যারা যুদ্ধ করে স্বাধীনতা নামক শব্দটি ছিনিয়ে এনেছি তাদের কপালে কি জুটেছে? কিছুই নয়। হাহুতাশ করা ছাড়া কিছুই করার নেই। অনেক দিন চেয়ারম্যান, মেম্বারদের কাছে গিয়েও কোন কিছু পায়নি। উপজেলা অফিসে গিয়ে কোন সুরাহা হয়নি। সবাই শুধু আশ্বাস দিয়ে যায়। কিন্তু...।
অবশেষে, কেঁদে কেঁদে চোখের জল ফেলতে শুরু করলেন।
বাবা! তারপর থেকে আর কারোরই দারস্থ হয়নি। যেখানে সেখানে দিনরাত পার করি। কখনও খেয়ে আবার কখনও না খেয়ে। কখনও রেলস্টেশনে আবার কখনও গ্রামগঞ্জের চায়ের দোকানেই কাটে সবসময়। তবে বাবা, আমি প্রতিমাসে ঢাকায় আসিনা। বিশেষ কিছু দিন ছাড়া ঢাকায় আসা হয়না আমার। দিনগুলোর কথা মনে পরলে বুকের ভেতর ফাঁকা মাঠের মতো হয়ে যায়। যেখানে শুধু মরিচীকারা বাস করে। শুকনো পাতাগুলো মরমর করে ভাঙতে থাকে।
আমি একটু থমকে গিয়ে বলতে শুরু করলাম, ‘কাকা বিশেষ দিন? মানে বুঝলাম না।’
ভাবলাম এরকম একজন নিরিহ মানুষেরও কি বিশেষ দিন থাকে? যার কারণে দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসা এই ব্যস্ত নগরী ঢাকায়। তাহলে কি সেই বিশেষ দিন? মনের মধ্যে ধীরে ধীরে আরও বেশি আগ্রহ জমতে থাকলো। পিপাসিত কাকের মতো হন্যে হয়ে গেলাম।
-বিশেষ দিন বলতে ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২৬শে মার্চ, ১৬ই ডিসেম্বর। এই তিনদিই আমার ঢাকা আসা হয়। যত ঝর বৃষ্টি, বাঁধা বিপত্তি আসুক না কেন আমাকে তুমি পাবেই।
খুবই শক্ত গলায় কথাগুলো বলতে ছিলেন তিনি। কথার মধ্যে কেমন যেন একটা গন্ধ আমাকে ছুঁয়ে যাচ্ছিলো। ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২৬শে মার্চ, ১৬ই ডিসেম্বর এই তিনটি দিনই যে আমার সত্তাকে নাড়িয়ে যায়। বাংলা ভাষাভাষী সকল মাতৃপ্রাণকে উজ্জীবিত করে।
-কেন কাকা? শুধুমাত্র এইদিগুলোতেই ঢাকায় আসেন কেন?
আবার সজোরে কাঁদতে শুরু করলেন। আমি কয়েকবার চেষ্টা করেও কোন সুরাহা করতে পারিনি। আসলে মনের মধ্যে গুপ্ত কষ্টগুলো এভাবেই মানুষকে আঘাত করে সুখ পায়। আর ভিতরের হৃদয় নামক কলকব্জাগুলো ধ্বংস করতে থাকে।
কান্না জড়িত কন্ঠেই বলতে শুরু করলেন,
-বাবারে! এই তিনটিদিনে আসলে বুকের পাঁজরগুলো ভেঙে তছনছ হওয়ার উপক্রম হয়। নিশ্বাস নিতে চাইলে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে পরি। থতমত হয়ে যায় কণ্ঠনালী। ফুসফাস শব্দ ছাড়া আর কিছুই বের হয় না।
-বাবা রে!! আমি সবচেয়ে বেশি কেঁদেছিলাম কোন দিন জানিস? জানিস না। সেদিনের অশ্রুজলে আমি নিজেই ডুবে যেতাম।
হাউমাউ করে কাঁদতে ছিলেন তিনি। বলতে ছিলেন,
-গত কয়েক বছর আগে ঢাকা শহরে ‘লাখো কন্ঠে সোনার বাংলাদেশ’ অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। অসংখ্য মানুষের আনাগোনায় ভরে গিয়েছিল পুরাতন বিমানবন্দর। দলবেঁধে, যে যার মতো, বিভিন্ন গার্মেন্টস, পোশাক শিল্প, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছাত্রীর পদচারণে মুখরিত হয়েছিল সমস্ত মাঠ। একসঙ্গে লাখো মানুষের জাতীয় সংগীত গাওয়া ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। সেদিন বাংলাদেশ সরকার লাখো কন্ঠে সোনার বাংলাদেশ এর সার্টিফিকেট, পানি, ঔষধ এবং খাদ্যদ্রব্যও বিলিয়ে দিয়েছিলেন। কিš‘ আমার কাছে মনে হয় সেদিনই ছিলো বাংলাদেশের সবচেয়ে অভিশপ্ত দিন। নাহলে কি এইদিন দেখতে হতো? কতো মায়ের বুক খালি করে, কতো বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে, কতো পিতার অশ্রু দিয়ে, কতো নিরীহ মানুষের জীবন বলিদান দিয়ে, কতো ভাইয়ের রক্তের দাগে, কতো নববধূর সিঁথির সিধুর মুছে স্বাধীনতা নামক শব্দটি ছিনিয়ে এনেছি, লাল সবুজের পতাকা উড়িয়ে নিয়ে এসেছি। সবই আজ বিফল মনে হচ্ছে। এই দুঃখগুলো আমাকে প্রতিনিয়ত কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। সেদিন দেখলাম হাজার হাজার পতাকা মাঠে গড়াগড়ি খাচ্ছে, কেউ কেউ ছিড়ে ফেলছে, কেউ কেউ ডাস্টবিনে ফেলে দিচ্ছে, আবার কেউ কেউ...ব্যবহার করছে।
-লাখ লাখ মানুষ সেদিন জাতীয় পতাকার উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো। অগুনিত পতাকা গুলো এভাবেই আর্তনাদে কেঁদে উঠছিলো বারবার বারবার। অনেকেই আবার পতাকার উপর... করছিলো। এই যদি দেশের মানুষের চিন্তাভাবনা হয়, এই যদি দেশের সরকারের উৎসব অনুষ্ঠান হয় তাহলে লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে লাল সবুজের পতাকা অর্জনের দরকার ছিলো না। দরকার ছিলো না ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২৬শে মার্চ, ১৬ই ডিসেম্বরে কোটি কোটি টাকা খরচ করে মিছিল মিটিং, প্রচার প্রচারণা করার। যেখানে বাঙালীরা একটি মাত্র পতাকার সম্মান দিতে পারে না।
-বাবা রে! আমরাতো যুদ্ধ করে স্বাধীনতা এনেছি। বিনিময়ে কিছুই পাওয়ার আশা করিনি। যদি পাওয়ার নেশায় বিভোর থাকতাম তাহলে সেদিন নিজের জীবন বিপন্ন রেখে দেশ রক্ষায় নিজেকে বিলিয়ে দিতাম না।
-বাবা রে! ঢাকায় আসি এই একটাই কারণে। নিজ উদ্যোগে যতটুকু পারি রাস্তাঘাটে, বাসস্ট্যান্ডে, রেলস্টেশনে এমনকি শহীদ মিনারে ছিটিয়ে থাকা পতাকা গুলো কুড়িয়ে এনে একটি নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে দিই। যাতে করে পতাকা গুলো কারো পদতলে না পরে। পদতলে পরলে ব্যথা অনুভূত হয় আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের শরীরে। আহত পতাকার কান্না জড়িত আওয়াজ সবসময়ই কানে বাজে। চিৎকার করে বলতে থাকে এ কেমন স্বাধীনতা!
নিশ্চুপ বসে আছি। দুই হাত দিয়ে মুখটাকে ঢেকে রেখেছি। চোখ খুলে তাকানোর সাহসটুকু হারিয়ে ফেলেছি। এইতো গতকাল ১৬ ডিসেম্বর ছিলো। ভাবতেই অবাক লাগছে আমি নিজেও পতাকার অপব্যবহার করেছি। শাস্তি আমারও হওয়া উচিত। মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার, দাঁড়িয়ে নিশ্বাস নেওয়ার শক্তিটুকু ইতিমধ্যেই হারিয়ে ফেলেছি। কোন রকম শব্দ ছাড়াই কেঁদে উঠলাম।
পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করলাম।
-কাকা, আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমাকে মাফ করে দিন।
-আরে বাবা! কাঁদছিস কেন? কি হয়েছে? তোর উপলব্ধি নিজে থেকেই তোকে মাফ করে দিয়েছে। তোর মতো উপলব্ধি যদি সবার হতো তাহলে...।
ইতিমধ্যে বাড়ি যাওয়ার শেষ ট্রেন এসে গেছে। লজ্জায়, অপমানে তাঁর দিকে না তাকিয়েই ট্রেনে উঠে পরি। শেষবারের মতো এক পলক দেখার জন্য ট্রেনের জানালা দিয়ে তাকিয়ে ছিলাম। কিন্তু মানুষের ভিড়ের কারণে দেখতে পারিনি।
আজ ২২শে ফেব্রুয়ারি। অনেক আশা নিয়েই রেলস্টেশনে বসেছিলাম সারাদিন। কিš‘ যাঁর খোঁজে সারাদিন বসে বসে কাটালাম তাঁর দেখা পেলাম না। ভেবেছিলাম গতকাল ২১শে ফেব্রুয়ারি ছিলো অবশ্যই তাকে এখানে পাওয়া যাবে। কিন্তু না, তাঁকে খুঁজে পায়নি।
ফেরার পথে একটু থমকে দাঁড়ালাম। রেলস্টেশনের একটি দেয়ালে ছবি লাগানো।
সেই মানুষটির ছবি। যাকে আমি খুঁজছিলাম।
হারানোর বিজ্ঞপ্তি, ‘মানসিক ভারসাম্যহীন শ্রী নারায়ণ চন্দ্র দাশের কোন খোঁজখবর পেলে নিচের নাম্বারে যোগাযোগ করুন। তাকে বিশেষ পুরুষ্কার দেওয়া হবে।’
বুকটা ধড়ফড়িয়ে উঠলো। উল্লেখিত নাম্বারে যোগাযোগ করলাম।
বলল, আমরা ওনাকে খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু তিনি...।
-কিন্তু তিনি কি ভাই?
অপরপ্রান্ত থেকে কান্নাজরিত কন্ঠে বলল, ‘তিনি না ফেরার দেশে চলে গেছেন।’
ততক্ষণে দুচোখ অশ্রুজল ভিজিয়ে দিয়েছে। আর কোনকিছু জিজ্ঞাসা না করে শুধু বললাম, ‘আপনার ঠিকানাটা পাওয়া যাবে?’
-ঠিক আছে লিখে নিন...।
একুশ এবং একটি ফুলের আক্ষেপ !
একুশ এবং একটি ফুলের আক্ষেপ
ইয়াকুব শাহরিয়ার
চৌহাট্টায় বসে আছি এক কোনে। পুরোনো অভ্যাস। রিকশা গুনছি। প্রতিজোড়া প্যাডেলওয়ালা পায়ের স্যান্ডেলের বাঁকিয়ে যাওয়া দেখছি। দু’চোখে পড়ছি শীতেও ঘাম ঝড়ার গল্প। পাগলের মতো এসব দেখি; দেখার মতো পড়ি। হুডতোলা রিকশার ভিতর দিয়ে দেখি দুই পৃথিবীর তফাৎ। প্যাডেল পায়ে জীবন যুদ্ধের গল্প টেনে চলে সুখের পায়রা। কত নিষ্ঠুর দুনিয়া! এখানে হরদম চলে এমনই গল্প লিখার সফল সমাপ্তি। আনমনা আমি দেখছি রিকশা-সিএনজির চলে যাওয়া-আসা। হঠাৎ ধুন ভাঙলো আমার। লাল ডোরার সবুজ চাদর গায়ে জড়িয়ে বসেছিলাম। চাদরটি শ্লোগান থেকে কিনেছিলাম ৭শ ২০ টাকায়। চাদরে সৈয়দ শামসুল হকের আমার পরিচয় কবিতাটি লেখা। উলুখাগড়ার মতো চুল, দাঁড়ি আর চাদরে আমাকে পাগলই লাগছিলো। নিজেকে আজকাল পাগল কিসিমের লোক মনে হয়। পাগলের নিজস্ব একটা দুনিয়া দরকার। আমার সে দুনিয়া আছে। এই দুনিয়া নিয়েই এমন ভাবনাই ভাবছি আনমনে। পেচন থেকে কে যেনো খুব কষ্ট করে বানান করে করে কবিতার মাঝখান থেকে একটি লাইন পড়ছে- ‘এ-সে-ছি বা-ঙা-লি রা-ষ্ট্র-ভাষার লাল রাজ-পথ থেকে’। এভাবেই আলগা আলগা করে পড়ছে। বিস্মিত হয়ে পেচন ফিরে থাকাই। একটা উদাম গতরি ছেলে দেখেই মনে হচ্ছে আমার মতোই একজন। পাগল কিসিমের কিন্তু পাগল না। কথা বলতে ইচ্ছে করছিলো। কথা বলছি না; আমার ধুন বাঙলেও তার ধুন এখনো ভাঙেনি। লাইনটা অনেক কষ্টে পড়ে শেষ করে আমার দিকে তাকায়। আর পড়লো না। একটি কাঁচা গোলাপ আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো- ফুল নিবেন? আমি সরাসরি না বলে দিলাম। কিছুক্ষণের জন্য চুপসে গেলো। আবার বললো নেন না মামা একটা। দশ টাকাই তো। চুপ করে রইলাম। তার ফুল বেচার নানা ধরণের আবদার। নেন মামা একটা। কালকে একুশে ফেব্রুয়ারি। শহিদ মিনারে দেবেন। না হলে ভাবীরে দেবেন। আমি তার দিকে দশ টাকার একটা নোট বাড়িয়ে দিলাম। সে আমাকে ফুল দিতে চাইলে নিলাম না। দশ টাকা ফেরত দিয়ে দিলো। বললো- মামা, আমি ভিক্ষা করি না। ব্যবসা করি। তার কথায় আরো অবাক হলাম। কতো আত্মগৌরবী ছেলে!
নিশ্চুপ হয়ে কিছুক্ষণ ছেলেটাকে দেখলাম। টাকা দিলাম না। তার থেকে অনেক কিছু শিখে নিলাম। পুরোটা পৃথিবীই একটা পাঠশালা। যেখান থেকে ইচ্ছা সেখান থেকেই শিক্ষা নেওয়া যায়। আমি এই ছেলেটার থেকে শিক্ষা নিলাম। আত্মগৌরবের শিক্ষা! সন্ধ্যা হয়ে এলো। পিঠা খেতে মন চাইলো। ভাঁপা পিঠা। তাকেও খাওয়ার কথা বললাম। প্রথম দিকে না করলেও আমার জবরদস্ত জোড়াজুড়িতে আর না করতে পারলো না। পিঠা খেতে খেতে তাকে নাম জিজ্ঞেস করলাম। বললো- হাবু। চমৎকার মিশেল দেওয়া নাম। ভালো লাগলো। কিছু কিছু জিনিস দুনিয়ায় আছে, যেটা কোনো রকমের কারণ ছাড়াই ভালো লাগে। হাবুর নামটাও আমার কাছে তেমনই একটা বিষয়। পিঠা খেয়ে হাবুকে ছেড়ে দিলাম। সে মালঞ্চের দিকে হাঁটা শুরু করলো। আমি আর রিকশা গুনতে বসলাম না। বাড়ি ফিরতে হবে। তাই গাড়িতে উঠলাম। কুমারগাঁও বাসস্ট্যান্ড থেকে ৪৮ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে বাড়িতে আসতে আসতে রাত তখন ৯টা।
তখনও হাবুর ঘোর কাটেনি আমার। তাকে নিয়েই ভাবছি। বাতির ভাইয়ের চায়ের দোকানে বসে এককাপ গুড়ের চা গিলে বাড়ির দিকে হাটতে লাগলাম। তখন হাইস্কুলের শহিদ মিনারের দিকে নজর পরে। লাইট দুইটা জ্বলছিলো। কোনো মানুষ নেই। হয়তো রাতের প্রথম প্রহরে দলীয় শ্লোগান ফাটিয়ে স্থানীয় রাজনীবিদরা পুষ্পস্তবক অর্পন করতে আসবেন। আবার নাও আসতে পারেন। এটা তাদের ইচ্ছা। ইদানিং রাজনীতিবিদদের ইচ্ছাতে অনেক কিছুই হয়। যা হওয়ার নয়, তাও হয়। রাজনীতি যেনো এখন সোনার কিংবা রুপার কাটি। একটি দিনের ইতিবৃত্তান্ত দিয়ে চোখবুঁজে আসে আমার।
ভোর ৬টা। আলো ফুটলো বলে দিনের। এখনো দেখা নেই সূর্যের লাল আভারও। ২১শে ফেব্রুয়ারি। প্রভাতফেরির কোনো প্রস্তুতি নেই আগের মতো। ফুল হাতে কোনো কিশোরীর দল খালি পায়ে আসতে দেখছি না। শাদা শার্ট আর নেভি ব্লু-প্যান্ট পড়া নগ্নপায়ী ছাত্র দেখছি না। কুয়াশা ভর করেছে ২১এর বুকে। কিছু কাল অতিক্রম করে ধীরে ধীরে ছেলে মেয়ে আসতে দেখছি আবেগহীনভাবে। জুতাপায়ে। ফুলহীন হয়ে লিপস্টিকে টকটকে লাল দুটি মেয়ের ঠোঁট। বিস্মিত হলাম! যেনো উৎসব যাত্রা। আহ!
আমার লাল সবুজের পাঞ্জাবি ও চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে খালিপায়ে ছোটছি। খালি হাতে। কিছুটা কুয়াশাঘোর কাটছে। মানুষের সমাগম বাড়ছে রেইন্ট্রি তলায়, জামতলায়। স্কুল মাঠে। স্যার ক্রমাগত প্রভাতফেরি শুরুর কথা বলে যাচ্ছেন। স্পোর্টস শিক্ষক বেহিসেবী বাঁশি বাজাচ্ছেন। কে কার কথা শুনছে? অধিকাংশ মেয়ে-ছেলে আলাদা ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আমার মতো কয়েকজন বোকাসোকা সাবেকি, আধাপাগল লোক হাঁটতে শুরু করেছেন। সাথে বেবুঝ কিছু শিক্ষার্থী আর চাকুরীরত শিক্ষকগণ। মেয়েরা আর ছেলেরা আড্ডায় মগ্ন। এ যেনো আনন্দ দিবস! শহিদদিবসের কোনো আবেগ নেই। স্কুল কর্তৃপক্ষের আবেগহীন টাকায় কেনা বড় ফুলের তোরা ছাড়া কারো হাতে কোনো ফুল নেই। সবাই এলোপাতাড়ি হাঁটছে। প্রাতঃভ্রমণের মতো করে কতক্ষণ হেঁটে অনেকটা আক্ষেপ নিয়ে দাঁড়াই শহিদ মিনারের সামনে। চোখজোড়া তখন টলটল করছিলো অতীত ভেবে। ভাষা শহিদদের কথা ভেবে। সকল আক্ষেপকে একত্রে করে দাঁড়াই সালাম-বরকত-রফিক-জব্বারদের সামনে। তখন সবচেয়ে বড় হয়ে উঠে হাবুর জোড় করে দেওয়া একটি গোলাপ না আনার আক্ষেপ। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি মাঠের এক কোণে। লোকজন কমতে থাকে। কিছু অতি সুন্দরী মেয়েরা তাদের সেজে আসাকে ক্যামেরা বন্দি করছে। তখনো মাইকে বাজছে- ‘আমার ভাইয়া রক্তে নাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কী ভুলিতে পারি।’
দক্ষিণ সুনামগঞ্জ