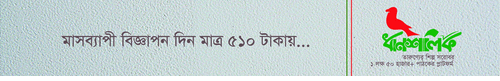পদাবলি
এক নিঃস্পৃহ বৈরাগী
শাহীন মাহমুদ
তোমার ভাষা ছিল হেঁয়ালি উচ্চার্য ডাকিনী মন্ত্র
রহস্যের ধূমল ছায়া তোমাকে বানিয়েছে চাতুরী
দেহের চাবি লুকিয়েছিলে জঙ্ঘার ভাঁজে
নিজে ঘোষণা দিলে তুমি এক নিঃস্পৃহ বৈরাগী ।
একবারও ভাবলে না কর্পোরেট বেশ্যার মতো দাঁড়িয়ে
ডামট্রাক, কাভার ভ্যান, কিছু ঊনমানুষ রাস্তার দুধার
ফুটপাতে চাঁদাবাজ প্রহরী
লক্ষ লক্ষ শুক্রাণু উপছে পড়ছে রাস্তায়, রাজপথে
যদি আসতে না পারি, ধরে নিও আমিও খুন হয়েছি ।
মাছ পুত্রের শহর দর্শন
সাইয়্যিদ মঞ্জু
গেল বারের মত এবারের বর্ষায় ও আসবে
ব্যস্ততম শহর দর্শনে
মাছের মা তাঁর পুত্রদের নিয়ে
উৎফুল্ল মাছ পুত্ররা নাচে খুশির নাচন।
আহ ! কি সুন্দর ইট পাথরের দালানের শহর
বর্ষার যৌবনে যেন এক ঢেউহীন নদী।
যে পথ স্থল, সে পথে বহে পদ্মা মেঘনা যমুনা
একই পথে কখনো গাড়ী, কখনো ডিঙি নৌকায়
ব্যস্ততার এ জীবন গড়িয়ে গড়িয়ে যায়
মাছ পুত্ররা ঘুরে বেড়ায় বিচিত্র শহর
আহ! কি আনন্দ।
উৎসব
আকিব শিকদার
বাবা যাদের সরকারি অফিসে ছা-পোষা কেরানী
তাদের আবার উৎসব কী! তিন বেলা খেতে পাই, এই তো বেশি।
আমরা হিন্দু। অফিসের বড়কর্তা
বাবাকে দিয়েছিলেন নিমন্ত্রণ- ‘বেড়াতে এসো সপরিবারে,
ঈদে খুব আনন্দ হয়।’
প্রভাতে দেখলাম মুসলিম লোকদের পরনে
পাঞ্জাবি-টুপি, হাতে জায়নামাজ, দল বেঁধে
যাচ্ছে ঈদগাহে। নামাজ শেষে পশুর গলায় চালাবে ছুরি।
বেলা বাড়তেই বাবা ডেকে বললেন- ‘চল বেড়িয়ে আসি
স্যারের বাসায়। সম্মানিত লোক, সাক্ষাৎমাত্র
পা ছুঁয়ে করবি সালাম।’
বাবার কথা রাখলাম। স্যার আমাকে
অবাক করে হাতে ধরিয়ে দিলেন
দুটি পাঁচশো টাকার নোট, ঈদের সালামী।
এবং পরম মমতায় বসালেন পাশের সোফায়; খেতে দিলেন
দুধেল সেমাই, ভাজা মিষ্টি পাঁপড়। বাবার সঙ্গে স্যার
কথা বলছিলেন এমন হাস্যোজ্জ্বল ভঙ্গিমায়, দেখলে কে বুঝবে
অফিসের বড়কর্তা আর সামান্য কেরানীতে চলছে আলাপ!
স্যারের একটা ছেলে, আমারই মতন বয়স। দুজনে
অনেকটা সময় খেললাম ক্রিকেট, দেখলাম
কুরবানীর মাংসের কাটাকুটি।
যখন বিদায় নিয়ে চলে আসবো, আমাকে দিলো
খাসির মাংসভরা একটা থলি। প্রায় দু’কেজি ওজন।
চোখ জলে ঝাপসা হয়ে এলো, আর ন¤্রতায়
নতমাথায় ভাবলাম- ‘ধর্ম যাই হোক, কোন উৎসবই
কারও একার নয়, আর ঈদও একটা উৎসব।’
সন্ধ্যাতারা
সোমা বড়ুয়া রিমি
সন্ধ্যা ঘনালে,
মনহারা পাখিও হয় দিকহারা ;
হন্যে হয়ে খুঁজে ঠিকানা,
ক্লান্তিতে শ্রান্তিতে সিটকে-
ক্ষতবিক্ষত হয়েও স্বপ্নগুলো ধরে রাখে।
স্বপ্নগুলোর মৃত্যু হয়না,
স্বপ্নগুলো তারা হয়ে জেগে থাকে,
মানসপটে ছবি আঁকে,
সেই থেকে হয়তো মেয়েটি সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালে
আর সন্ধ্যাতারাটি এসে মিলনসুখে হাসে,
দূর থেকে নিত্য ভালোবাসে।
নৈঃশব্দ্যের শৈল্পিক চিহ্ন
ইসলাম তরিক
সবকিছুতেই শৈল্পিকতা
শৈল্পিকতায় ভরা পৃথিবী
শিল্পী ও শিল্পর মাঝে
বেঁচে আছি আমরা
আমাদের স্রষ্টা মহাশিল্পী যিনি
তিনিও ভালোবাসেন
শৈল্পিকতার নিখুঁত আঁচর
যে মৃত্যুকে আমরা ভয় পাই
সেই মৃত্যুর আলিঙ্গনও একটি শিল্প
তাতেও কতগুলো শৈল্পিক চিহ্ন থাকে
যা ভাবিয়ে তোলে সবাইকে
আমি শিল্পী!
কালের খেয়ায় আমিও আঁকাতে পারি
নৈঃশব্দ্যের শৈল্পিক চিহ্ন।
আয়না
সাঈদ চৌধুরী
আমি আয়নার আত্না হতে চাই
কেবল আয়নারাই জানে মেয়েটি আজ কার জন্য সাজলো...
সাজ বেলায় মেয়েটির সাথে
আমার চোখাচখির সময়
তার হাসিতে মনে হয়েছিল
সে খুব কারুকাজ করে লিপিস্টিক
আর লিপলাইনারে ঠোঁট একেছে আজ,
বেনীর ভাঁজে ভাঁজে যে স্বপটি গেঁথেছে
সেখানেও আমার পদচারনাই ছিল অপেক্ষাকৃত বেশী...
কই, কিছুক্ষণ ব্যপ্তিতে আরও চোখাচোখি দেখলাম
মেয়েটির সাথে অন্য কোন বখে যাওয়া ছেলের
সে হাসিতেও তার অনেক রং
শুনেছিলাম ষোল সতের বছরের কেবল নারী হয়ে ওঠা মেয়েরা
প্রেমময় হলেও নাকি ছলনাময়ীও হয় !
যার চোখে আমি ভোর দেখি
যার নুপুরের শব্দে লাখো কবিতার প্রসব গুনি
তার সাজার কারণ জানতে হলে
তার ব্যক্তিগত আয়নার আত্নাই হতে হবে !
আমি আয়নার আত্না হয়ে
শুধু জানতে চাইবো
মেয়েটির বেনীর ভাঁজে ভাঁজে
আজ কার পদচারণায় হাসনাহেনার গন্ধ দোলে
কতটা পোড়ালে
মারুফ আহম্মেদ নয়ন
আমায় পোড়ালে কতটা তুমি,
জানে ডানা ঝাপটানো পাখি, পাখা পোড়ানো পতঙ্গ।
পুড়ে যাওয়া ফুল, ফসল, শস্যের দানা।
জানে বনপথ, মরে যাওয়া ঘাসের ডগা।
জানে আগুন, হু হু করা বাতাস।
জানে, নোঙ্গরহীন কাঠের নৌকা।
তবুও তুমি যদি বলো, কোথায় কি,
গভীর ক্ষতের চিহ্ন।
তোমাকে দেখাবো বুকের ভেতরে,
এইখানে এইখানে ক্ষয়ে গেছে।
এইখানে এইখানে পচে গেছে।
জীবন
তপন কান্তি মুখার্জি
দিন বদলায়, চলন বদলায়, বয়স বদলায়,
বদলায় না শুধু জীবন । রাতের অন্ধকারে
হঠাৎ করে নেমে পড়া অজানা স্টেশন,
স্টেশনের বাইরে চা দোকান , দোকানের মেয়ে,
বেঞ্চের নীচে শুয়ে থাকা কুকুরের কুঁইকুঁই-
সবকিছু মনে থাকে নিভে আসা কয়লার মতো ।
যাতনার ছায়ায় খসে পড়ে জীবনের পলেস্তারা,
উঁকি দেয় হাড়গোড় । তবু নাকের ডগায় ঝোলে
সুতো দিয়ে বেঁধে রাখা লেবু আর লংকা
অমরত্বের আশায় ।
কুরবানি ও লাল গরুটা
কুরবানি ও লাল গরুটা
কবির কাঞ্চন
সকাল থেকে ঝিরঝিরে বৃষ্টি ঝরছে। ঘনকালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। মাঝেমধ্যে বিজলি চমকাচ্ছে। সেই সাথে বিজরীর মনেও শংকা কাজ করছে। তবে কি আজও কুরবানির হাটে যাওয়া হবে না। গত দুইদিনের টানা বৃষ্টির কারণে গরুর হাট ঠিকমতো বসতে পারেনি। সেকারণে বিজরীরও বাবার সাথে কুরবানির হাটে যাওয়া হয়নি।
আজও সেই অবিরাম বৃষ্টি। বিজরীর মনাকাশে কালো মেঘ ছেয়ে গেছে। একটু পরপর দরজাটা ফাঁক করে বাইরের দিকে তাকায় সে।
দূর থেকে মেয়ের এমন কাজ দেখে সোলায়মান সাহেব মিটিমিটি হাসেন। তারপর বিজরীকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন,
-এভাবে বারবার বাইরে গিয়ে কি দেখছো, মামনি?
বিজরী আমতা আমতা করে বলল,
-না বাবা, বৃষ্টি থামলো কিনা তা দেখছি।
-তো বৃষ্টি কি থেমেছে?
-না বাবা, এখনও ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছে। বাবা, বৃষ্টি এমন কেন? সময়-অসময় বোঝে না। আর মাত্র ক’দিন পর ঈদ। এখন কি বৃষ্টি না হলেই নয়?
সোলায়মান সাহেব বিজরীর কথা শোনে একগাল হাসলেন। এরপর মেয়েকে বুকে টেনে নিয়ে আদর করে বললেন,
-শোন মা, এমন কথা আর কখনও মুখে আনবে না। এই পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণকারী একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহই ভালো বোঝেন। কখন রোদ দিলে সৃষ্টির ভালো হবে। আর কখন বৃষ্টি হলে সৃষ্টির কল্যাণ হবে।
বিজরী মাথানিচু করে বাবার কথায় সায় দিয়ে বলল,
-হ্যাঁ, বাবা, আল্লাহ যা করেন আমাদের ভালোর জন্যই করেন। তবুও।
-না, মা, এরূপ কিছু ভাববে না।
এবার সোলায়মান সাহেব মেয়েকে সাথে নিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন। ব্যালকুনীতে দাঁড়িয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন। বিজরী তখন আনন্দে লাফাতে লাগলো। বৃষ্টি একেবারে থেমে গেছে। আকাশেও কালো মেঘ নেই।
বিজরী বাবাকে উদ্দেশ্য করে বলল,
-বাবা, এখন তো বৃষ্টি নেই। চল, কুরবানির হাটের দিকে যাই।
সোলায়মান সাহেব ব্যস্ততার গলায় বললেন,
-হ্যাঁ মামনি, তুমি ভিতরে গিয়ে রেডি হও। একটুপর আমরা কুরবানির হাটে যাব।
-আচ্ছা, বাবা।
এই বলে বিজরী মায়ের কাছে ফিরে গেল।
বিকাল সাড়ে চারটা। বিজরীকে সাথে নিয়ে সোলায়মান সাহেব কুরবানির হাটের দিকে এলেন। এবার ‘লেবার কলোনী’ মাঠে কুরবানির হাট বসেছে। বিশাল মাঠ। চারিদিকে মানুষ আর মানুষ। সারি সারি গরু বিভিন্ন পয়েন্টে পয়েন্টে বেঁধে রাখা হয়েছে। লাল গরু, সাদা গরু, কালো গরু, দেশী-বিদেশী গরু, বড় গরু, ছোট গরু ইত্যাদি।
সোলায়মান সাহেব জন্মসূত্রে চট্টগ্রামের বাসিন্দা। চরম অসময়েও নিজেদের বংশগত ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে হাটের সবচেয়ে বড় গরু কুরবানি দিতে বাপ-দাদাকে দেখে এসেছেন। নিজেও তার ব্যতিক্রম নন।
পুরো হাটে বিজরীকে নিয়ে গরু দেখলেন। সোলায়মান সাহেবের বেশ কয়েকটি গরু পছন্দ হলেও বিজরীর আপত্তির কারণে সেগুলোর দরদাম করা হয়নি। হঠাৎ বিজরী চিৎকার করে বলে ওঠে, ‘ঐ দেখো বাবা, বিশাল, সুন্দর লালগরু। তোমাকে এই গরুটাই কিনতে হবে।
সোলায়মান সাহেব বিজরীকে সাথে নিয়ে গরুটির কাছে আসলেন। ভালোভাবে গরুটিকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। গরুটির পিঠে সুউচ্চ কুঁজ রয়েছে। বিশালাকার গরুটির পুরো গা লাল রঙের পশমে ঢাকা। রং বেরঙের ঝরি পেঁচানো শিং দেখে মনে হচ্ছে যেন রাজার মাথায় রঙিন মুকুট জ্বলজ্বল করছে। তার উপর গলায় সুন্দর মালা পরানোয় বেশ আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে। গরুটিকে ঘিরে মানুষের ভীড় ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।
সোলায়মান সাহেব বিজরীর কানে কানে বললেন,
-কি মামনি, গরুটি কি তোমার পছন্দ হয়েছে?
বিজরী খুশি মনে বলল,
-বাবা, গরুটি খুব সুন্দর। আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এই গরুটিই নিয়ে নাও।
সোলায়মান সাহেব মেয়েকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,
-আরো আস্তে বল, মামনি। গরুর মালিক শুনলে দাম বাড়িয়ে দেবে।
বিজরী চুপচাপ দাঁড়িয়ে লালগরুটার দিকে তাকিয়ে রইলো।
সোলায়মান সাহেব গরুর মালিকের আরো কাছে এগিয়ে এসে কানে কানে জিজ্ঞেস করলেন,
-ভাইজান, গরুটার দাম কত ?
-দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা।
গরুর দাম শুনে সোলায়মান সাহেবের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়লো। মনে মনে ভাবতে লাগলেন- গরুটির দাম দেড় লক্ষের বেশি হওয়া অন্যায়। গরুটি যে বিজরীর খুব পছন্দ হয়েছে তা নিশ্চিত গরুর মালিক বুঝতে পেরেছে । তাছাড়া আমার বাজেট মাত্র ‘এক লাখ’ টাকা।
ইত্যাদি ভাবতে ভাবতে বিজরীর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে গরুর মালিককে বললেন,
-ভাই, দেড় লক্ষ টাকা হবে।
-না, ভাই, আমি গরুর দাম বেশি চাইনি। যদি নেন একদাম দুই লক্ষ টাকা দিতে হবে।
সোলায়মান সাহেব মন খারাপ করে বিজরীর কাছে ফিরে আসেন।
বিজরী উৎফুল্ল হয়ে বলল,
-বাবা, গরুটি কি নিয়েছো?
-না, মা, চল আমরা অন্য কোন গরু নেব। গরুর মালিক অনেক বেশি দাম চাইছে।
এই কথা বলে সোলায়মান সাহেব বিজরী সাথে নিয়ে হাঁটতে লাগলেন। বিজরী গরুটার দিকে তাকিয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো। কোন অজানা কারণে গরুটিও বিজরীর দিকে তাকিয়ে হাম্বা হাম্বা স্বরে চিৎকার করতে লাগল। উপস্থিত লোকজন বিজরীর দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। সোলায়মান সাহেব বিজরীকে আপ্রাণ বুঝালেন। কিন্তু বিজরীর সেই একই কথা। লালগরুটা কিনতে হবে।
গরুর মালিকও বিষয়টি লক্ষ্য করলেন। তারপর গরুটির দড়ি হালকা ছেড়ে দিয়ে সোলায়মান সাহেবের কাছে এসে বললেন,
-ভাই, ও কি আপনার মেয়ে?
-হ্যাঁ।
-এভাবে কান্না করছে কেন?
- আপনার গরুটা ওর খুব পছন্দ হয়েছে। আমারও। কিন্তু আমার বাজেট ছিল এক লক্ষ টাকা। আমি দেড় লক্ষ টাকা বলেছি শুধু আমার মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে।
গরুর মালিক একটু ভেবে নিয়ে বললেন,
-শুধু আপনার মেয়ের জন্য গরুটি আমি আপনার কাছে বিক্রি করছি। তবে আমাকে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা দিতে হবে। তাতে আমার খুব একটা লাভ হবে না।
সোলায়মান সাহেব আর কোন কথা না বাড়িয়ে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা মূল্যে গরুটি কিনে নিলেন।
গরুর মালিককে কানে কানে বললেন,
-ভাই আমি আসবার সময় এক লক্ষ টাকা নিয়ে এসেছিলাম। বাকী টাকা বাসা থেকে দেব। প্লিজ আপনি যদি আমাকে একটু সাহায্য করতেন।
গরুর মালিক হাসিমাখা মুখে বললেন,
- চলুন, আমিই আপনার বাসা পর্যন্ত গরু পৌঁছে দিই।
-এ আপনার বদান্যতা। অশেষ ধন্যবাদ।
গরুর মালিক গরু নিয়ে বিজরীদের বাসার দিকে ছুটছে। বিজরী তার বাবার হাত ধরে আনন্দে হাঁটছে। সে মনে মনেতো কী ভাবছে! বাবা যখন গরুকে গোসল দিবেন তখন নিজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা উপভোগ করবে। গরুকে খাবার দেবার সময় নিজের হাতে দিবে। আরও কতো কী!
বাসায় এনে প্রথমে বাসার সম্মুখের প্রধান ফটকের সাথে বেঁধে রাখা হলো। গরুর মালিক তার পাওনা বুঝে পেয়ে নিজ গন্তব্যে চলে গেলেন।
শুরু হলো গরুর পরিচর্যা। কিছুক্ষণ পরপর ভালো ভালো খাবার খাওয়ানো হচ্ছে। খাবার দেবার সময় বিজরী ভয়ে ভয়ে গরুর মুখে খাবার তুলে দেয়। গরুটিও মাথা নাড়তে নাড়তে তা মুখে নিয়ে নেয়। এরপর কিছু মুহূর্ত তা চিবিয়ে স্থির দাঁড়ালে বিজরী আবার দেয়।
এই দুই দিনে বিজরী ও লালগরুটির মাঝে খুব ভাব হয়। এক মুহূর্ত সময় পেলে বিজরী গরুটির কাছে ছুটে যায়। আশপাশের লোকজন নিয়মিতভাবে লালগরুটিকে দেখতে আসছে।
আগামীকাল ঈদ। লাল গরুটির পুরো মুখমন্ডলে বিষন্নতা। চোখ থেকে পানি ঝরছে। বিজরী মনে মনে ভাবছে, তবে কি লালগরুটি বুঝে গেছে কাল ঈদের দিন তাকে কুরবানি দেয়া হবে! তা কি করে সম্ভব! ওরা কী মানুষের কথা বোঝে? মনে হয় না। বুঝলে কি আর এভাবে বাঁধা থাকতো। তখন তো দড়ি ছিঁড়ে পালানোর চেষ্টা করতো।
ইত্যাদি ভাবতে ভাবতে বাসায় ফিরে আসে সে।
আজ কুরবানির ঈদ। চারিদিকে পশু কুরবানি হচ্ছে। ইতোমধ্যে
বিজরীদের গরুটির পা ভালো করে দড়ি দিয়ে বেঁধে গলাটা পশ্চিম দিক করে শোয়ানো হয়েছে এবং কিছু লোক পা ও মাথা শক্ত করে চেপে ধরে আছে । গরুটি ভেজা চোখে যেন শেষবারের মতো বিজরীকে ে দেখার জন্য ঘাঁড়টা নাড়াতে চাইল। অদূরে বিজরী বিষন্ন মনে দাঁড়িয়ে আছে। ওর চোখ দুটো যেন ছলছল করছে।
একটুপর হুজুরকে লাল গরুটির গলায় ছুরি চালানোর প্রস্তুতি নিতে দেখে বিজরী দু’হাতে মুখ ঢেকে দৌড়ে বাসার ভিতরে চলে গেল। আর এইদিকে উচ্চস্বরে ধ্বনিত হলো , ‘বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর’।
উছল আর ঢেউতোলা কবিতার স্বার্থক কবি
উছল আর ঢেউতোলা কবিতার স্বার্থক কবি
ফরিদা ইয়াসমিন সুমি
মাহমুদ নোমান
ছন্দের বালাই নেই, গীতল শব্দের অববাহিকায় কিছু খুচরো চিত্রকল্প আর ফরফর বাতাসে ভাসানো নীল উড়নার মোহনিয়া উপমাতে ছোট্ট কবিতার ঘর ফরিদা ইয়াসমিনের কবিতার বই ‘প্রজাপতি মন’
। যেন ভালবাসার নানা রঙ নিয়ে উড়াউড়ি করছে প্রজাপতি প্রতিটা কবিতার অক্ষরে অক্ষরে। মনে হয়েছে কোমরে উড়না বেঁধে আবেগের শার্টটি ধুয়ে, সযতনে কপালের ঘামবিন্দুটিও ঝেড়ে শুকাতে দিয়েছেন হালকা রোদে। প্রতিটি কবিতা পড়তে আঁচ লাগে এ রোদের-
তোমার বুকে টেনেছো বলে
হিমালয় আমায় টানে না
তোমার অরণ্যে হারিয়েছি বলে
আমাজনের পথে হাঁটি না
[তোমার মালিকানা পেয়েছি বলে ১১ পৃ ]
আধুনিক কবিতা মানে প্রচ্ছন্ন আড়াল থেকে মানে নেকাবের ভেতর থেকে কথা বলা। অর্থ্যাৎ এক সত্যকে অপর সত্যে প্রকাশ করার নাম পরাবাস্তবতা। ফরিদা ইয়াসমিন সুমির কবিতায় এ দিকটা অস্বীকার করে এটা বলবো না, হয়তো কবির এটা নিজস্বতা। এটাকে আমি শ্রদ্ধা করি। এখনতো এক কবি আরেক কবিকে অস্বীকার বা হেনস্থা করার মহারণে নামে। আমি ওদেরকে প্রশ্ন করি, কেন নামেন...?
হ্যাঁ, জানি উত্তর পাব না। কেন পাব না...? পাব না এ কারণে যে, অন্যকে অস্বীকার করা মানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার হৈ চৈ, এরা এক ধরণের মানসিকভাবে বিপর্যস্ত বটে । রবীন্দ্রনাথের একটা কথা স্মরণযোগ্য এ ব্যাপারে-
‘যিনি প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কবি হইয়াছেন তিনি সহজে কথার কবি, সহজ ভাবের কবি।’
ভাব, ভাবনা, চিন্তা, চেতনা, বক্তব্য ইত্যাদি জীবনসংলগ্ন বা জীবনঘনিষ্ট হতে পারে। শিল্পসাহিত্যে যে জীবনের কথা বলে তারই টিকে যাবার সম্ভাবনা, সে-ই আদৃত হতে পারে মানুষের কাছে। আর যে জীবনবিমুখ সে শুধু ছড়ায় তার উৎকট ভাবের দুর্গন্ধ। আমাকে সেটা কখনো টানে না, যদিও হয় মিলন কখনো না, ভাবের ধর্ষণ কেবল। তবে অনেকে তাতে সুখ খুঁজে পেলে পাক, তা ভাববার অবকাশও নেই। ফরিদা ইয়াসমিন সুমীর কবিতা সাধারণের মধ্যে অসাধারণত্ব। মনে হয় তিনি সবার জন্য কবিতা লিখলেন, কেন মনে হবে না...? ভালোবাসাই তো সার্বজনীন, সবার কাছে সমান আবদার। তাই ফরিদা ইয়াসমিন সুমী এ ভালোবাসার খোলস থেকে বেরুতে চান না সেটা না বলে বলবো ভালোবাসাতেই থাকতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ। তাই ‘প্রজাপতি মন’ কাব্যগ্রন্থটি আপাদমস্তক একটি ভালোবাসাকে মলাটবন্দী করেছে। এ কাব্যগ্রন্থে ফরিদা ইয়াসমিন সুমী অন্ত্যমিলে পাঠককে সাথে নিয়ে কাব্য করার খায়েশে পাঠকের আত্মার খোরাক বা অংশগ্রহণ বিষয়টি জাগিয়ে দিয়েছে। যেমন ‘চলো ভিজি’ কবিতায় লিখলেন-
চলো ভিজি এই অবেলার তুমুল বৃষ্টিতে
প্রেম ধরি চলো দু’জোড়া প্রগাঢ় দৃষ্টিতে
সিঁথিতে সাজাই যতো নীল তারকার ফুল
চুলে বাঁধি কাজলকালো মেঘরাজির দুল
[চলো ভিজি; ১২ পৃ]
ফরিদা ইয়াসমিন সুমির কবিতা সহজাত, সাবলীলতায় স্বীকারযোগ্য এই বলে ঠেস্-গুঁতায় বলা যাবে না এসব কবিতায় নতুনত্ব নেই বা নিরীক্ষা নেই। হ্যাঁ, এটাই ঠিক এদিকে নিয়মমাফিক যাতায়াত না করে নিজস্ব বলয়ে কবিতাগুলোতে স্মার্ট শব্দগুচ্ছে আলাদা টিউনিং, পাঠককে তৃপ্তিকর অনুভূতি দিতে পারঙ্গম। কেননা এখানে জটিলতা নেই, আন্তরিকতা আছে। আর গদ্যছন্দেও বেশ কয়েকটি কবিতা এই ‘প্রজাপতি মন’ কাব্যগ্রন্থের শৈল্পিক ওজন-উচ্চতার পরিমাপক। বিভিন্ন রুচির পাঠককে কাব্যিক রস্বাদনে ফরিদা ইয়াসমিন সুমির অনন্য মুন্সিগিরি। উছল আর ঢেউতোলার অপরূপ তাল- লয়ে পাঠককে দোলা দিয়ে যাবে ফরিদা ইয়াসমিন সুমির কবিতা, নিঃসন্দেহে-
ক. কান পেতে শোনো
বৃষ্টি ঝরার শব্দ
ভালোবেসে আজ
চলো হই নিস্তব্ধ
[বৃষ্টি ও প্রেম ৬১ পৃ ]
খ. সাগর ঘুরে নোনা হয়ে
আবার এসো তীরে
বুকের মায়া পাতাই রবে
শ্যামল দু’কূল ঘিরে।
[কোনো এক নদীকে ৫৯পৃ]
গ. খুব করে চাইছি,
আকাশে ভীষণ মেঘ জমুক আজ
মেঘের ফাঁকে রুপোলি বিদ্যুৎ চমকাক!
খুব করে চাইছি,
তুমুল ধারায় বৃষ্টি নামুক আজ
বানের তোড়ে খানাখন্দ ভরে যাক!
[খুব করে চাইছি; ৫৭ পৃ]
সত্যিই, ফরিদা ইয়াসমিন সুমির কবিতায় পাঠকের মনের খানাখন্দ ভরে যাক, ঘুচে যাক অপ্রাপ্তি। ভালোবাসায় ভরে যাক পৃথিবী ‘প্রজাপতি মন’ এ...
স্মৃতি বড় বিষণ্নময় !
স্মৃতি বড় বিষণ্নময় !
ফৌজিয়া লীনা
ঈদ মানে হাসিখুশি, ঈদ মানে আনন্দ। ঈদকে ঘিরে প্রত্যেকেরই কিছুনা কিছু স্মৃতি থাকে ; আমারো তাই। প্রত্যেক ঈদে ঘুম থেকে উঠে মায়ের হাতের পিঠা-পায়েশ খেয়ে তারপর আস্তে আস্তে ঘর-দোর সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। তবে বরাবর ঈদে আমার প্রধান কাজ ছিল দাদীকে সাজানো। উনাকে গোসল করিয়ে নতুন কাপড় পরিয়ে বসিয়ে রেখে তারপর নিজের কাজে যাওয়াটাই ছিল রুটিনমাফিক কাজ। অনেক সময় মা দাদীকে গোসল করিয়ে বলতেন যা তুই বাকী কাজটুকু সেরে নে। তখন নিজেকে খুবই দায়িত্বশীল মনে হত। এ যেন এক অসীম তৃপ্তি, ঈদের দিনে বাড়তি কিছু আনন্দ।
কিন্তু, গতবছর থেকে মহান আল্লাহ্ তায়ালা আমার কাঁধ থেকে মহৎ এই দায়িত্বটি চিরতরে কেড়ে নিয়েছেন। ২০১৭ সালের ৩১ মে আমার দাদী আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন ওপারে, না ফেরারই দেশে। সে বছরের দু’টি ঈদই ছিল আমার জন্য সীমাহীন যন্ত্রণাদায়ক। দাদীকে ছাড়া ঈদ; এটা ভাবতে গেলেই কেমন যেন শিহরিত হই, শীতল হয়ে আসে পুরো শরীর, অদ্ভুত এক টান লাগে কলিজায়, এমন কষ্ট অনুভূত হয় যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।
দাদীকে ছাড়া এটি আমার চতুর্থ ঈদ। এখনকার ঈদের সকালটা কেমন জানি অসম্পূর্ণ লাগে। মা আর আমাকে বলেন না
‘যা তোর দাদীর গোসলটা সেরে নে অথবা গোসল করানো শেষ তুই শুধু কাপড়টা পরিয়ে চুলটা আঁচড়িয়ে দিয়ে আয়’। এখন আর মুচকি হাসি দিয়ে কেউ আমায় বলেনা, ‘পিনআপ করে কি করবি আমার আর ওসবের বয়স আছে নাকি’! এসব ভেবে ভেতরটা কেমন খাঁ খাঁ করছে।
দাদী নেই ঠিকই কিন্তু দাদীর উপস্থিতি আমি সবসময় টের পাই। আমি অনুভব করি উনি আমার আশেপাশেই আছেন।
কেন যে এমন হয়; এত মায়ার মানুষগুলা কেন কাঁদিয়ে চিরতরে চলে যায়। খুব কাছের কেউ, অতি আপনজন হারানোর যন্ত্রণা কেমন হয় দাদীকে হারিয়ে আমি তা বুঝেছি।
দাদীকে আমি খুব বেশি মিস করিওপারে ভালো থেকো, অনেক বেশি ভালো থেকো।
ধারাবাহিক উপন্যাস : রামবন্দনা : শাদমান শাহিদ : পর্ব ০৬
রামবন্দনা
শাদমান শাহিদ
সব আপনাদের দয়া। এজন্যই বোধ হয়, ঘুরতে ঘুরতে আপনার প্রাসাদে চলে এসেছি।
আরেকটা কথা মা।
কী?
বনের অন্যান্য সরীসৃপ প্রাণী, এই যেমন টিকিটিকি, তক্ষক, বিচ্ছু, কচ্ছপ, গুইসাপ প্রভৃত্তি প্রাণিরাও কীভাবে যেনো আপনাদের জাতে উঠে গেছে। তারা আপনাদের নামের জিগির তুলে আমাদের প্রতি নানান তা-ব চালায়। যখন-তখন যাকে ইচ্ছে ছোবল মারে। একছেলে-দশছেলে বোঝে না। ভাগে পেলেই ছোবল মেরে শেষ করে দেয়। যার দশ ছেলে, সেখান থেকে একটা মরে গেলে শোকটা ততো গাঢ় হয় না। কিন্তু মা, যার একটা মাত্র অবলম্বন, তার কী উপায়? আপনি এসব বন্ধ করে দিন। আর সওদাগর সাবের উপর থেকে আপনার ক্রোধ উঠিয়ে নিন। তাকে সর্বস্বান্ত করেছেন। সাতপুতসহ সপ্তডিঙা গ্রাস করে নিয়েছেন। আপনি তাকে সব ফিরিয়ে দিন। কথা দিলাম, আমরা তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে যেভাবেই হোক— আপনার অনুগত করে আনবো।
তোমরা তো সবই বুঝ, জানো। সওদাগরকে আমি ইচ্ছে করে কিছু করিনি। যা হয়েছে, সেটা তার কর্মফল। তোমাদের মতো আমার কয়েকজন ভক্ত তার পরিবারেও রয়েছে। তারা সারাক্ষণ সওদাগরের ভয়ে তটস্থ থাকতো। এখানেই শেষ নয়, গোপনে গোপনে আমার পূজা সাজিয়ে এটা ওটা চাইতো। আমিও সন্তুষ্টচিত্তে সব উজাড় করে দিতাম। বিষয়টা একদিন সওদাগরের চোখে পড়ে গেলো। সেদিন আমার ভক্তরা তার রক্তচক্ষুর ভয়ে একেবারে মাদুলির মতো ছোট হয়ে গেলো। তারপরও সওদাগরের রোষ থেকে তারা বাঁচতে পারলো না। সে তাদেরকে তো শাস্তি দিলোই, সে-সাথে লাথি মেরে আমার মূর্তিসহ পূজার সব উপকরণ গুড়িয়ে দিলো। এরপরও কি তোমরা তার হয়ে উকালতি করবে!
তারপরও মা, তাকে ক্ষমা করে দিন। তার হারানো দিনগুলো ফিরিয়ে দিন। বিনিময়ে আপনি যা বলবেন, আমরা তা-ই করবো। আপনার পরিবারের সকলের মূর্তি ঘরে ঘরে স্থাপন করে পুজো জারি দেবো।
সত্যি বলছো তো?
মা কালীর দিব্যি।
আবার মা কালী কেনো?
ভুল হয়ে গেছে মা। মাফ করে দিন। আর কখনো মুখ দিয়ে আপনার নাম ছাড়া অন্যকিছুু বের হবে না।
আচ্ছা ঠিক আছে। প্রথমবার হয়েছে বলে মাফ করে দিলাম। এখন যাও। বিশ্রাম করো গে। তোমাদের জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা হচ্ছে। খেয়ে দেয়ে মর্তে ফিরে যাবে।
আচ্ছা।
মা
আবার কী?
আপনি অনুমতি দিলে স্বর্গটা একনজর ঘুরে দেখবার চাই। কুরানে-পুরাণে কতো পড়েছি। পৃথিবীর মহামনীষীরা স্বর্গ-নরক ভ্রমণ করেছেন। আজ এতো কাছে এসে ফিরে যাবো, তা কি হয়!
বাছারা, এটা তো স্বর্গ নয়, পাতালপুরী। স্বর্গে থাকে পার্বতী। বাবা বলেছেন, তোমরা আমার পূজা করলেই আমি দেবী হতে পারবো এবং স্বর্গে স্থান পাবো। এটা আমার বানানো প্রাসাদ। বলতে পারো কৃত্রিম স্বর্গ। যাও, এটাই একনজর দেখে এসো। তবে বেশি দূর যেও না, আশ-পাশটা দেখেই তাড়াতাড়ি চলে এসো।
অনুমতি পেয়ে আমরা কৃত্রিম স্বর্গের বহিরাঙ্গণ ঘুরে দেখতে লাগলাম। মনে হচ্ছে ইন্টারনেটের ভার্চ্যুয়াল সাইটের ভেতর বুঝি ঢুকে গেছি। চোখ ধাঁধানো দৃশ্য। মানচিত্রের দাগের মতো আঁকাবাঁকা পথ। কোথাও উঁচু কোথাও নিচু। কোথাও সবুজ অরণ্যানী। তারপরেই বিশাল বিশাল নদী। এগুলো আমাদের পদ্মা-মেঘনা-যমুনা নয় তো! দৌড়ে গেলাম দেবীর কাছে।
মা, এই জায়গাটা কেমন যেনো চেনা চেনা লাগছে। আসলেই কি তাই?
দেবী তখন মিটি মিটি হাসেন।
তার মানে যা ভেবেছি—। আমরা তখন শতোৎসাহে আরো বেশি করে ঘুরে দেখতে লাগলাম। যতোই দেখি ততোই মুগ্ধ হই আর মহাকবি কালিদাসের জন্যে আফসোস বেড়ে যায়। আহ! তিনি যদি ভাগিরথীর পূর্ব পাড়ে জন্ম নিতেন। নিশ্চয়ই ‘মেঘদূত’এর পা-ুলিপিটা সামনে রেখে আবার নতুন করে ভাবতেন।
আমরা নদীর পাড় ধরে হাঁটতে থাকি। কখনো নলখাগড়া, কখনো কেয়াকাঁটার ঝোপের ভেতর দিয়ে। তারপরই হঠাৎ টের পাই, পায়ের নিচে কী যেনো মরমর করে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। তাকিয়ে দেখি মাথার খুলি। এক দুটো নয়, শতশত। ঘটনা কী!
পরক্ষণেই দেখি কেয়াবনে পরতে পরতে কারা যেনো শব্দহীন ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখতে মাজার-আস্তানার পাগলদের মতো। মুখে লম্বা দাড়ি, মাথায় জটা, কাঁধে ঝোলা।
বিষয়টা কী হতে পারে ভাবতেই মাহবুব রেজা জানায়, লোকগুলো কোনো সাধারণ মানুষ নয়। সাধু-দরগার গাঁজাখোরদের মতো সস্তা পাগলও নয়। ছবি-সুরতে মনে হচ্ছে, এরা তান্ত্রিক। বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে এমন বেচুইন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।
যা ইচ্ছে হোক, চলো, সামনে এগুই। ঐ দেখো আকাশ ছোঁয়া পাহাড়। নিশ্চয়ই ওটা তাজিন ডং হয়ে থাকবে। চলো, ওটার চূড়ায় গিয়ে ওঠি।
দাঁড়াও, বিষয়টা ভালো কইরা দেইখ্যা লই।
তুমি দেখো, আমরা যাই।
দাঁড়াও না, পাহাড় কি যাইতাছে গা?
লেখকদের এই দোষ, সবকিছুতেই তলা খুঁজে দেখার অভ্যাস।
কবি-সাহিত্যিকদের অতিরিক্ত একটা চোখ আছে জানো তো?
কি জানি, থাকলে থাকতেও পারে।
এজন্যেই লোকেরা তোমাদের নিয়ে বিটলামি করে। কিছুক্ষণ আগেই দেবীর সাথে চমৎকার বাচচিৎ করে এলে। তখন একবারও মনে হয়নি তোমরা বেবোঝ। অথচ এখন চোখের সামনে এতোবড়ো একটা ঘটনা চিৎ হয়ে আছে দেখেও চোখে ধরা পড়ছে না।
কী বলতে চাও?
বলতে চাচ্ছি, এরা সাধারণ সাধু-সন্ন্যাসী নয়। হাতে ত্রিশূল, কপালে চন্দন, সে-সাথে রহস্যময় বিচরণ দেখে মনে হচ্ছে এরা কাপালিক।
কাপালিক মানে?
কাপালিককে চিনতে পারছো না? ঐ যে, বঙ্কিম বাবুর ‘কপালকু-লা’ উপন্যাসের কাপালিক চরিত্রটা?
হা হা মনে পড়ছে। খুব ভয়ঙ্কর চরিত্র ওটা। মানুষ খুন করে রক্তপান আর লাশের বুকে চড়ে বসে তন্ত্র-মন্ত্র সাধনই তার কাজ।
ঠিক ধরেছো। আমার মনে হচ্ছে এলোকগুলো এমনই কোন কারণে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে।
হবে হয়তো।
হবে হয়তো কী? আমার ধারণাই ঠিক। এই দেখো বনের ফাঁকে ফাঁকে কত কঙ্কাল। এগুলো কি এমনি এমনি চলে এসেছে এখানে?
দুরু, কী যে বলো না তুমি। কাপালিক এখানে আসবে কেনো? এখানে যারা আছে তারা সবাই মা মনসার শিস্য।
শিস্য বলেই তো ভয়টা বেশি লাগছে। চলো, অন্য কোথাও যাই, এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাটা নিরাপদ মনে হচ্ছে না।
থাক, কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। চলো, দেবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মর্তে চলে যাই।
হা, চলো।
তারপর চলে এলাম দেবীর কাছে। দেখি তিনি প্রসন্ন মনে কী যেনো ভাবছেন। সে ভরসাতেই বললাম, মা, এসব কী?
কোথায়?
এই যে স্থানে স্থানে স্তুপ স্তুপ মাথার খুলি।
ও একথা। এগুলো কিছু না। যাও। খাবার প্রস্তুত হয়েছে। খেয়ে দেয়ে মর্তে ফিরে যাও।
আমরা তখন খেতে বসি বটে। কিন্তু প্রশ্নটা তখনো মাথার ভেতর লাঠিমের মতো ঘুরতে থাকে।
খাবার পর্ব শেষে দেবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে আসবো। এ মনে করে যখন অন্দর মহলের দিকে ঢু মারতে গেলাম, তখনই শুনি কাকে যেনো তিনি ভর্ৎসনা করছেন। দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলতে লাগলেন, ওরা যখন ওদিকে যায়, তখন তুমি কোথায় ছিলে? আমার তো মনে হয়, তারা কাপালিকদেরকেও দেখে থাকবে। তখন? হুজুগে বাঙালি বলে কথা, কোনটা থেকে কোনটা নিয়ে দুনিয়া মাত করে দেয়, বলা যায়? যাও, খুলিগুলো এখনই মিশিনে ফেলে পাউডার করে ফেলো। তারপর যা খুশি করো। পারলে ভালো কোনো কোম্পানির নাম লাগিয়ে বাজারে ছেড়ে দিতে পারো। এতেও যদি কিছু আয় হয়। এমনিতেই গবেটের দল পালতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠছি। সরীসৃপ প্রাণী ছিলাম, ওটাই ভালো ছিলো। কেনো যে দেবী হওয়ার বাসনা জাগলো...
ফোঁস ফোঁস করতে লাগলেন দেবী। ভয়ে আমাদের অবস্থা তখন দেখার মতো। মনসা বলে কথা। অবস্থা বেগতিক দেখলে ছোবল মারতে মুহূর্ত সময় নেবে না। বিদায় পর্বের দরকার নেই। তাড়াতাড়ি জান বাঁচাই। যে চিন্তা সে কাজ। কাউকে কিছু না বলে দ্রুত বেরিয়ে আসতে লাগলাম।
এ সময় মাহবুব রেজা ফিসফিসিয়ে বলতে লাগলো, দেখলে তো আমার ধারণাই ঠিক। এই শালারা কাপালিক। লাশের খোঁজেই এমন বেচুইন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাগ্যিস ওরা আমাদের দেখতে পায়নি। দেখলে অবস্থা খারাপ হয়ে যেতো। দেবীও তাদের পক্ষেই রায় দিতেন।
সকালে ঘুম থেকে জেগে শুনি রাতে পুলিশ এসে অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা আবু বকর সিদ্দিকি সাহেবের বড়ো ছেলে বিরোধী দলীয় যুবনেতা মাসুদকে ধরে নিয়ে গেছে। আমাদের জানামতে তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা নেই। অতএব পুলিশ এখন ধরে নিয়ে গেলেও দুপুর পেরোনোর আগেই ছেড়ে দেবে। এ ভেবে এক প্রকার নির্ভার মনেই বিষয়টাকে পাত্তা না দিয়ে মহল্লার সবাই যার যার কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। আমিও পার্টির অফিসে যাই। রাজেশ দা’র কথা, মাত্র দশ হাজার কর্মী জেগে উঠলে কয়েদখানার প্রতিটা ইট পেঁজাতুলোর মতো উড়ে যাবে। তারপর থেকেই একটু আধটু নড়েচড়ে বসার চেষ্টা। অফিসে গিয়ে দেখি সাজ্জাদ। নাটকে নাকি প্রাণ পাচ্ছে না। পাবে কি করে, সবক্ষেত্রেই যে দাড়িয়াবান্ধা কোটের মতো দাগ আঁকা। এর বাইরে গেলেই আউট। এতো ছকের ভেতর খেলা-ধুলা চলতে পারে কিন্তু শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি নয়। বললাম, নাটক তুমি অবশ্যই করবে। তবে সে-সাথে রাজনীতির দীক্ষাটাও প্রয়োজন। পার্টির অফিস যেহেতু চিনেছো, তখন আশা করি ওটাও হয়ে যাবে। তারপর ওকে নিয়ে মার্কেটে গেলাম। দুজনের ইচ্ছে মতো শপিং সেরে অনেকদিন পর স্টার প্লাসে ঢুকলাম। মদের দরিয়ায় ভাসতে ভাসতে অনেক কথাই হলো। একটা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হিসেবে জয়েন্ট করেছে। সেলারি যা শোনালো মন্দ না। বাবা নেই, মা-বোন নিয়ে তিনজনের সংসার। বাবার রেখে যাওয়া ব্যাংক ব্যালেন্স আর চাকরিতে খুব ভালো ভাবেই চলতে পারবে।
(চলবে)
দুঃখের আরেক নাম হেলাল হাফিজ
দুঃখের আরেক নাম
হেলাল হাফিজ
রাহাত রাব্বানী
হেলাল হাফিজ । নামটি উচ্চারণ করতে গেলেই শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় অনেকটা স্থির হয়ে যাই । কবি হিসেবে যেমন, ব্যক্তি হিসেবেও আমাদের তেমন প্রিয় তিনি। নিজেকে আড়ালে রেখে কবিতায় মানুষ জমিয়ে যাচ্ছেন হেলাল হাফিজ । ব্যক্তি হেলাল হাফিজকে যারা চিনেন বা জানেন না; তারাও জানেন কবি হেলাল হাফিজের নান্দনিক কবিতার নানান পঙক্তি। বিংশ শতাব্দীর শেষাংশে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেন বাংলাদেশের আধুনিক এই কবি । তিনি সেই বিরলপ্রজদের একজন যিনি মাত্র একটি কবিতার বই দিয়ে বাংলা কবিতায় গড়েছেন নিজস্ব আবস্থান । প্রেম-বিরহ-বিপ্লব কোনটি নেই তাঁর কবিতায়? তিনি সময়কে লিখেন কবিতার শরীরে। আর তাই তো ’৬৯-র গণঅভ্যুত্থানে প্রথম তিনিই লিখেন,
“ এখন যৌবন যার মিছিলে যাওয়ার তার শ্রেষ্ঠ সময়
এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাওয়ার তার শ্রেষ্ঠ সময়।”
[ নিষিদ্ধ সম্পাদকীয় ]
এ দুই পঙক্তিতেই কবি হেলাল হাফিজ অমরত্ব অর্জন করেছেন । কবিতামোদী ও সাধারণ পাঠকের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়ে থাকে এ দুই লাইন । তবে এ কবিতায় সেরা আরেক অংশ হলো প্রেম ও দ্রোহের নিপুণ মিশ্রণ। যা খুব কম কবিই করেছেন ।
“...কোনো কোনো প্রেম আছে প্রেমিককে খুনী হতে হয়”
প্রেমের কবিতাতেও কবি হেলাল হাফিজ অনন্য । কবিতা লিখেই প্রেয়সীর সব ঋণ শুধ হয় না, এ সত্য মেনে নিয়েই নির্মাণ করেন-
“...আঙুল দিয়ে আঙুল ছুঁয়েছিলাম বলেই আমার
আঙুলে আজ সুর এসেছে,
নারী-খেলার অভিজ্ঞতার প্রথম এবং পবিত্র ঋণ
তোমাকে নিয়ে কবিতা লিখে সত্যি কি আর শোধ হয়েছে?”
[হিরণবালা]
বাঙালি সাহসী জাতি। বাঙালির ইতিহাস সাহসিকতার ইতিহাস। নানান ভাবে, নানান সময় বাঙালিরা সেই প্রমাণ দিয়েছে। কবি হেলাল হাফিজ সেই ইতিহাসের ছন্দ থেকে সরে না দাঁড়িয়ে স্বাক্ষী হতে চেয়েছেন। নিজেই বলেছেন-
“...এরকম দুঃসময়ে আমি যদি মিছিলে না যাই,
উত্তর পুরুষ ভীরু কাপুরুষের উপমা হবো...”
[ দুঃসময়ে আমার যৌবন]
প্রসঙ্গত যে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে বন্ধুদের সাথে আড্ডায় পড়ে নিজের ইকবাল হলে ( জহুরুল হক) ফেরেননি হেলাল হাফিজ। যার কারণে ক্র্যাকডাউনের এই রাতে পাক সেনাদের নৃশংস হত্যাযজ্ঞ থেকে অলৌকিকভাবে বেঁচে যান তিনি। ক্র্যাকডাউনে বন্ধু হেলালের খোঁজ নিতে আজিমপুর থেকে ইকবাল হলে ছুটে আসেন আধুনিক বাংলা কবিতার আরো একজন পাঠকনন্দিত কবি নির্মলেন্দু গুণ। কারফিউ তুলে নিলে কবি হেলাল হাফিজ নিজের হলে গিয়ে দেখেন লাশের মিছিল। হলের গেইট দিয়ে বেরুতেই কবি নির্মলেন্দু গুণকে পেয়ে যান তিনি। আর হেলাল হাফিজকে জীবিত পেয়ে অঝোরে কাঁদতে থাকলেন নির্মলেন্দু গুণ।
কবি হেলাল হাফিজ নিজেকে নিজেই কবিতায় পরিচয় দিয়েছেন ‘দুঃখের আরেক নাম হেলাল হাফিজ’ হিসেবে। প্রেমিক কবি হিসেবেও হেলাল হাফিজের নিজস্বতা আছে। এক লাইনের কবিতায় তুলে ধরেছেন শতসহস্র শতাব্দীর গভীর প্রেম। যা বাংলা সাহিত্যে অনন্য সংযোজন।
“তোমার বুকের ওড়না আমার প্রেমের জায়নামাজ!”
[ ওড়না ]
বলা হয়ে থাকে, তরুণ-তরুণীদের প্রেম নাকি অনেকাংশে অসম্পূর্ণ থাকে হেলাল হাফিজের কবিতা ছাড়া। বিরহে কাতর প্রেমিকের কাছেও কবি হেলাল হাফিজের কবিতা তুমুল আলোচিত।
“...ইচ্ছে ছিলো রাজা হবো
তোমাকে সম্রাজ্ঞী করে সাম্রাজ্য বাড়াবো,
আজ দেখি রাজ্য আছে,
রাজা আছে
ইচ্ছে আছে
শুধু তুমি অন্য ঘরে।”
[ইচ্ছে ছিলো]
প্রেমিকার প্রস্থানে লিখেছেন-
“এখন তুমি কোথায় আছো কেমন আছো,পত্র দিয়ো,
.................................................................
আর না হলে যতœ করে ভুলেই যেয়ো, আপত্তি নেই।
গিয়ে থাকলে আমার গেছে, কার কী তাতে?
আমি না হয় ভালোবেসেই ভুল করেছি ভুল করেছি,
নষ্ট ফুলের পরাগ মেখে
পাঁচ দুপুরে নির্জনতা খুন করেছি, কী আসে যায়?
এক জীবনে কতোটা আর নষ্ট হবে,
এক মানবী কতোটাই বা কষ্ট দেবে!”
[প্রস্থান]
নিঃসঙ্গতায় কবি বলেন-
“কেউ জানে না আমার কেন এমন হলো
কেন আমার দিন কাটে না রাত কাটে না
রাত কাটে তো ভোর দেখি না”
[যাতায়াত]
এসব ছিলো কবিতায় হেলাল হাফিজের আংশিক পরিচয়। ব্যক্তিজীবনেও হেলাল হাফিজ এক বিস্ময়ের নাম, ঘোরের নাম। অদ্ভুত এক ভালোলাগার নাম। যা তাঁকে মৌলিক কবি হিসাবে গড়ে তুলতে অধিক কাজ করেছে। আজন্ম মানুষ তাঁকে পুড়াতে পুড়াতে কবি করে তুলেছেন, এ স্বীকারোক্তি তিনি নিজেই দিয়েছেন। জন্মের পর মাকে হারান। সেই কষ্ট তাঁকে প্রতিনিয়ত দগ্ধ করে। কিন্তু এ কষ্টই যেন তাঁর বেঁচে থাকার হিরণময় হাতিয়ার; জীবনের পরম অর্জন।
“কার পুড়েছে জন্ম থেকে কপাল এমন
আমার মতো ক’জনের আর
সব হয়েছে নষ্ট,
আর কে দেবে আমার মতো হৃষ্টপুষ্ট কষ্ট।”
[ ফেরিওয়ালা]
১৯৪৮ সালের ৭ অক্টোবর পিতা খোরশেদ আলী ঔরসে এবং মাতা কোকিলা বেগমের গর্ভে নেত্রকোণায় জন্মগ্রহণ করেন হেলাল হাফিজ। ১৯৬৫ সালে নেত্রকোণা দত্ত উচ্চ বিদ্যালইয় থেকে এসএসসি এবং ১৯৬৭ সালে নেত্রকোণা কলেজ থেকে এইচএসসি পশ করেন তিনি। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি হন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায়ই তৎকালীন জাতীয় সংবাদপত্র দৈনিক পূর্বদেশে যোগদান করেন তিনি। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এই পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭৬ সালের শেষ দিকে তিনি দৈনিক দেশ পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন এবং সর্বশেষে দৈনিক যুগান্তরে কর্মরত ছিলেন।
ব্যক্তি হেলাল হাফিজের সাথে আমার পরিচয় অনেকদিনের। গভীর এক বন্ধন আছে তাঁর সাথে। আর এ কারণেই তাঁকে আলাদাভাবে, আলাদা করে জানতে পেরেছি; কতোটা আত্মমর্যাদায় ঋদ্ধ কবি তিনি। কবিতার জন্য স্বেচ্ছায় নিঃসঙ্গতা বরণ করেছেন। সংসার করেননি। পড়েননি মেডিকেল। কর্ণফুলি হোটেলের এক ছোট্ট ঘর আর প্রেসক্লাব সীমানায় নিজেকে আটকে রেখে জমাচ্ছেন মানুষ। ভালোবাসা বিলিয়ে দিয়ে কবি হেলাল হাফিজকে ছাড়িয়ে ব্যক্তি হেলাল হাফিজও তুঙ্গস্পর্শী জনপ্রিয়। আকাশের চেয়ে অধিক এই উচ্চতা। তখন ব্যক্তি হেলাল হাফিজ লিখেন-
“কে আছেন?
দয়া করে আকাশকে একটু বলেন-
সে সামান্য উপরে উঠুক,
আমি দাঁড়াতে পারছি না।”
[রাখালের বাঁশি]
এতো এতো ভালোবাসা নিয়ে বেড়ে ওঠা কবি হেলাল হাফিজ নীরবেই হারাচ্ছেন তাঁর দৃষ্টিশক্তি। তাঁর চারপাশ ছেয়ে যাচ্ছে নিকষ অন্ধকারে। অভিমানী এ কবি নিজের ব্যক্তিত্ব নিয়েই বেঁচে আছেন, মেনে নিচ্ছেন সব। কিছুই বলছেন না। কারণ তিনি জানেন, তিনি হেলাল হাফিজ। আর কবির এ দুঃসময়ে কবির সহোদর নেহাল হাফিজ উচ্চারণ করেনঃ
“কবিতায় বামহাত দিয়েছিলে, বাম-
চোখটাও স্বেচ্ছায় দিয়ে দিলে!”
হেলাল হাফিজের মতো মৌলিক ও পাঠকপ্রিয় কবি আমাদের খুব বিরল। তাই দেশের দায় কিছুটা মুক্তির জন্য হলেও হেলাল হাফিজের চিকিৎসা নিশ্চিত ও বাস্তবায়ন করা জরুরী ।
এতে সদস্যতা:
মন্তব্যসমূহ (Atom)