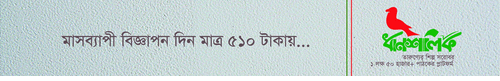আধুনিকতায়
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
মনোজিৎ কুমার দাস
ঊনিশ শতকের যুগসন্ধিক্ষণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের( ১৮২০- ১৮৯১) আবির্ভাব। ঊনিশ শতকের নবযুগের উদ্গতা ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে। বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য আর আধুনিকতার মেলবন্ধনে সমাজ সংস্কারের পুরোধা তিনি। বাঙালি হিন্দু সমাজের বিবিধ বিধিবিধানের সংস্কারকর্মে নিবেদিতপ্রাণ ঈশ্বরচন্দ্রের শিক্ষা ও কর্মজীবনের প্রতি আলোকপাত করলে সহজেই বুঝতে পারা যায় তিনি কোন আঙ্গিকে তৎকালীন সমাজকে অন্ধকার বৃত্ত থেকে আলোকে নিয়ে আসবার সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন।
ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে। পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ভগবতী দেবী। প্রাথমিক শিক্ষারম্ভ গ্রামের পাঠশালায়। ১৯২৮ সালে তিনি পিতার সঙ্গে পায়ে হেঁটে কলকাতায় আসেন এবং পরের বছর ১ জুন কলকাতার সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। গ্রামের টোল খোলার উদ্দেশে ঠাকুরদাস ছেলেকে শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। সংস্কৃত কলেজে শিক্ষার্জন ছিল ঠাকুরদাসের কাজে সম্মানের বিষয়। কিন্তু যে ছেলে বাবার সঙ্গে কলকাতায় আসবার সময় পথের ধারের মাইল ফলক দেখে ইংরেজি সংখ্যা শিখে ফেলেন, তাকে কি টোলের ক্ষুদ্র গ-িতে আটকে রাখা যায়? ঈশ্বরচন্দ্র একাধিকক্রমে ১২ বছর কাব্য, ব্যাকরণ, অলংকার, বেদান্ত, স্মৃতি, ন্যায়, জ্যোতিষ প্রভৃতি পাঠ করে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হন। শুধু তাই নয়, ১৮৩৯ সালে হিন্দু ল’ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। ১৮৪১ সালে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেডপ-িতের চাকরি পান। ওখানে তিনি ইংরেজি ও হিন্দি শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন।
কলকাতার বৃহত্তর পরিম-লে এসে তিনি দুটি বিবাদমান ভাবের সঙ্গে পরিচিত হলেন- একদিকে পাশ্চাত্য ভাবধারা গ্রহণে যুবসমাজের মধ্যে আকাঙ্খা, অন্যদিকে সতীদাহ ও অন্যান্য সামাজিক কুসংস্কারের প্রতি মোহ। পাশ্চাত্যের হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে বাংলার তরুণসমাজ আলোড়িত, বিভ্রান্তও খানিকটা। এক শ্রেণির তরুণদের মনে এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল হল যে, পাশ্চাত্যের অনুসরণ ও অনুকরণই আধুনিকতা। এই পরিবেশের মধ্যে থেকেও ঈশ্বরচন্দ্র হিন্দু ঐতিহ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা তাঁকে ভারতীয় ঐতিহ্যে উজ্জীবিত করেছিল। পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তিনি কলকাতার বিদ্বৎসমাজে যাতায়াত করে হয়ে ওঠেন যুগোপযোগী এক মহান চরিত্রের অধিকারী। সে সময় কলকাতার বাঙালি তরুণ সমাজ ও প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে চলছিল এক ধরনের টানাপোড়েন। এক দিকে, ডিরোজিও’র ভাবধারায় ¯œাত ইয়ংবেঙ্গলদের কালপাহাড়ি মনোভাব, অন্য দিকে, প্রবীণদের প্রাচীন সংস্কার আঁকড়ে থাকার আত্মঘাতী প্রয়াস। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবস্থান ছিল এই দুইয়ের মাঝখানে। হিন্দু ঐতিহ্যের মধ্যে তিনি আধুনিকতার সন্ধানী ছিলেন।
এক পর্যায়ে ডিরোজিও’র চিন্তাধারায় প্রভাবিত রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখ্যোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী প্রমুখের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের সখ্যতা গড়ে ওঠে। সে সময় কলকাতার পাশ্চাত্য শিক্ষার ভাবধারায় বিভিন্ন সভাসমিতি গড়ে উঠতে থাকে। ডেভিড হেয়ারের স্মরণ সভায় বিদ্যাসাগরের চিন্তাধারার প্রথম স্ফুরণ দেখা যায়। তাঁর চরিত্রে পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের তেজোময় নির্ভীক ঋজুস্বভাব পরিলক্ষিত হয়। পুরুষকারে বলীয়ান ঈশ্বরচন্দ্র হিন্দুধর্মের কুসংস্কারসমূহ বর্জন করে পশ্চিমাসভ্যতার ভাল দিকগুলো গ্রহণে ব্রতী হলেন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সংমিশ্রণে নতুন পথের সন্ধানেও সচেষ্ট হলেন। একথার স্বীকৃতি মেলে রবীন্দ্রনাথের কথা থেকে---- ‘ ঈশ্বরচন্দ্র পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিদ্যার মধ্যে সম্মিলনের সেতুস্বরূপ হয়েছিলেন। ’
সংস্কৃত ও হিন্দুধর্মের নানা শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করেও ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজি ভাষায় পা-িত্য অর্জন করতে পিছিয়ে থাাকেননি। ১৮৪৬ সালের ৬ এপ্রিলে তিনি সংস্কৃত কলেজের সহ -সম্পাদক হন কিন্তু কলেজের সংস্কার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হবে এই শর্তে তিনি ১৮৫০ সালে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য-- অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৫১ সালের ২২ জানুয়ারি কলেজের নবসৃষ্ট অধ্যক্ষের পদে তিনি নিযুক্তি লাভ করেন। তিনি অচিরেই কলেজের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীতে পরিবর্তন আনেন। তিনি অচিরেই কলেজের সব বিভাগের সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হন। কলেজের বিরতি দিবস পরিবর্তন, মাহিনা প্রবর্তন,পাঠ্যক্রম সংস্কার, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের পরিবর্তে সহজবোধ্য নতুন ব্যাকরণ তৈরি, গণিতে ইংরেজির ব্যবহার, দর্শনে পাশ্চাত্য যুক্তিবিদ্যার অন্তর্ভুক্তি এবং অব্রাহ্মণের প্রবেশাধিকার প্রভৃতি তাঁর সংস্কারের উদাহরণ। তাঁর আধুনিক মন পাশ্চাত্য ভাবধারার ভাল দিকগুলো গ্রহণে দ্ধিধা করেনি। তিনি জানতেন , বিদ্যার মধ্যে পূর্ব-- পশ্চিমের বিরোধ নেই। তিনি নিজে সংস্কৃতশাস্ত্রে মহাপ-িত হয়েও ইউরোপীয় বিদ্যার অভিমুখে ছাত্রদের অগ্রসর করতে উদ্যোগী হন।
সে --সময় শিশুশিক্ষার উপযোগী পাঠ্যবই, শিক্ষা পদ্ধতি এবং শিক্ষকের অভাব ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র এ সকল বিষয়ে ভাবিত হন। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের আগে হাতে লেখা পুঁথির মাধ্যমে এদশের শিশুদের শিক্ষা দেওয়া হত। ছাপাখানা স্থাপিত হবার পরও শিশুদের পাঠ্যবই ছাপার ব্যবস্থা করা হয়নি। ছাপা বই পড়লে জাত যাবে এমন একটা ধারণা সে যুগের লোকদের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল। এক পর্যায়ে কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হয়। এখান থেকে প্রকাশিত পাঠ্যবই সোসাইটি পরিচালিত পাঠশালা এবং খ্রিষ্টান মিশনারি সোসাইটির পাঠশালাগুলোতে পড়ানোর ব্যবস্থা হয়। শ্রীরামপুর মিশনারিরা শিশুদের উপযোগী কয়েকটি পাঠ্যবই প্রকাশ করে। হিন্দু কলেজের সঙ্গে স্থাপিত পাঠশালা এবং তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা কয়েকটি শিশুপাঠ্য বই প্রকাশ করে। শিশু পাঠ্য বইয়ের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও নানা সমস্যা দেখা দেয়। নানা লেখক এবং শিক্ষা সোসাইটি প্রকাশিত শিশুবোধক, লিপিধারা, জ্ঞানরুণোদয়, অন্নদামঙ্গল, হিতোপদেশ প্রভৃতি বই শিশুদের পড়ানো হত।
ঈশ্বরচন্দ্র এসময় যুগোপযোগী শিশুপাঠ্য প্রণয়নে এগিয়ে আসেন। এখানে একটি কথা বলা দরকার , ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে ঈশ্বরচন্দ্র বেথুন সাহেবের অনুরোধে বেথুন বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। সে সময় মদনমোহন তর্কালংকার এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। মদনমোহন তর্কালংকার শিশুদের উপযোগী শিশুশিক্ষা নামে বই প্রকাশ করেন। ্এই বইয়ের প্রথম ভাগে তিনি বেথুন সাহেককে উৎসর্গ করে ভূমিকায় লেখেন--- ‘ অনেকেই অবগত আছেন প্রথম পাঠোপযোগী পুস্তকের অসম্ভবে আমাদেশীয় শিশুগণের যথানিয়ম স্বদেশ ভাষা শিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে না-----’
জানা যায়,শিশুশিক্ষা পাঁচভাগে প্রকাশিত হয়। প্রথম তিন ভাগ লেখেন মদনমোহন তর্কালংকার স্বয়ং, চতুর্থভাগ বোধদয় লেখেন ঈশ্বরচন্দ্র এবং পঞ্চমভাগ নীতিবোধ রচনা করেন রাজকুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
ঈশ্বরচন্দ্র শিশুশিক্ষার বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে সহজ রীতিতে শিশুপাঠ্য রচনার কথা ভাবতে থাকেন। তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে বর্ণ পরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ রচনায় তিনি প্রগাঢ় মনীষার স্বাক্ষর রাখেন। শিশুদের উপয়োগী করার জন্য তিনি এই বই দুটোতে সরল অক্ষর, ভাষা ও উচ্চারণ সংযুক্ত করে মেধা- মনন – ভাষাজ্ঞানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।
বর্ণ পরিচয় প্রথমভাগে বর্ণের দ্বারা সহজ সরল শব্দ নির্মাণ নি:সন্দেহে শিশুমনে গভীর ভাবে রেখাপাত করে। উদাহরণস্বরূপ এই শব্দগুলোর কথা বলা যেতে পারে।---- ‘ অচল অধম অপর।’ কোথায়ও ‘আ ’কার বা ‘ ও’ কার ব্যবহার ছাড়াই রচিত শব্দগুলোর মধ্যে ছন্দের দ্যোতনা লক্ষ করা যায়। এই বইয়ের ছোট ছোট বাক্যগুলো শিশুমনে দোলা দেয়।‘ বড় গাছ। ভাল জল। হাত ধর। বাড়ী যাও।’ ইত্যাদির কথাও বলা যেতে পারে। বর্ণ পরিচয় দ্বিতীয় ভাগে তিনি যুক্তাক্ষর ব্যবহার করে শব্দ ও বাক্য রচনা করেন। বর্ণ পরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে তিনি নীতিকথা সন্নিবেশিত করেন, যা স্বত:সিদ্ধ সত্যের পরিচায়ক। তাঁর লেখা বর্ণ পরিচয় দ্বিতীয় ভাগে ধর্মেরবাণীকে তুলে ধরেন ঐতিহ্যের আলোকে। ‘ সদা সত্য কথা বলিবে’, কাহাকেও কুবাক্য বলিবে না’ ইত্যাদি হিতোপদেশ তিনি আধুনিক আঙ্গিকে উপস্থাপন করেন। কিন্তু আজ বড়ই দু:খের বিষয় , আমরা অবলীলাক্রমে ঈশ্বরচন্দ্রের বর্ণপরিচয়কে বর্জন করেছি।
১৮২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশ সরকার আইন করে সতীদাহ প্রথা বিলোপ করায় তৎকালীন বাঙালি হিন্দু সমাজে প্রচ- আলোড়ন সৃষ্টি হয়। গোঁড়া সমাজপতিরা এই আইন মেনে নিতে পারেনি। এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার জন্য ‘ ধর্মসভা’ স্থাপন করে তারা বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলে সতীদাহ প্রথা বহালের আবেদন করেন। ঈশ্বরচন্দ্র তখন সবে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়েছেন। বয়সও দশ বছরেরও কম। সতীদাহের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে না পারলেও ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি বিধাব বিবাহের জন্য এগিয়ে আসেন।
আগেই বলা হয়েছে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত প-িত হয়েও হিন্দুধর্মের কুসংস্কারমূলক বিধিবিধানগুলো আঁকড়ে থাকেননি। ডিরোজিও’র শিষ্য ইয়ং বেঙ্গলদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। হিন্দুসমাজের কুসংস্কার দূর করার লক্ষে গঠিত ‘ তত্ত্ববোধিনী সভা’র সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। পরবর্তীকালে ‘সর্বশুভকারী সভা’র মুখপত্র হিসাবে মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ‘সর্বশুভকারী পত্রিকা’। ঈশ্বরচন্দ্র এই পত্রিকায় ‘ বাল্যবিবাহের দোষ’ নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন, বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে হলে মেয়েদেরকে লেখাপড়া শেখাতে হবে। তখন শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে স্্রীশিক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র হিন্দুর প্রাচীন শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে স্ত্রীশিক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র হিন্দুর প্রাচীন শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে আধুনিক জীবনে তাকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সচেষ্ট হন। শাস্ত্র নির্দিষ্ট অর্থে এগিয়েই ঈশ্বরচন্দ্র বিধাবা বিবাহ প্রচলন ও বহু বিবাহ নিবারণের চেষ্টা করেন। তিনি বিচার বিবেচনা ছাড়া হিন্দুশাস্ত্রেও বিধিবিধান মেনে নিতে রাজি হননি।
আগেই বলা হয়েছে, ঈশ্বরচন্দ্র্রের সমাজ সংস্কারমূলক কাজের সূত্রপাত ১৮৫০ সালে ‘সর্বশুভকারী পত্রিকা’য় বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখে,‘ স্মৃতিশাস্ত্র প্রতিপাদিত কল্পিত কালমৃগ তৃষ্ণায় মুগ্ধ হইয়া অস্মদ্দেশীয় মনুষ্যমাত্রই বাল্যকালের পাণিপীড়নের প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন।----- লোকাচার ও শাস্ত্র ব্যবহারপাশে বদ্ধ হইয়া দুর্ভাগ্যবশত: আমরা বাল্যবিবাহ নিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ও দুরপনেয় দুর্দশা ভোগ করিতেছি।’ এই প্রবন্ধ থেকে দেখা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যবিবাহ সম্পর্কে হিন্দুধর্মের যুক্তিহীন বিধান মেনে নিতে পারেনি।
ঈশ্বরচন্দ্র যখন বিধবাবিবাহের সমর্থনে হিন্দুশাস্ত্রের বিধিবিধান সংগ্রহে রত, তখন বাংলার যুবসমাজে বিষয়টি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ১৮৫৩ সালের গোড়ার দিকে বিধাব বিবাহের সমর্থনে কলকাতায় তিনটির মত সভা হয়। ওই সব সভায় একদল যুবক বিধাব বিবাহকে সমর্থন করেন। পরবর্তীকালে তাদের অনেকেই আবার বিধাব বিবাহে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।
এক পর্যায়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিধাব বিবাহের পক্ষে শাস্ত্রীয় সমর্থন পান। ‘ পরাশর সংহিতা’য় তিনি বিধাব বিবাহের পক্ষে একটি বচনের সন্ধান পান। এই বচনটির সাহায্যে ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে ‘ বিধাব বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এটি প্রকাশের পর পর হিন্দু সমাজে আলোড়ন দেখা দেয়। ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র ওটার ১৫ হাজার কপি ছাপাতে বাধ্য হন। অন্য দিকে, ঈশ্বরচন্দ্র্রের বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর বক্তব্য ঠিক নয় বলে একের পর এক পুস্তিকা প্রকাশ করতে থাকে। ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে ঈশ্বরচন্দ্র লিখলেন দ্বিতীয় প্রবন্ধ ‘ বিধাব বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক দ্বিতীয় সম্বাদ’। বিধাব বিবাহ আন্দোলনের বিপক্ষে হিন্দু সমাজের অনেকেই এককাট্টা হন। এক পর্যায়ে ঈশ্বরচন্দ্র অনুভব করেন, বিধাব বিবাহ চালু করতে গেলে সমাজ ও রােেষ্ট্রর সমর্থন প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় আইনের জোরেই সতীদাহ প্রথা নিবারণ করা সম্ভব হয়েছিল। তাই তিনি শাস্ত্র- সন্ধানে বিধাব বিবাহ আইন পাশের জন্য আবেদনপত্র রচনা ও স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে অবতীর্ণ হন। ১৮৫৫ সালের ৪ অক্টোবর ভারত সরকারের বিবেচনার জন্য তিনি ৯৮৭ জনের স্বাক্ষরসংবলিত আবেদন পত্রটি প্রেরণ করেন। বিধাব বিধাব আইন পাশের বিপক্ষে বিরোধীরা সোচ্চার হয়ে ওঠে। তারাও সরকারের কাছে আবেদন করে যাতে আইনটি পাশ হয় না।১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই বিধাব বিবাহ আইন পাস হল, কয়েকমাসের মধে ধুমধাম করে কলকাতায় বিধাব বিবাহ বিয়েও হল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ঈশ্বরচন্দ্র্রের উদ্যোগে প্রথম বিধাবা বিবাহ করেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারতœ।
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মানবিক মূল্যবোধে জারিত মন বালবিধবাদের দু:খ- বেদনার ভারাক্রান্ত ছিল। হিন্দু বিধবাদের দু:সহ জীবনের করুণ চিত্র বিদ্যাসাগরের মর্মপীড়ার কারণ হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে তিনি নিজ উদ্যোগে নিজ অর্থ ব্যয়ে বিধবা বিবাহ দেন এবং এক সময় এ কারণে তাঁকে ঋণভার বহন করতে হয়। তিনি ১৮৭০ সালে তাঁর পুত্র নারায়ণচন্দ্রের সঙ্গে জনৈক বিধাবার বিবাহ দেন। তিনি বহু বিবাহ রোধে এগিয়ে আসেন। ১৮৬৩ সালের অক্টোবর মাসে প্রাণনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখরা বহু বহু বিধবা রোধে আইন তৈরির জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানান। তার কিছুদিন পরে দুর্গাচরণ নন্দী ও অন্যান্য সমাজ হিতৈষী ব্যক্তি এ বিষয়ে সরকারের কাছে আরেকটি অনুরোধ করেন।বহু বিবাহ নিবারণে হিন্দুদের প্রয়াসকে ‘ফ্রে- অফ ই-িয়া পত্রিকা’ স্বাগত জানায়। ১৮৬৫ সালের ৩০ মার্চ প্রকাশিত এক প্রবন্ধে পত্রিকাটি বিদ্যাসাগরকে বহু বিবাহ বিরোধী উদারপন্থী হিন্দুদের নেতা হিসাবে চিহ্নিত করে। বহু বিবাহের পক্ষে রাধাকান্ত দেব ও তাঁর দলবল সোচ্চার হয়ে ১৮৬৬ সালে সরকারের কাছে বহু বিবাহ রোধ না করার জন্য আবেদন করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বহু বিবাহ নিবারণে শাস্ত্রীয় বিধি বিধান উল্লেখ করে একখানা বই লেখেন। তিনি এ বইতে কুলীনদের বহু বিবাহের একটা তালিকা লিপিবদ্ধ করেন। এই বই হিন্দু সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বহু বিবাহের পক্ষের লোকেরাও বসে রইলেন না। তারাও ঈশ্বরচন্দ্র্রের বইয়ের জবাব দিলেন তাদের পক্ষে পাল্টা যুক্তি দেখিয়ে। ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৭২ সালে তাদের বক্তব্যেও বিরোধিতা করে ‘ বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার’ নামে দ্বিতীয় পুস্তক রচনা করেন। আইন করে বহু বিবাহ রোধ করা না গেলেও জনসাধারণের মধ্যে বহু বিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে ওঠে। ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রজ্ঞ প-িত হওয়া সত্ত্বেও কখনোই কুলীনদের একাধিক স্ত্রী গ্রহণের পক্ষে মত দেননি।
সে সময় শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করে মেয়েদের লেখাপড়ার দ্বার রুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয় এই অপব্যাখ্যাকে ঈশ্বরচন্দ্র কখনও মানতে পারেনি। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। যে, হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহ নিবারণের অন্যতম উপায় হল মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। ঊনিশ শতকের সূচনাপর্বে বাঙালি সংস্কারকরা স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে সোচ্চার ছিলেন। দু’একটি পুঁথিপড়া কূলীনসর্বস্ব প-িত নামধারীরা মেয়েদের অন্দরমহলের ঘেরাটোপে আবদ্ধ রেখে নিজেদের লালসা চরিতার্থ করার ষড়যন্ত হিন্দুসমাজেকে কোন অতলে নিক্ষেপ করছে সে বিষয়ে ভাবিত ইয়ং বেঙ্গল ও রামমোহনপন্থীদের সঙ্গে একদল সংস্কারপন্থী প-িত হাত মেলালেন। তাঁদের বোধদয় হয় , মেয়েদের শিক্ষাদান ছাড়া হিন্দুসাজের কল্যাণ কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এঁদের মধ্যে তারাশঙ্কর তর্করতেœর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৪৯ সালে বেথুনের উদ্যোগে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের জন্য কলকাতায় বিদ্যালয় খোলা হলে বিদ্যাসাগর সর্বশক্তি দিয়ে এই বিদ্যালকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেন। সে সময় বেথুনের পাশে ছিলেন ইয়ং বেঙ্গল দলের রামগোপাল, দক্ষিণারঞ্জন আর শাস্ত্রজ্ঞ প-িতদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন বিদ্যাসাগর । বেথুনের বিদ্যালয়ে মেয়েদের পাঠাতে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যমণি রবীন্দ্রনাখের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ডিরোজিও শিষ্য প্যারীচাঁদ , সংস্কৃতজ্ঞ মদনমোহন ইতস্তত করেননি। ১৮৫০ সালে বেথুন ঈশ্বরচন্দ্রকে সেক্রেটারি পদে নিয়োগ করেন।
ঈশ্বরচন্দ্র মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা কলকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে গ্রাম- গ্রামন্তরে ছড়িয়ে দেন। সরকার তাঁকে স্কুল ইনস্পেক্টও নিযুক্ত করলে গ্রামাঞ্জলে মেয়েদের স্কুল স্থাপনের সুযোগ এসে যায়। শিক্ষার্থীদেরকে বেত না মেরে ভালবেসে পাঠদানে ব্রতী করার জন্য তিনি শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। তাঁর উদ্যোগে বর্ধমান, হুগলি, নদীয়া ও মেদিনীপুরের বিভিন্ন গ্রামে একের পর এক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ছোটলাট হ্যালিডের মুখের কথায় উৎসাহিত হয়ে ১৮৫৭ সালের ২৪ নভেম্বর থেকে ১৮৫৬ এর মে’র মধ্যে তিনি ৩৫টির মত বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মেয়েদের এই বিদ্যালয় স্থাপন করতে গিয়ে তাকে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়।মেয়েদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সরকারি নির্দেশ লিখিতভাবে না থাকার কারণে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর ইয়ং বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলোতে অর্থ সাহায্যের বিরোধিতা করতে থাকেন। অনেক আবেদন নিবেদনের পর সাময়িকভাবে আর্থিক সাহায্য দিলেও স্থায়ী কোন অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়নি। কিন্তু এতে হতোদ্যম হননি তিনি। ১৮৭৮ সালে কোন কোনমহল থেকে মেয়েদেও বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেবার বিরোধিতা হলে বিদ্যাসাগর ব্যথিত হন। নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে চন্দ্রমুখী বসু বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে বিদ্যাসাগর তাঁকে সম্ভাষণ জানান।১৮৭০ সালে কুলনি স্বামীর অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে কৃষ্ণমণি নামে একটি মেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন। বিচারপতি নর্মান দায়িত্বহীন কুলীন স্বামীটিকে জেলে পাঠালে ‘ সনাতন ধর্মরক্ষণী সভা’র মত রক্ষণশীল সংগঠনের সদস্যরা নির্যাতিতা নারীর বিপক্ষে অবস্থান নেয়। বিদ্যাসাগর চুপ থাকতে পারেননি। আবার তিনি বহু বিবাহ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বহু বিবাহ বিবাহ বিষয়ক যে বইটির মুদ্রণ বন্ধ করে রেখেছিলেন তা আবার নতুন ভাবে মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন।
পিতা যে পুত্রকে তাঁদের গ্রামের পাঠশালার প-িত হিসাবে গড়ে তোলার জন্য কলকাতায় এনে শাস্ত্রজ্ঞ করতে চেয়েছিলেন।, সেই ছেলেটি শাস্ত্রজ্ঞ হয়ে শাস্ত্রেও সারবত্তাকে সত্যসন্ধানী দৃষ্টিতে আবিষ্কার এবং তাকে আধুনিকভাবে উপস্থাপন করে হিন্দুসমাজের কুসংস্কার দূরীকরণ, বাল্যবিবাহ রোধ, বহুবিবাহ নিরোধ, বিধবার বিাবাহ প্রবর্তন এবং শিক্ষার আলোকবঞ্চিত মেয়েদের শিক্ষাদানে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণে জীবন নির্বাহ করতেন. যদি ইউরোপীয় ভাষা- সাহিত্যের চর্চা না করে পাশ্চাত্য ভাবধারা সম্পর্কে জানার্জন থেকে বিরত থাকতেন তবে হিন্দু সমাজের কৌলিন্য প্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রথা নারী নমাজকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রাখত একথা নির্দ্ধিায় বলা যায়। নারীদরদী, নারীমুক্তি আন্দোলনের পুরোধা, কালোত্তীর্ণ আধুনিক ঈশ্বরচন্দ্র চিরকাল আমাদের নমস্য হয়ে থাকবেন।