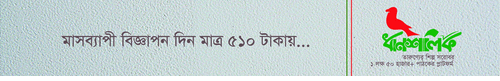দুর্ভেদ্যযামিনী : নৈঃশব্দ্যের মিছিলে শব্দের অভিযাত্রা
আসআদ শাহীন
ঝঞ্ঝাট-কোলাহলমুক্ত প্রকৃতি। নিস্পন্দন-নিঝুম-পিনপতন-নৈঃশব্দ্যতা চারিদিকে। ফাগুনীয়-শৈত্যপ্রবাহের মৃদু হিমেলীয় দমকা হাওয়া বইছে। অন্তরীক্ষে উড়ো উড়ো শ্বেতাভ জীমূতমালারা লুকোচুরি খেলায় মত্ত। নিহারিকা ও ইন্দু দু’জনার গভীর সখ্য গড়ে উঠেছে। নেই কোনো রেষারেষি ও মনান্তর। সত্যিই এসব বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিকের কথা কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কাব্যরূপে নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন-
‘চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা-কোথায় উজান এমন ধারা,
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ, এমন কালো মেঘে,
তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে পাখির ডাকে জেগে।’
তদ্রুপ বুদ্ধদেব বসু-ও এ প্রকৃতির রূপ, বৈচিত্রময়তা ও সৌন্দর্যতার উপমা কাব্যিক তুলিতে এঁকেছেন-
‘কী নির্মল নীল এই আকাশ, কী অসহ্য সুন্দর,
যেন গুণীর কণ্ঠের অবাধ উন্মুক্ত তান
দিগন্ত থেকে দিগন্তে;
কী ভালো আমার লাগলো এই আকাশের দিকে তাকিয়ে;
চারদিক সবুজ পাহাড়ে আঁকাবাঁকা, কুয়াশায় ধোঁয়াটে,
মাঝখানে চিল্কা উঠছে ঝিলকিয়ে।’
গিরি এক পথ ধরে হেঁটে চলেছি নির্লিপ্ত আনমনে আর অবলোকন করছি রাতের নৈসর্গিকতা। তবে, কায়াতে শীতলের প্রকটতা জেঁকে বসেছে। লোমকূপগুলো ক্রমশই জড়সড় ও কেঁপে কেঁপে উঠছে। বদনে ¯্রফে একটি শুভ্রবসন। সেই সন্ধ্যেয় পরিধান করে বেরিয়ে পড়েছি। অংসে একটি ব্যাগ ঝুলিয়ে। কেনো বেরিয়ে পড়েছি, কারণ কি-সবই অজান্তা। এখন একটি ল্যাম্পপোস্টের নিচে দণ্ডায়মান। কতকগুলো কুকুরের আনাগোনা। লাল-কালো-ধূসর-ডোরাকৃতি। নেই কোনো পত্র-পল্লবের দূষিত শব্দবহের অনুরণন। নেই কুকুরদের ও ‘ঘেউ-ঘেউ’ শব্দের প্রকটতা। এই ঠাঁইয়ের সঙ্গে আমি পূর্বপরিচিত। বেশ কয়েক দফা নিজ তাগিদে এখানে আগমন ঘটেছে। এতক্ষণ যাবৎ মোবাইলে পিডিএফ বইপাঠে মগ্ন ছিলুম। বঙ্গবন্ধুর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’।
‘এ বইটা মূলত ১৯৩৮/৩৯ -১৯৫৫ পর্যন্ত সময়কালের ঘটনা প্রবাহ নিয়ে লেখা। (বিশেষ করে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ঘটনাবলীর এক অনবদ্য দলিল)। এছাড়া শুরুতে বঙ্গবন্ধুর গ্রামের বাড়ি, জন্মবৃত্তান্ত, বংশ, ও তরুণ কালের কিছু ঘটনা পাঠকদের সুবিধার্থে তুলে ধরেছেন। বইটা ঠিক ডায়েরী না। ১৯৬৭ সালে কারাগারে থাকাকালীন তিনি এই বই লেখা শুরু করেন। তাই এটিকে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ স্মৃতিচারণ মূলক আত্মজীবনীই বলা যায় আবার স্মৃতি ডায়েরীও বললেও ভুল হবে না হয়ত। বইটি শ্রুতিলিখন বা অনুলিখনের মাধ্যমে অন্য কারো হাতে লিপিবদ্ধ নয় বরং বঙ্গবন্ধু নিজেই জেলখানায় বসে নিজের স্মৃতি থেকে বইটি রচনা করেন। তাঁর দুহিতাদ্বয় (বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী) শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা শুধুমাত্র প্রকাশের আগে কিছু ভাষাগত সম্পাদনা করেন। এছাড়া তথ্যগত কোন সম্পাদনা করা হয়নি বলেই উল্লেখিত রয়েছে।
একজন সাধারণ মানুষ থেকে পূর্ব বাংলার মুক্তিকামী মানুষের মুক্তির দিশারী হয়ে উঠার গল্পে ভরা এর প্রতিটা পাতা। পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ। সহজ সরল ভাষায় তিনি তার স্মৃতির রাজ্য খুলে দিয়ে বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের যে ধারাবাহিক বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন, তাতে একজন পাঠক খুব সহজেই তাঁর- শেখ মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠার উপাদান সমূহ অনুধাবন করতে পারবেন ।’
এবার একটু উঠে দাঁড়ালাম আমি। কিঞ্চিদধিক অগ্র হয়ে চলতে আরম্ভ করলাম। কোথায় যাচ্ছি, কোনদিকে এগোচ্ছি- তা বিস্মৃত। এই ফাগুনের নিশীথ সময়েও চারিধার প্রকট ঘনান্ধকারে আঁধারের শামিয়ানায় ঢাকা। নিশিপুষ্প-শিউলি-হাসনাহেনা ও আম্রমুকুলের সঙ্গমের সৌরভময় ঘ্রাণে ঘ্রাণেন্দ্রিয় সুবাসিত হচ্ছে।
এই ঋতুরাজ বসন্ত তথা ফাগুনের আবির্ভাবপ্রণয়জনিত সঙ্গমে বৃক্ষাদি পুরনো পাতা-পল্লব ছাড়িয়া নব কচি কচি সবুজাভ পাতা-পল্লবে প্রসবিতা হয়। বসন্তের দৃষ্টিনন্দিত রূপবিভায় বাংলা অপরূপ এক রূপ ফিরে পায়। তাই তো জীবনানন্দ দাশ কবিতার ভাষায় কতই না চমৎকার ভাবে বাংলার রূপের কথা ব্যক্ত করেছেন-
‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর : অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতো বড় পাতাটির নিচে বসে আছে
ভোরের দোয়েলপাখি - চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের-অশথের করে আছে চুপ;
ফণীমনসার ঝোঁপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে;
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ।’
যদি এসবের উপমা কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভাষায় বলি তবুও ভুল হবে না। কেননা, তিনি তো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেছেন-
‘পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি,
গুঞ্জরিয়া আসে অলি, পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে,
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রানী সেযে আমার জন্মভূমি।’
চতুঃর্পাশ্ব বিক্ষিপ্ত শুকনো পাতা-পল্লবের মর্মরধ্বনি ঝঙ্কারিত হয়। গগনে গর্জ্জনবিরত শ্বেতকৃষ্ণাভ নীরদমালার মধ্যে হ্রস্বদীপ্তি সৌদামিনী মধ্যে মধ্যে চমকাচ্ছে। বোধ হচ্ছিল হয়ত বৃষ্টি নামবে। কিন্তু আমার বোধ শেষ না হইতেই হঠাৎ-ই ফাগুনাকাশ ছেদ করে ঝিরিঝিরি বারি নেমে আসল। তবে বোধহয় ভালোই হলো। ক্রমাগত চলতে থাকা ঘর্মাক্তবদন বর্ষণমুখর বারিবিন্দুতে কিছুটা শৈত্যের শীতলতম আবেশ-বিহ্বলতায় সিক্ত হলো।
তবে বারিবর্ষণ শব্দের মধ্যে বৃক্ষাগ্র হতে বৃক্ষপত্রের’ পর বর্ষাবশিষ্ট বারিবিন্দুর পতনশব্দ, বৃক্ষতলস্থ পত্রচ্যুত জলবিন্দুপতনশব্দ, পথিস্থ অনিঃসৃত জলে শৃগালের পদসঞ্চারণশব্দ, কদাচিৎ বৃক্ষারূঢ় পক্ষির আর্দ্র পক্ষের জল মোচনার্থ পক্ষবিধূননশব্দ। মধ্যে মধ্যে শমিতপ্রায় বায়ুর ক্ষণিক গর্জ্জন, তৎসঙ্গে বৃক্ষপত্রচ্যুত বারিবিন্দু সকলের এককালীন পতনশব্দ। এহেন পরিস্থিতিতে রবী ঠাকুরের কবিতাটি অনির্বার উচ্চারিত হচ্ছে মনের কুঠরিতে-
‘আজি গন্ধবিধুর সমীরণে
কার সন্ধানে ফিরি বনে বনে।
আজি ক্ষুব্ধ নিলাম্বর-মাঝে
এ কি চঞ্চল ক্রন্দন বাজে।
সুদূর দিগন্তের সকরুণ সংগীত
লাগে মোর চিন্তায় কাজে--
আমি খুঁজি কারে অন্তরে মনে
গন্ধবিধুর সমীরণে।
ওগো জানি না কী নন্দনরাগে
সুখে উৎসুক যৌবন জাগে।
আজি আম্রমুকুলসৌগন্ধে,
নব-পল্লব-মর্মর ছন্দে,
চন্দ্র-কিরণ-সুধা-সিঞ্চিত অম্বরে
অশ্রু-সরস মহানন্দে
আমি পুলকিত কার পরশনে
গন্ধবিধুর সমীরণে।’
কবিতাটি বিস্মৃতিপ্রবণতাযুক্ত করিয়া অগ্রসর হইলাম। ইহার একটা হেতুও রয়েছে। তবে থাকুক না হেতুটা পুশিদা!
হাতঘড়ির গ্লাসের ’পর আলতো ছোঁয়া লাগাতেই আলো জ্বলে উঠলো। জ্বলজ্বল করে জ্বলে থাকা গাণিতিক সংখ্যাগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হতেই আমি ভড়কে উঠলাম। দেখি- শূন্য এক, তেত্রিশ। মানে এখন মধ্যরাত। তবে রাস্তাঘাট অনেকটাই ফাঁকা। এই পরিবেশে নিঃসঙ্গ-নিশাচর-একাকি হেঁটে বেড়াবার মজ্জাই ভিন্নতর। সেই ছোট বেলা থেকেই পথ হাঁটতে আমার ভালো লাগে। আলোজ্বলা পথ, ছায়ার ঘোমটা-ঢাকা পথ, সুনসান পথ, ধুলোওড়া পথ, ফেরিওয়ালার গলার আওয়াজে চমকে-ওঠা পথ; সবরকমের পথ বেয়ে হেঁটে যেতে ভালোবাসি আমি।
তথাপি এই নিশীথ সময়ে নিজেকে মনে হচ্ছে আমিই হিমু। কারণ, হিমুর শখ ছিল গভীর রজনীক্রান্তে একাকি হেঁটে বেড়ানোর। মন বলছে হিমুর শহর ‘নুহাশ পল্লীতে ঘুরে বেড়াবার। কিন্তু তা আদৌ সম্ভবপর নই। আকাশকুসুম কল্পনা। নানাবিধ কল্পনা-জল্পনা স্মৃতির দফতরে নাযরানা পেশ করছে। কিন্তু একটাও গ্রাহ্য হচ্ছে না। কোথায় এসেছি ভ্রুক্ষেপ করিনি। কিছুদূর হেঁটে যাওয়ার পর একটি বিলবোর্ড চোখে পড়ল। সেথায় লেখা আছে পদ্মা নদীর পাড়। এর মানে হল আমি এখন পদ্মা নদীর তীরে অবস্থান করছি।
(এই পদ্মা নদীকে ঘিরে রয়েছে অনেক ইতিহাস। পদ্মা নদী (চধফসধ জরাবৎ) মূলত গঙ্গার নিম্ন ¯্রােতধারার নাম, (হিমালয় পর্বতমালার গঙ্গোত্রী নামক হিমবাহ হতে গঙ্গা নামে উৎপত্তি) আরও নির্দিষ্টভাবে বলা যায় গোয়ালন্দ ঘাটে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম স্থলের পরবর্তী মিলিত প্রবাহই পদ্মা নামে অভিহিত। এই নামটি (পদ্মা) গঙ্গা নদীর ডান তীর থেকে বিভক্ত হয়ে আসা ভাগীরথী নামক শাখাটির উৎসস্থল পর্যন্ত ব্যবহূত হয় এবং হিন্দুমতে এই ধারাটিই গঙ্গার ধর্মীয় পবিত্রতা বহন করে।
নদীজ ভূমিরূপ বিদ্যাগতভাবে যমুনার সাথে সঙ্গমস্থলের পূর্ব পর্যন্ত প্রবাহটিকে গঙ্গা নামে এবং সঙ্গমস্থল পরবর্তী নিম্ন¯্রােতধারাকে পদ্মা নামে অভিহিত করা অধিকতর সঠিক। পদ্মা কখনও কখনও ভুলবশত গঙ্গা নামে উল্লিখিত হয়।
ব্রহ্মপুত্রের স্থানান্তরিত প্রবাহের ফলে এই নদীখাতের সৃষ্টির কারণে শুধুমাত্র নয় বরং বৎসরের অধিকাংশ সময়ে ব্রহ্মপুত্র-যমুনা গঙ্গার তুলনায় পদ্মার প্রবাহে অধিকতর ভূমিকা রাখে।
রাজা রাজবল্লভের কীর্তি পদ্মার ভাঙ্গনের মুখে পড়ে ধ্বংস হয় বলে পদ্মার আরেক নাম কীর্তিনাশা।)
এই পদ্মা নদী নিয়ে বিভিন্ন কবি অনেক কবিতা রচনা করে গেছেন। রচিত হয়েছে অনেক গান।
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর কবিতায় পদ্মার প্রতি বলেছেন-
‘হে পদ্মা! প্রলয়ংকরী! হে ভীষণা! ভৈরবী সুন্দরী!
হে প্রগলভা! হে প্রবলা! সমুদ্রের যোগ্য সহচরী
তুমি শুধু, নিবিড় আগ্রহ আর পার গো সহিতে
একা তুমি সাগরের প্রিয়তমা, অয়ি দুবিনীতে!
দিগন্ত বিস্তৃত তোমার হাস্যের কল্লোলতারি মত
চলিয়াছে তরঙ্গিয়া, চির দৃপ্ত, চির অব্যাহত।
দুর্নমিত, অসংযত, গূঢ়চারী, গহন গম্ভীর;
সীমাহীন অবজ্ঞায় ভাঙিয়া চলেছ উভতীর।’
কাজী নজরুল ইসলাম-ও পদ্মা নদীকে তাঁর কাব্যতে এভাবে তুলে ধরেছেন-
‘পদ্মার ঢেউ রে
মোর শূণ্য হৃদয় পদ্ম নিয়ে যা যারে
এই পদ্মে ছিল রে যার রাঙ্গা পা
আমি হারায়েছি তারে।।
মোর পরান বধু নাই,
পদ্মে তাই মধু নাই নাই রে
বাতাস কাঁদে বাইরে
সে সুগন্ধ নাই রে
মোর রূপের সরসীতে আনন্দ-
মৌমাছি নাহি ঝঙ্কারে।’
অনুরূপ জসিম উদ্দিন-ও তাঁর কবিতাতে পদ্মানদীর কথা উল্লেখ করেছেন-
‘জেলে গাঙে মাছ ধরিতে যায়,
পদ্মা নদীর উজান বাঁকে ছোট্ট ডিঙি নায়।
পদ্মা নদী কাটাল ভারী, চাক্কুতে যায় কাটা,
তারির পরে জেলের তরী করে উজান ভাঁটা।
জলের উপর শ্যাওলা ভাসে, ¯্রােতের ফুলও ভাসে,
তারির পরে জেলের তরী ফুলেল পালে হাসে;
তারি সাথে ভাসায় জেলে ভাটীর সুরে গান,
জেলেনী তার হয়ত তাহার সাথেই ভেসে যান।’
যেখানে দিনের বেলায় রিকশা আর রঙ বেরঙের বিভিন্ন আকৃতির মানুষে ভরা থাকতো, এখন সেখানে শুধুই আবর্জনার স্তূপ ছড়িয়ে আছে। ফুটপাত-শপিংমলের টাইলস মোড়ানো চকচকে সিঁড়িগুলো বেওয়ারিশ কুকুর আর হাড্ডিসার অর্ধ-নগ্ন মানুষের বিছানায় পরিণত হয়েছে। পথ ছিল গাড়ি-ঘোড়া শূন্য, ফাঁকা রাস্তায় দ্রুতই পৌঁছে গেলাম ব্রিজের গোঁড়ায়।
ল্যাম্পপোস্টের ঝলমলে আলোয় চারপাশ উদ্ভাসিত, তীব্র আলোর কিছু রশ্মি ছায়া ফেলছে ¯্রােতস্বিনীর জলে, তাতে লোচনে পড়ছে অনুদ্ধত তটিনীর আলতো লহরী। মৃদু বীচিপুঞ্জের উপর ভাসছে কিছু গলুইবিহীন ছোট নৌকা। দূরে নোঙ্গর করা বিরাট সাইজের লাইটার অর্ণবপোতগুলো ভাসছে নিশ্চল। নদের দু’পাড়ের উঁচু উঁচু দালানগুলোর শরীর থেকে আলোকচ্ছটা ঠিকরে বেরুচ্ছে এই মাঝ রাতেও। ছাদের উপর বসানো রঙিন বিলবোর্ডের লাল-নীল-হলুদ আলো ধাঁধিয়ে দিচ্ছে রাতের অন্ধকার আকাশ।
এই পরিবেশে পদ্মা নদীকে দেখে স্মৃতির বাতায়ন খুলে যায় দখিনা হাওয়ায় এক নিমিষেই। তখন ভিড় করে সারি সারি, গুচ্ছ গুচ্ছ সাজানো ছোটবেলার কত শত স্মৃতিকথা। আশৈশবের দুরন্তপনা। ফেলে আসা দিনগুজরানোর রূপ-রস-গন্ধ-ছোঁয়া-স্পর্শের অনুভূতিতে ধূসর-মলিনবিধুর চিত্রায়ন ভেসে ওঠে স্মৃতিপটে। আমার ছোট চোখ দু’টো হয় যদি অতীতের স্বপ্ন ধরে রাখার আরশি-তবে আমার ছোটবেলার প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি দিন সেই অতীতের স্বপ্ন ধরে রাখা সারি সারি সাজানো একেকটা মহামূল্যবান হিরে-পান্না। আমার বুকের অন্তরায় শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্রটা যদি হয় পৃথিবীর সর্বোচ্চ মুস্তার্দা-তাই তো সেথায় সারি বেঁধে সাজানো বেসাতের বোরার মত রয়েছে আমার শৈশব-কৈশোরের সেই সুমধুর সময়-আনন্দঘন মুহূর্ত-দিনগুলো।
আমি আশৈশব-যখন থেকে বই পড়তে শিখেছি তখন থেকেই বইয়ের প্রতি ভালোবাসা-ভালোলাগা ছিল তীব্রতর। একটি কথা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বললেও ভুল হবে না- আমি গ্রন্থকীট। সব রকমের বই পড়তে ভালোবাসতাম। সেসময় কোনো বাচবিচার ছিল না। যখন যেটা হাতের নাগালে পেতাম গোগ্রাসে গিলে ফেলতাম। আমাদের গ্রামে একটা পাঠাগার ছিল। সেখানকার প্রায় বই-ই আমার পড়া হয়েছে। ইশ! মন বলে আবার যদি সেই সোনা ঝরা রৌদ্রময় শৈশব ফিরে পেতাম! আজও যদি সেরকমই গ্রন্থকীট হতাম! সময়ের বিবর্তনে সব কিছু যেন ওলোটপালোট হয়ে গেছে। আজ এই পদ্মানদীর পাড়ে বসে মনে পড়ছে মানিক বন্দোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসের কথা। এই উপন্যাসটি শুরু হয়েছে পদ্মার রূপ বর্ণনার মধ্য দিয়ে।
‘বরষার মাঝামাঝি ইলিশ ধরার মওসুমে রাত্রিকালীন পদ্মার রূপ চিত্রনে লেখক সংকেতময় উপমা মত ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন। লেখকের দৃষ্টিতে নদীর বুকে শত শত কৈবর্ত নৌকা আলো জোনাকীর মত ঘুরে বেড়ায়। অন্ধকারের মধ্যে আলো দুর্বোধ্য। রাতে সারা পৃথিবী যখন নিদ্রামগ্ন তখন আলোগুলো থাকে অনির্বাপিত। এই আলোতে ইলিশের নিষ্পলক চোখগুলো হয়ে ওঠে স্বচ্ছ নীলাভ মনি সদৃশ্য। রাত্রিকালের কৈবর্ত নৌকার এই বর্ণনা ছাড়া লেখক উপন্যাসের একাধিক স্থানে পদ্মার রূপ অংকন করেছেন।
পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসটি মানিক বন্দোপাধ্যায়ের আধুনিক বাংলা উপন্যাসের একটি বিশিষ্ট সংযোজন। জীবন জীবিকার তাগিদে পদ্মানদীর সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত মানুষের জীবন কাহিনী।
জীবন কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে উপন্যাসিক কৈবর্তদের যে অনবদ্য চিত্র অংকন করেছেন তা যেমন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তেমনি এই ঔপন্যাসে মানুষের হৃদয় বৃত্তির যে বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে তাও পাঠকের মনকে দারুণভাবে নাড়া দিয়ে যায়। বাংলাদেশের সমাজ জীবনে নিম্ন শ্রেণির গ্রামীণ মানুষের বাস্তব চিত্র এখানে নিখুঁত ভাবে রূপায়িত হয়েছে।
পদ্মা নদীর মাঝি উপন্যাসটি বাংলাদেশের পদ্মা তীরবর্তী অঞ্চলের জেলে সম্প্রদায়ের জীবন চিত্র। কৈবর্ত ও নাবিকদের দুঃসাহসিক জীবনযাত্রা এই উপন্যাসের উপজীব্য। পদ্মার সংগ্রামী জীবনের সাথে কৈবর্তদের যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক তাতে তাদের আনন্দ নেই, নেই স্বপ্ন, নেই চাওয়া পাওয়া। আছে সীমাহীন বেদনা ভার। প্রাণন্তর পরিশ্রম করেও সেই পরিশ্রমের ফসল তারা ভোগ করতে পারেনা। ভোগ করে মহাজন। উপোষ কাপসে তাদের দিন কাটে। পদ্মানদীর মাঝি কৈবর্তদের জীবন দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাতে জর্জরিত। জেলে পাড়ার ঘরে ঘরে শিশুদের ক্রন্দন কোনদিন থামে না।’
উপন্যাসটির কথা চিত্রায়ন করতে গিয়ে কখন যে চোখের কোণায় জল এসে খেলা করছে তা বুঝতেই পারি নি। আমি এতোক্ষণে ব্রীজ থেকে নেমে নদীর উপর বেঁধে রাখা একটা ডিঙি নৌকায় উঠে বসলাম। এখান থেকে রাতের আকাশটা মনে হচ্ছে আমার খুব কাছে। হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারব। তবে যেহেতু আজ সন্ধ্যেয় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হয়েছে সেজন্য আকাশটা একটু মেঘলা। বৃষ্টিস্নাত আকাশ হলেও শশীর কৌমুদিনী ঠিকই নদীর অনুদ্ধত জলের সাথে লুকোচুরি খেলছে। আমি আমার পা দু’টো সেই শান্ত জলে ডুবিয়ে দিয়ে বিস্তৃত রাত্রিকালীন নদীর দৃশ্য অবলোকন করছি।
দূর হতে দেখা যায়-এই মধ্য রাতেও কিছু কৈবর্তরা নৌকায় চড়ে জাল ফেলে মৎস শিকার করছে। নাবিকেরা বৈঠা বইছে। রাতের আকাশে আনোখা কিছু পাখির উড়াউড়ি। কিনারে থাকা ঝোপঝাড় থেকে ভেসে আসছে নিশি-পাপিয়াদের সুরের মূর্ছনা। মধ্যে মধ্যে কল্লোলিনীর তরঙ্গ আছড়ে পড়ছে তরঙ্গিণীর বক্ষঃস্থলে। ঊর্মিমালার প্রকট গর্জ্জনের হ্রস্বধ্বনি। সহসা কেনো যেন মন বলে উঠল-এমন মুহূর্তকে নিয়ে কিছু লিখতে। তাই উদাসী মনে লিখে ফেললাম-জানি না এটাকে কবিতা বলে কি না!
‘প্রগাঢ় কৃষ্ণে নিশিকৃষ্ণ
ধরত্রীর ওই অন্তরীক্ষ
কুঞ্জকাননে কুররপক্ষী
উড়ন্ত তাহারী বক্ষ।
ডলক ডহাতে ধুনিজল
ফিরে যৌবনে থৈ থৈ
প্রত্যেহ নিশিতে চন্দ্র
ধুনির লগে পাতে সই।
নাবিকেরা তরী তীরে
প্রাবৃটপ্রাতে করে নঙর
কৈবর্ত মৎস দরিয়াপ্তে
সঙ্গেতে নেয় স্বকোঙর।’
পুনশ্চ: ভাবনার সাগরে ডুব দিতে দিতে মনের দহলিজে কিসের যেন ঘণ্টাধ্বনি বেজে উঠল-কর্ণকুহর সজাগ হয়ে অনুসন্ধিৎসু হলো। এক অচিনকূল হতে অনুরণিত হচ্ছে রবী ঠাকুরের এই পঙক্তিমালা-
“নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস,
ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।
নদীর ওপার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে;
কহে, যাহা কিছু সুখ সকলি ওপারে।”
শিক্ষার্থী: ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।